সালটা ১৯৪৩। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তিম দশক। চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। টালমাটাল অর্থনৈতিক পরিবেশ। অসম্ভব বেড়ে গেছে জিনিসের দাম। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমছে। ইতিমধ্যেই গান্ধীজি ডাক দিয়েছেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের, অন্যদিকে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ বাহিনী সামরিক সংগ্রাম চালাচ্ছেন। অন্যদিকে জাপান ১৯৪২ এ বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) নিজের অধিকারে এনে ফেলেছে। ব্রিটেন প্রমাদ গুনছে। ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ছে। কলকাতা বেশ কয়েকবার কেঁপে উঠেছে জাপানি বোমার শব্দে। জাপানি আগ্রাসনের ভয় থেকে ব্রিটিশ প্রশাসন গ্রহণ করেছে পোড়ামাটি নীতি, সেই কুখ্যাত নীতি যার ব্যবহারে রাশিয়া ১৩০ বছর আগে পরাস্ত করেছে দোর্দন্ডপ্রতাপ আগ্রাসী শক্তিকে — নেপোলিয়নের দূর্জয় সেনাদলকে।
জাপানি আক্রমণের ভয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো মাঠ ভরা ফসল, নিশ্চিত করা হলো গ্রামে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটুও খাদ্যশস্য না থাকে। এদিকে যুদ্ধের বাজারে সামরিক খাতে সরকারি খরচ বিপুল বৃদ্ধি পায়। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত করা শুরু হয় শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর জন্য। এই দুর্দিনের মাঝেই '৪২ এ উপকূলীয় বঙ্গে আছড়ে পড়ে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়, ক্ষতির মুখে পড়ে কৃষিজমি। আমন ধানের ফলন কমে। কিন্তু ফলনের এই ক্ষতি এমন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না যে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। এমনকি ১৯৪৩ এ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি ছিল। আই আই টি গন্ধীনগরের গবেষক বিমল মিশ্রের মতে, বর্ষার ব্যর্থতা নয়, আসলে নীতিগত ব্যর্থতা সংকট ডেকে আনে। অমর্ত্য সেনের মতে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক অ-কৃষিজীবী শ্রেণি যে মূল্যে তাদের জিনিসপত্র ও শ্রম বিক্রি করেছে তার চেয়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। মূল্য আর খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য নড়ে যাওয়ায় দরিদ্র কৃষক পরিবারগুলোয় শুরু হয় তীব্র অনটন।
.jpeg)
১৯৪৩ এর শুরু থেকেই বাংলার কৃষিনির্ভর মানুষ গুলো এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। খাবার নেই, সর্বত্র হাহাকার। অনাহারে দিন কাটে, জাঁকিয়ে বসে অসুখ। ভেঙে যায় স্থিতিশীল বন্ধন। ভুখা পেটে সর্বস্ব বেচে দুটো ভাতের আশায় মাথা কুটে মরে তারা। চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে চলে যায় উপোসি প্রানগুলো। ঘনিয়ে আসে দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ — পঞ্চাশের মন্বন্তর... ১৩৫০ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ বাংলার ইতিহাসে, মানুষের স্মৃতিতে থেকে যায় দগদগে ক্ষত হয়ে...
আসলে যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরুর সময় থেকেই আখের গোছাচ্ছিল ছিল মানুষ। গ্রামের মানুষগুলো ভেবেছিল এরাই বোধহয় ঈশ্বর! হাত পাতলেই টাকা দেয়, খাবার জোটে। মহানুভবতার মুখোশ পরে তারা কেড়ে নিচ্ছিল অনাহারী মানুষদের অন্তিম অবলম্বনটুকু। জমিজমা ছিনিয়ে নিয়ে পকেট ভরাচ্ছিল। তাদের ঘাম ঝরানো সোনার ফসল বেচে দিয়ে আসছিল আর একদল অর্থলোলুপের জিম্মায়। তারা মজুতদার! চাল ডাল জমিয়ে রেখে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে সেসব বেচে দিচ্ছিল পয়সাওয়ালাদের কাছে, যারা পেট ভরাতে দ্বিগুণ, তিনগুণ অর্থ ব্যয় করতে পারে। মজুতদারের গুদামঘর না খাওয়া মানুষদের ঘাম ঝরানো ফসলে ভরছিল, জমে উঠছিল কালোবাজারি — "হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার,/ ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার/ গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো / বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান ছয় হাঁকালো।/ কেউ নেই ত্রিভুবনে, নেই কিছু অভাবও/তবু ছাড়ল না তার লোক-মারা স্বভাব ও।" (সুকান্ত ভট্টাচার্য)
আরেকদিকে স্বভাব-শোষক শাসক। গবেষক মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় এই দুর্ভিক্ষের জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে। বারবার যখন মন্ত্রিসভাকে সাবধান করা হয়েছিল দুর্ভিক্ষ আসছে, তারা কর্ণপাত করেনি, উল্টে চার্চিল এক ভয়ঙ্কর মন্তব্য করে ভারতের মতো দেশে দুর্ভিক্ষকে স্বাভাবিক বলে প্রমাণ করেন! তিনি বলেন "ভারতীয়রা খরগোশের মতো বাচ্চা জন্ম দেয়, এই এতো জনসংখ্যাই দায়ী দুর্ভিক্ষের জন্য!" তিনি আরো বলেন "কোথায় দুর্ভিক্ষ? দুর্ভিক্ষই যদি হবে, তাহলে গান্ধী এখনও বেঁচে আছে কেন?"
তীব্র অনাহারে সব হারিয়ে গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ কলকাতায় ভিড় জমান। তাদের এই বিপুল সংখ্যার কাছে লঙ্গরখানায় খাদ্যের যোগান ছিল অতি সামান্য। শহরের আকাশ বাতাস ভরে ওঠে "ফ্যান দাও, ফ্যান দাও আর্ত চিৎকারে", ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে মারামারি করে খাবার খেতে দেখা যায় মানুষকে! ফুটপাত ভরে যায় অনাহারী মানুষের মৃতদেহে।
আর সমস্ত কঠিন পরিস্থিতিতে যা হয়, এবারও তাই হলো, সবচেয়ে কোপ পড়লো মেয়েদের ওপর! যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা দেশভাগ মেয়েরাই যে সহজলভ্য। পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে যেকোনো ছুতোয় মেয়েদের ভোগ করা যায়, সুযোগ নেয়া যায় অসহায়তার। অনাহারী সেই পুরুষ গুলোকে লড়তে হয়েছে ক্ষুধার সাথে, রোগের সাথে, আর মেয়েদের এসবের সাথে লড়াইয়ের পাশাপাশি লড়তে হয়েছে লোলুপ হায়নাদের সাথে। কোলের শিশুকে নিয়ে বিনিদ্র রাত কেটেছে উপোসি মায়েদের।

সংকটকাল শিল্পের জন্ম দেয়। '৪৩ এর দুর্ভিক্ষের আয়নার কাজ করেছে একঝাঁক গল্প উপন্যাস নাটক সিনেমা। এমনই এক অগ্নিক্ষণের নাটক নবান্ন। বিজন ভট্টাচার্যের লেখনীতে এক জ্বলন্ত দলিল...
নবান্ন-র প্রথম প্রকাশ ধারাবাহিকভাবে অরণি পত্রিকায় ১৯৪৩ সালে। পরিচয় পত্রিকায় লেখা হয় :- "লেখক নতুন নাটক রচনা করেছেন নবান্ন। তা চার অঙ্কের নাটক, তাতে অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা। অরণি-তে তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তুও এই মন্বন্তর, মন্বন্তরের ক্রমিক প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যসাহিত্য সংবন্ধে লেখক যেরূপ দৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, নবান্ন-এ তার স্ফুরণ দেখছি। আশা করে থাকব এর অভিনয়ের জন্য। কারণ, আশার কথা আছে। বাংলার লেখকদের মতো অভিনয়শিল্পীরাও অনেকেই গণনাট্য সংঘের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই ছিলেন এঁদের সভাপতি। গণনাট্যের মধ্যে তাঁরাও একটা নূতন সম্ভাবনা দেখছেন। সাহিত্যিক ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের এই শুভ সম্মেলন ঘটলে বাংলার নাট্যকলার এই চতুর্থ যুগের সূচনা ব্যর্থ হবে না। আমরাও দেখব এবার বাংলা-নাট্যকলা বাঙালির নাট্যকলা হয়ে উঠল।" ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (আইপিটিএ) প্রযোজনায় নবান্ন নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে, শ্রীরঙ্গম (পরবর্তী কালে যা বিশ্বরূপা নামে পরিচিত হয়) মঞ্চে। শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্য যৌথভাবে নাটকটি পরিচালনা করেন।
অগ্নিযুগের এই নাটক আবারো মঞ্চায়ন শুরু করেছে নান্দীকার। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অভিভাবকত্বে, সোহিনী সেনগুপ্ত ও অর্ঘ্য দে সরকারের যৌথ নির্দেশনায় মঞ্চে প্রাণ পাচ্ছে প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী, মাখন, দয়াল, হারু দত্ত, কালিধনের মতো বাস্তবের মাটি থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলো। অনাহারী শুকনো মুখগুলোর অনন্ত সংগ্রাম যেমন দর্শকাসনে বসে চোখে জল আনলো, তেমনই হারু দত্ত, কালিধনরা ক্রোধে অস্থির করলো। মনেই হলো না যা দেখছি তার প্রেক্ষাপট আট দশক আগের বাংলা। হারু দত্ত, কালিধনরা তো আজও নানা রূপে, নানা বেশে শুষে খায় প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জনদের রক্ত, রাধিকা, বিনোদিনীরা আজও লাঞ্ছিত হন এদের ক্ষমতার দম্ভের হাতে! শেষ অঙ্কে সুদিনের সুরে মাখা গান গুলো রোমাঞ্চ জায়গায়, রাতের শেষে ঠিকই সূর্য হাসে, শেষ দৃশ্যে একদা জনশূন্য আঙিনায় যখন নবান্নের আঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে, সেই গন্ধ এসে ধরা দেয় দর্শকাসনেও... আনন্দের মাঝেও আজীবন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল মানুষগুলোর সংগ্রাম থামে না, লুকিয়েই থাকে আশঙ্কা আর শোষণের লেশ, তারই মাঝে দয়ালের শেষ সংলাপে লড়াই জারি থাকে হাসিমুখে — জোর প্রতিরোধ... জয় প্রতিরোধ...
"আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।।
এছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।"
গত রবিবার ৬ ই জুলাই গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হলো নান্দীকারের নতুন প্রযোজনা নবান্নের চতুর্দশ শো। প্রেক্ষাগৃহ ছিল প্রায় পূর্ণ। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী মন জয় করলেন। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করলেন শম্ভুনাথ সাউ (প্রধান সমাদ্দার) ও অর্ঘ্য দে সরকার (কুঞ্জ সমাদ্দার)। শিশুশিল্পী মাখন অনবদ্য। আবহে শুভদীপ গুহ, মঞ্চ শয্যায় দেবব্রত মাইতি, অঙ্গবিন্যাসে দেবকুমার পাল, আলোয় সাধন পাড়ুই, আবহ প্রক্ষেপণে অধীর গাঙ্গুলি, রূপ সজ্জায় নৃপেণ গাঙ্গুলী ও মলয় দাস প্রত্যেকেই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। নাটক শেষে অন্যতম নির্দেশক অর্ঘ্য দে সরকার বললেন, গতবছর আগস্ট থেকে যখন এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়া শুরু হলো, তখন ওনারা ভেবেছিলেন এতো বছর পরে কি নাটকটির প্রাসঙ্গিকতা থাকবে? যত দিন যাচ্ছে উপলব্ধি হচ্ছে নাটকটি যেন আজকের দিনের সাথেও একাত্ম হয়ে পড়ছে। এভাবেই তো শিল্প যুগোত্তীর্ণ হয়।
নাটকটির রেশ কাটতে সময় লাগবে। কানে বাজবে ফ্যান দাও, ফ্যান দাও - করুণ আকুতি। নান্দীকারের উপস্থাপনাকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা। ২৯ জুন গেলো নান্দীকারের ৬৬ তম জন্মদিন। তাদের রথের চাকা এগিয়ে চলুক এমন অসাধারণ সব প্রযোজনার চাকায় ভর করে। অনন্ত শ্রদ্ধা নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে।

 লিখেছেন :
লিখেছেন : 



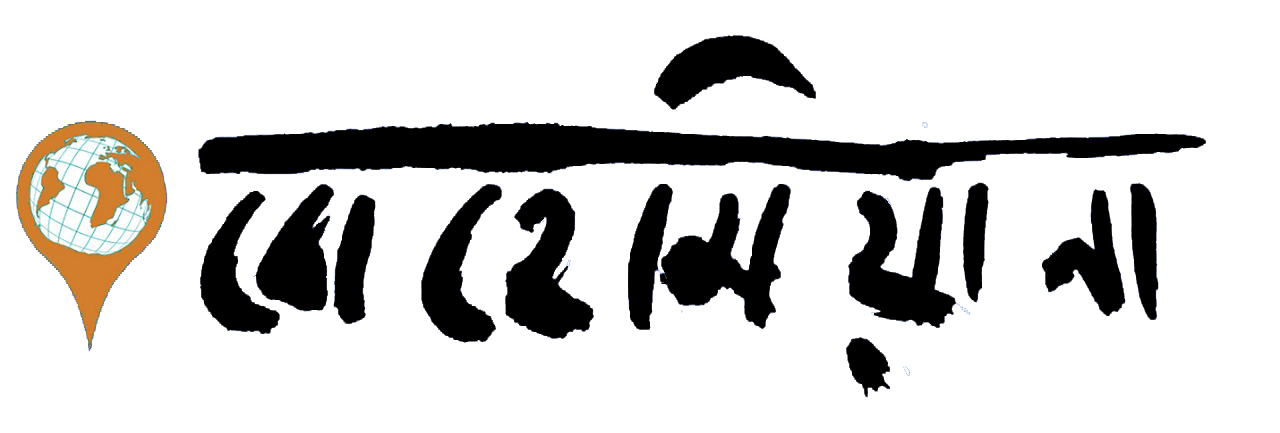
.png)