তবে একটা ছোট্ট গল্প বলি শুনুন। আমরা না ছোট্টবেলায় খুব ভোর ভোর খেলতে যেতাম। তা কখনও ফুটবল, কখনও ক্রিকেট; খেলার প্রতি অদ্ভুত ঝোঁক ছিল। ফজরের আজান দিলেই নানি ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন,‘ভাই উঠ, খেলতে জাবিন্যা?’ ভোর বেলায় খেলতে যেতাম আর মাঠের পাশে বড় রাস্তা। চাষিরা লাঙল আর গরু নিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত, আওয়াজ আসতো ‘হুরররর...হুট...হুট.. ওই বাইয়ে বাইয়ে বাইয়ে ওই ডাইহনে ডাইহনে,ঠিক ক্যোরে চল ক্যানেরে শালোরা, এব্যার খাবি পাচুনের বাড়ি।’
রাস্তায় অসংখ্য মানুষ সাইকেলে চাল নিয়ে শহরের দিকে পাড়ি দিত। মাঝে মাঝে আমাদের বল যখন রাস্তায় চলে যেত আমরা হাঁক দিতাম, ‘ওই চেল্যাকি,বলটো দ্যাও’। সাইকেল থামিয়ে অনেকেই বলটা আমাদের দিয়ে দিতেন। ওহ! বলতে বলতে ভুলেই গেছিলাম, ‘চেল্যাকি’ জিনিসটা আপনারা বুঝবেন না। ‘চেল্যাকি’ একটা আঞ্চলিক শব্দ। আচ্ছা বেশ। বিষয়টি আরও বিস্তারিত বলি, ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে মুর্শিদাবাদের কান্দি,নবগ্রাম, খড়গ্রাম পর্যন্ত অনেক নদী, খাল, বিল। এই নদীর পাশের জমিগুলোতে প্রতিবছর পলি জমে দারুণ ধান চাষ হয়। এই ধানগুলো কিনে নিয়ে বা কারোর কারোর নিজের জমির ধান নিয়ে যারা বাড়িতে ধান সেদ্ধ করে, ধানভাঙা কলে ছাঁটাই করে, সেই চাল যখন শহরে নিয়ে গিয়ে যারা বিক্রি করত, তাদের আমরা ‘চেল্যাকি’ বলি।
আমাদের এলাকায় মূলত ধানই প্রধান ফসল। ধান চাষই প্রধান চাষ। সারা বছর সবুজ মাঠ, শুধু ধান আর ধান। গোটা মাঠ জুড়ে ধান পাকলে মনে হতে চারদিক যেন সোনালি রঙে ছেয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় খাবারও যে ভাত। আহা! ভেতো বাঙালি বলে কথা, লোকে বলেনা ‘মাছে-ভাতে বাঙালি’, ঠিক তেমন! যাই হোক আবার গল্পে ফিরে আসি, ক্রমে আমরাও বড় হতে শুরু করলাম, খেলার প্রতি ঝোঁকও কমল, তার বদলে টিভি দেখার প্রতি নেশা বাড়লো। আর এখন টিভি বাদে স্মার্ট ফোন। অদ্ভুত ভাবে চেল্যাকিদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখতে পেলাম। চেল্যাকিরা আস্তে আস্তে কোথায় হারিয়ে গেল। না, মানে, মানুষগুলো হারিয়ে যাইনি, কিন্তু পেশা হারিয়ে গেল। আসলে এই গল্পটা বলতে গিয়ে অদ্ভুত কান্না পায় জানেন। আসলে এটা ঠিক গল্প নয়। গল্প হলেও সত্যি। একটা সত্যিকারের ইতিহাস।
এই ইতিহাস লিখতে গিয়ে কান্না পায়, এ তো আমার আপনজনের কথা। যাই হোক তা হলে বাকিটা বলি, আস্তে আস্তে চেল্যাকি হারিয়ে গেল। অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়ে ফেলল। বড় বড় পুঁজি বিনিয়োগ হল, বড় বড় রাইসমিল হল। আর মানুষ কাজ হারাতে শুরু করল। এলাকায় মজুতদার তৈরি হল। আর চালের বাজার নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে চলে গেল। আগের মতো বড় বড় রাইস মিলের সাথে চেল্যাকি আর পাল্লা দিতে পারল না। জমির ক্ষেত্রেও যদি বলি, তা হলে জমিতে চাষ করে সেই ভাবে লাভ নেই। কারণ যাদের অল্প জমি আছে, তাদের চাষ করে আসল টাকা থেকে কিছু বেশি টাকা আসে। বলতে গেলে সেই ভাবে লাভ নেই। কারণ ধানের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করে রাইস মিলের মালিক আর মজুতদাররা। সরকার যে ধান কেনে সেখানেও তাঁবেদারি করার ব্যপার আছে। যা প্রতিটি সরকার করে আর কী। চাষির হাতে চাষ ছাড়া কিছুই নেই। যারা একটু বেশি চাষ করে অথবা নিজেই সব কাজ করে, তাদের ক্ষেত্রে তাও কিছুটা মুনাফা হয়। কিন্তু যদি মুনিষ (শ্রমিক) দিয়ে যারা কাজ করায়, তাদের ক্ষেত্রে কিছুই থাকে না। ফলত যাদের অল্প জমি আছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজে না চাষ করে ভাগচাষে দিয়ে দেয়। লাভ থাকলে কেউ নিশ্চয় ভাগ চাষে দেবে না। লাভ নেই বলেই কিছু ধানের বিনিময়ে নিজের জমি অন্যদের চাষ করতে দেয় কেউ কেউ। যাঁরা ভাগচাষ করেন, তাঁরা সাধারণত নিজে খেটেই সমস্ত কাজ করেন। সবটা মুনিষ (শ্রমিক) দিয়ে কাজ করালে তাঁরাও হয়তো ভাগচাষ করতেন না।
এর মাঝে আরও কিছু জিনিস ভুলেই গেছিলাম। সেটাও বলি, চাষের কাজে লাঙল ব্যবহার করা হত। এই পেশায় গ্রামের অনেক মানুষ যুক্ত থাকতেন, সেই কাজেও ভাটা পড়লো। কারণ লাঙল দিয়ে চাষ একটু সময়সাপেক্ষ। একটা ট্র্যাক্টরে যা হয়, তা লাঙলের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রযুক্তি আমাদের উন্নত করছে ঠিকই, কিন্তু প্রচুর মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে সেই ছোট থেকেই একই কথা শুনে আসছি। প্রতিটি চাষা (কৃষক) সেই ছোটবেলায় যা বলেছিলেন, আজও তা-ই শুনছি, ‘চাষ করে কোন লাভ নেই’।
আমাদের এলাকায় একজন কৃষকের মুখেও এই কথাটা শুনিনি যে, ‘আমার ছেলেও কৃষক হবে’। আমার কৌতূহল হয়। প্রশ্ন জমে।
একজন ডাক্তার তাঁর ছেলেকে ডাক্তার করতে চায়। একজন উকিল ভাবে তার ছেলে যেন উকিল হয়। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে একমাত্র কোনও চাষি চায় না যে তার ছেলে চাষি হোক।
কেন?
তার প্রচুর কারণ আছে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে ‘এই নেতা আসে ওই নেতা যায়, জামাকাপড়ে রঙ বদলায়স দিন বদলায় না’।
হ্যাঁ, এটাই সত্যি। আমাদের মুখে যাঁরা অন্ন তুলে দেন, যাঁদের ঘাম, রক্ত প্রতিটি শস্যদানার গায়ে লেগে থাকে, তাঁদের জন্য কেউ কোনও দিন কিছুই করেনি। হাজার হাজার কোটি টাকার কর্পোরেট ঋণ মকুব হয়ে যায়। কিন্তু কোনও চাষার ঋণ মুকুব হয় না। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, গেরুয়া সরকার আসে। তারা বারবার কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না।
ভারতের মানুষের আর কী দেখতে বাকি আছে? প্রতিদিন দেশের কোনও না কোন প্রান্তে কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। কেউ বা ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করছে। আমরা কি দেখিনি বলুন তো? আমরা যন্তরমন্তরে মৃত কৃষকের মাথার খুলি নিয়ে আন্দোলন দেখেছি। আমরা তেভাগা দেখেছি। আমরা এই হাড়হাভাতের দলকে লং মার্চ করতে দেখেছি। তাদের পায়ের রক্তের দাগ দেখেছি, ফেটে যাওয়া পা দেখেছি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর অথ্য অনুসারে, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভারতে সর্বমোট ৩২১৪০৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অনেক গবেষকদের মতে, এই সংখ্যা আরও বেশি। বর্তমান সরকারের আমলে কৃষক আত্মহত্যা সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে। দেশের মোট আত্মহত্যার মধ্যে কৃষক আত্মহত্যা ১১.২%।
বর্তমান সরকারের আনা কৃষি বিল নিয়ে দেশজুড়ে কৃষক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। গর্জে উঠেছে দেশের ছোট, বড়,মাঝারি সব ধরনের কৃষক।খু ব গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যাবে, বর্তমান সরকার কর্পোরেট হাঙরদের হাতে কৃষি ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দেশের কৃষকদের চরম সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে, শুধুমাত্র কিছু পুঁজিপতির জন্য। নতুন কৃষি বিলে সরকারের বেঁধে দেওয়া ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যা পেতেন কৃষকরা, সেটাও হয়তো আর পাবে% না। এই বিল দেখে নীলকর সাহেবদের কথা মনে পড়ে যায়। কারণ এই বিল চুক্তিভিত্তিক চাষের পথ প্রশস্ত করবে। ফসল মজুত করার সরকারি নিয়ন্ত্রণ লোপ পাবে।
যাই হোক, কৃষি এবং কৃষক নিয়ে এই সব অতীতেও দেখেছি, বর্তমান সরকারের আমলে আরএ ভয়ঙ্কর ভাবে দেখছি, আবার পরদিন সকালে ভুলেও গেছি। আর ওই যে আমাদের ‘হাম দো হামারা দো’ নীতি, এই নীতি নিয়ে সব ভুলে গেছি। আমরা বুঝতেই পারি না, প্রতিদিন আমরা মরে যাচ্ছি। আর প্রতিদিন যে কৃষক মরছে তার দায় আমার, আপনার গোটা দেশবাসীর। এই দায় এড়াতে এড়াতে একদিন আমাদের পেশায় যখন কোনও কোপ পড়বে সে দিন দেখব, সবাই মরে গেছি। আমাদের শরীর আছে, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক কারওর কাছে বন্ধক রাখা আছে।
এই রে! বলছিলাম আমাদের এলাকার গল্প, আর তা বলতে গিয়ে অনেক দুরে হারিয়ে গেছিলাম।
তবে এ বার পরেরটা শুনুন।
এই যে এত মানুষ বেকার, আর অন্যদিকে ফসলের দাম নেই— এর ফলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে দেশের বিভিন্ন দিকে পাড়ি দিতে লাগল। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হিসেবে। কারণ বেকারত্বের জায়গাটা ঠিক করতে গেলে কলকারখানা দরকার, যা আমাদের মুর্শিদাবাদ নেই। অসংগঠিত শ্রমিক হিসেবে বেশির ভাগ মানুষকে আগে দেখতাম মুম্বাইয়ে যেতে, এখন কেরালাতেও যেতে দেখি। বেশির ভাগই নির্মাণ শ্রমিক। পরবর্তী কালে সেই কাজেও যখন ভাটা পড়ে, অনেকে তখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যেতে শুরু করে। ওই যে আগেই বলেছিলাম, ‘চেল্যাকি’। এই মানুষগুলো সব মধ্যপ্রাচ্যের অসংগঠিত শ্রমিক হয়ে গেল। ভিসা-পাসপোর্ট বানিয়ে ভিনদেশে পাড়ি। ঘর সংসার ছেড়ে শুধু পেটের জন্য কেউ রাস্তার কাজ, কেউ ড্রাইভিং, কেউ মরুভূমিতে উট চরানো, আবার কেউ বা তপ্তরোদে খেজুরের বাগানে কাজ নিল।
আসলে মরুভূমির রোদ গায়ে না পড়লে এই ব্যথা লিখে বোঝানো যায় না! কষ্ট লেখা বড় সহজ নয়। কিছু রোজগারের জন্য মানুষ কী না করে! অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তো নিদিষ্ট কোনও কাজ হয় না, ওখানে গিয়ে যা বলে তাই করতে হয়। অনেকেই বলে, মুর্শিদাবাদ শ্রমিকদের জেলা। একটুও ভুল বলে না। এই জেলার প্রচুর মানুষ শ্রমিক। আমার প্রচুর প্রিয়জন শ্রমিক। আর প্রতিদিন সেই শ্রমিকদের মধ্যে কেউ না কেউ লাশ হয়ে ফিরে আসে। আমার আপন জনের লাশ। কোনও ভিনদেশ থেকে অথবা এই দেশেরই কোনও শহর থেকে লাশ হয়ে ফিরে আসে। তাদের ব্যথায় মলম দেওয়ার কেউ নেই। চাষের মূল্য চাষাই বোঝে। আমরা যারা সেই অন্ন ভোগ করি, তার মূল্য কেউ বোঝে না। আমরা শুধু তাদের যাপন নিয়ে সিনেমা করি, গল্প লিখি, থিসিস লিখি। নাম হয়, রয়্যালিটি পাই। কিন্তু তাদের পাশে থাকি কি? তাদের জন্য রাস্তায় নামি কি?
তাদের ইতিহাস যুগ যুগ ধরে একই ধারায় বইছে। আসলে এই গল্প শুধু আমাদের নয়, ভারতের প্রতিটি প্রান্তে খোঁজ নিলে দেখা যাবে সবই এক। ভারতের প্রতিটি কৃষক একই অবস্থায় আছে। অসহায় অবস্থায় সব চাষাই দিন কাটাচ্ছে। আর ভাবছে, সামনের দিনে কোন অজানা রঙের সরকার এসে তাদের দিন বদলে দেবে! আর সেই দিন হয়তো সেই চাষা তার সন্তান-সন্ততিকে বলবে পড়াশোনা শেষ করে তোরাও চাষাই হবি।গল্পটা আজ হয়তো শেষ করতে পারলাম না, বাকিটা সেই দিনটা দেখে শেষ করবো।
লিখতে লিখতে ফজরের আজান শুরু হয়ে গেল,আবার নানির কথা মনে পড়লো। বেঁচে থাকলে যে মানুষটা হয়তো বলে উঠত, ‘ভাই উঠ, খেলতে জাবিন্যা? খেলে তাড়াতাড়ি আসিস, মুনিষদের ল্যেগে ভাত লিয়ে যাবি, আমি ড্যাইল ব্যাইটছি। বড়া আর বাসিভাত টিপিনক্যারে ভোর্যে লুঙ্গি দিয়ে বেঁইন্ধে রাইখবো। আড়হাই পাক নাঙল দিলে অদের ভোক লেগে যাই’।
আবার রাস্তায় আওয়াজ পেতাম ‘হুরররররর...হুট...হুট… ওই বাইয়ে বাইয়ে বাইয়ে, ওই ডাইহনে ডাইহনে, ঠিক ক্যোরে চল ক্যানেরে শালোরা, এ ব্যার খাবি পাচুনের বাড়ি..’

 লিখেছেন :
লিখেছেন : 


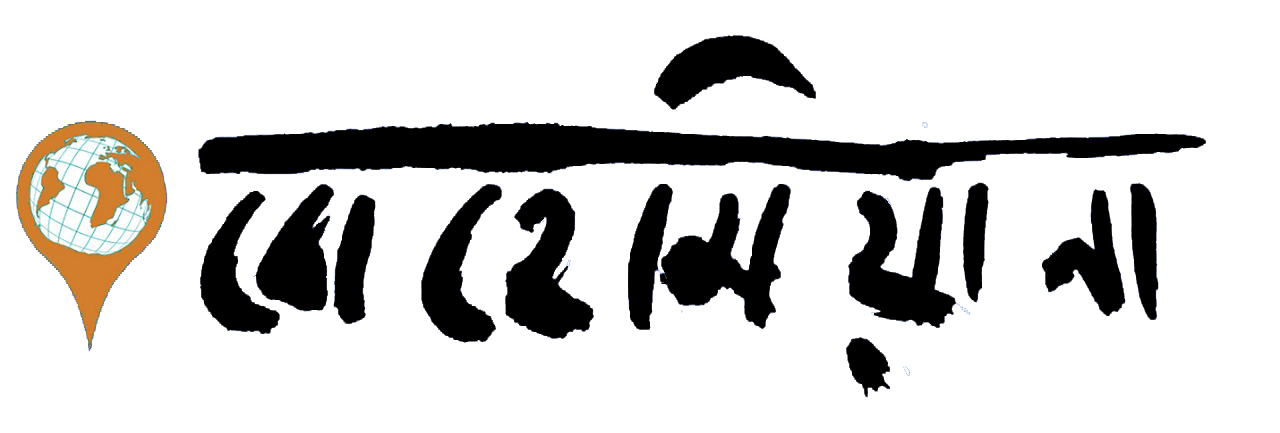
.png)