ছবি-Life Is Beautiful
পরিচালনা -রবার্তো বেনিগ্নি
প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালে গোটা মানব-সভ্যতা এক মর্মপীড়িত ,যন্ত্রণাক্লিষ্ট ডিস্টোপিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছে। অতিবাহিত করেছে দু:স্বপ্নের কাল।সাধারণ মানুষের ছোট ছোট স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে জ্বলন্ত সময়ের লাভাস্রোত,সেই ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত ছাইগাদার ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অবিনশ্বর মানবজীবন ও তার মিউটেটেড ডালপালা। সে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল তার পুরানো ধারণার ধারাপাত ও মূল্যবোধ। ফ্যাসি-নাজিবাদের উত্থান ও তার অবিশ্বাস্য নৃশংসতার ঝাঁকুনি সভ্যতার স্নায়ুকেন্দ্রে যে তরঙ্গ প্রেরণ করেছিল তার অভিঘাত শেষ তো হয়ইনি, বারবার নতুন নতুন হিংস্রতার প্রকরণে সজ্জিত হয়ে সংকট কালের দ্যোতক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে অনেকটা দূরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে ১৯৯৭ সালে রবার্তো বেনিগ্নি যখন ইতালিতে life is Beautiful (la vita è bella) ছবিটি তৈরি করছেন তখন নব্য-উদারবাদের বিকাশকাল । প্রবল জনপ্রিয়তা পায় ছবিটি। তিনটি অস্কার পুরস্কার ও বিদেশি ভাষার শ্রেষ্ঠ ছবির শিরোপা লাভ করে। তখনো মানুষ ভাবেনি আর দশবছরের মধ্যে আসবে অর্থনৈতিক মন্দা এবং তৎ পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে চরম-দক্ষিণপন্থী শাসকের উগ্র উত্থান ঘটবে। নানা দেশে তা বাঁক নেবে নব্য-ফ্যাসীবাদে।হলোকস্টের যৌথ স্মৃতি ও দহনের মর্মস্থলে আঘাত করেছিল ছবিটি। পপুলিস্ট রিডাকশন ও নাৎসি বীভৎসতাকে খাটো করে দেখানোর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ছবিটিতে ব্যক্তি মানবের ত্যাগ ও বেঁচে থাকবার দুর্মর আশাকে সাধারণ দর্শক চোখের জলে গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ছবিটিকে তাই আরেকবার ফিরে দেখা।
কাহিনিসূত্রঃ
ছবিটির পরিস্কার দুটি ভাগ। একটি কমেডি,রোমান্স ও স্যাটায়ার। অন্যটি হলোকস্ট, কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প এবং হত্যা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে ব্যক্তি মানুষের নাছোড় আশার এক অভিনব লড়াই।
নাজি ক্যাম্পের অন্ধকার থেকে বেঁচে ফেরা শিশু জোসুয়ার পরিণত বয়সের স্মৃতিচারণ থেকে কাহিনির বিস্তার। ছবিতে আমরা পরিণত জোসুয়া কে দেখিনা। শুধু তার ভয়েস ওভার যেন বা ইতিহাসের কন্ঠস্বর হয়ে ১৯৩৯ এর ইতালির আজেরাতে দর্শককে টেনে নিয়ে যায়।
গুইদো,জোসুয়ার বাবা,আমুদে খোশমেজাজী ইহুদী যুবা, সম্পন্ন পরিবারের স্কুল শিক্ষিকা ডোরার প্রেমে পাগল ও তাকে পাবার জন্য অজস্র উদ্ভট উদ্যোগ নেয় সে। শেষ অবধি সফল হয়,বিবাহ হয় ও জোসুয়ার জন্ম হয়। ছবির এই অংশ নিখুঁত স্ল্যাপস্টিক কমেডি,খানিক চ্যাপলিনোচিত। পরবর্তীতে বলিউডের বহু রোমান্সকাহিনি এই অংশের দৃশ্য-পরিকল্পনা ও মোচড় আত্তীকৃত করেছে। কিন্তু যা সে পারেনা তা হল উচ্চকিত রোমান্টিক কমেডির ভিতরে ভিতরে রেসিস্ট কর্তৃত্ববাদী সমাজের অন্ধকারগুলি গুঁজে দিয়ে দিয়ে একটি আলো-আঁধারি প্রতিবাদ নকশা এঁকে তোলা।
১৯৩৮ এ মুসোলিনি চালু করে ইহুদি-বিরোধী আইন।স্কুল-কলেজ,পেশা এবং সম্পত্তির অধিকারের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ হলেও গণহারে ইহুদিদের কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো শুরু হয়নি। এই রকম এক সময়ের ক্যানভাসে গুইদো-ডোরার যৌথ জীবনের শুরু। জোসুয়ার জন্ম।চারদিকে ইহুদি-বিদ্বেষের বিষাক্ত আবহে জোসুয়া বড় হতে থাকে।
১৯৪৩ এ জার্মান অধিগ্রহণের পর থেকে ইতালির রাজনৈতিক অবস্থা আরো চরম আকার নেয়। ব্যাপক হারে কমিউনিস্ট ও ইহুদি মানুষকে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে চালান করা শুরু হয়। ছবির কাহিনীও নেয় বিপদজনক মোড়। গুইদোর পুরো পরিবার কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়।ছোট্ট জোসুয়াকে বীভৎসতার অনুভব থেকে রক্ষা করতে এবং প্রাণে বাঁচাতে ক্যাম্পের জীবনটিকে একটি ‘গেম’ বলে বর্ণনা করে গুইদো। যত পরিশ্রম, তত পয়েন্ট,আর সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেলে পুরস্কার একটি আসল ট্যানক।গুইদো নাজিদের হাতে মারা যায়। তখন যুদ্ধে হারছে জার্মানি।আমেরিকান সেনা ক্যাম্পে প্রবেশ করে। ছোট্ট জোসুয়া দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ট্যানক।
প্রকৃতপক্ষে এই ‘গেম’ শব্দবন্ধ অনুচ্চারিত বৃহৎ রাজনীতির ভাবনা উস্কে দেয়।
ছবিটিকে ঘিরে প্রশংসা ও বিতর্ক আসলে উন্মুক্ত করেছিল বিংশ-শতকের শেষভাগে ফ্যাসিজম ও গণহত্যাকে ঘিরে ইউরোপীয় মননে জেগে থাকা সাংস্কৃতিক উদ্বেগ ও শংকা। ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ ও সোভিয়েতের ভাঙণকালে শাসনক্ষমতায় না এলেও ইতালি জার্মানি, ফ্রান্স,স্পেইন ও পর্তুগালে নব্য-ফ্যাসিবাদি পার্টিগুলির নতুন করে আদর্শিক সংহতিকরণ এই উদ্বেগের জননী।
দৃশ্যনির্মাণঃ
রোমান্টিক স্ল্যাপ্সটিক কমেডি থেকে গাঢ় ট্র্যাজেডিতে ছবিটি পিছলে যায় অতি নাটকীয়তা ছাড়াই —মসৃণ নিস্পৃহতায়। বাস্তবিক, সাধারণ ব্যক্তি মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের দন্ডাজ্ঞা নেমে আসবে কখন,কোন পথে তা সে ঠিকভাবে আঁচ করতে পারে না। সে দীর্ঘ স্মৃতিবাহিত কিছু মূল্যবোধে আক্রান্ত থাকে,ভাবে অতবড় বিপদ আমার সাথে হবেনা। যে দৃশ্যের মধ্য দিয়ে জোসুয়ার জন্মদিনের পার্টি থেকে গুইদো ও জোসুয়াকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়,সেই দৃশ্য আমরা দেখতে পাইনা। ডোরার চোখ দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া জন্মদিনের আয়োজন ও সংসারটিকে দেখি। কমেডি ও ট্র্যাজেডির এক টোনাল দুলুনি দর্শককে অস্থির করে রাখে।কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিচালক তৈরি করেন এমন সব দৃশ্য যাতে হাসি আসতে চায়,কিন্তু তখনই তা চোখের জলে চাপা পড়ে।
অন্যান্য হলোকস্ট ছবির থেকে এ ছবির প্রস্থানবিন্দু এইখানে।
ছবির প্রথম অংশে সূর্যকরোজ্জ্বল টাসকান ল্যান্ডস্কেপ, রঙের সমারোহ।এই বর্ণোজ্জল প্রেক্ষাপটের উপরে কালি ঢেলে দিয়ে আসে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প। অসম্পৃক্ত ধূসর। এর সাথে খুব অদ্ভুত বৈপরীত্যে বাজে নিকোলা পিওভানির কাব্যিক আবহ যাকে অনেক সমালোচক ‘'পলিটিকাল রিডাকশন” বলেছেন।কিন্তু ক্যাম্পের নৃশংস নিষ্ঠুরতার সাথে এই সঘাত বৈপরীত্য তৈরি করে একটি মোক্ষম প্রশ্ন।ঐতিহাসিক নৃশংসতা যৌথ স্মৃতিতে কীভাবে ক্রিয়া করে?নিছক ফেবলের(fable) মত? নয়ত নতুন করে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসে কেন?
রাজনৈতিক মাত্রাগুলিঃ
ছবির প্রথম অংশে একটি ক্লাসরুম প্যারডি দৃশ্যে গুইদো ব্যঙ্গে ব্যাঙ্গে ফালাফালা করে ফেলে মুসোলিনির ইহুদিবিদ্বেষী আইন আর চরম কতৃত্ববাদী রীতি-প্রথাগুলি। টেবিলের উপরে উঠে গুইদোর বক্তৃতা অনিবার্যভাবে উপস্থিত করে ‘গ্রেট ডিক্টেটর ছবির’ অমোঘ রেফারেন্স।ফ্যাসিস্টদের ছদ্ম-বিজ্ঞান ও তার চূড়ান্ত অ্যাবসার্ডিটিকে চ্যালেঞ্জ করে গুইদোর কমেডি।ছদ্ম-বিজ্ঞানের বাড়-বাড়ন্ত দিয়েও চিনে নেওয়া যায় সময়কে। আর এইকারণেও ছবিটি চিরচেনা হয়ে ওঠে।
ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে পরিচালক ঠিক সরে যাননি,নিয়েছেন একটি কৌশলগত ভিন্ন রাস্তা। গ্যাসচেম্বারের সমূহ মৃত্যুর বদলে তিনি ব্যক্তি-মানবের এক অনন্য প্রতিরোধী অবয়ব আঁকতে চেয়েছেন।আমরা নিজেরা আজ জানি দৃশ্য-শ্রাব্য মিডিয়া পুন:পুন: ব্যবহার করে মানব-মানসে মৃত্যু আর রক্তের অভিঘাতকে কোন পর্যায়ে হ্রাস করে এনেছে।একটি অনির্বচনীয় দৃশ্যের কথা না বললেই নয় -যেখানে দেখি গ্যাসচেম্বারে প্রেরিত হবে এমন এক মেয়ের সঙ্গে আসা বিড়ালছানাটি জামাকাপড়ের স্তুপে একা একা ঘোরে।গ্যাসচেম্বারের দৃশ্যের প্রয়োজন এখানে স্তব্ধ হয়ে যায়।
নায়ক গুইদোর লড়াই এক আশাবাদী পিতার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ভিন্ন ধরণের প্রতিরোধ। শুধু মৃত্যু থেকে নয়,ঘৃণা থেকেও। ক্যাম্পে আসার আগে থেকেই সেই লড়াই লড়ছে সে।ডোরা ইহুদি নয়।কিন্তু ইহুদি-বিদ্বেষের আবহেই সে ভাল বেসেছিল গুইদোকে।সুযোগ থাকলেও সে মুক্তি নিতে চায়নি।সাথী ও সন্তানের পিছু পিছু ক্যাম্পে গেছে। যেমন সাধারণে করে। আর জোসুয়া এ ছবির চোখ।যার শৈশব স্মৃতিতে ক্যাম্প একটি ‘গেম’' আর পরিণত বয়সে সে জেনেছে হলোকস্টের প্রকৃত বীভৎসতা। পাঠ-অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির মাঝখানে একটি ফিল্টার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পিতা গুইদো,জোসুয়ার কাছে তাই-ই তার পিতার ‘'আত্মত্যাগ”।
অবশ্যই তীব্র রাজনৈতিক স্পষ্টতা ও অভিঘাতের প্রশ্নে পোলান্সকির ‘পিয়ানিস্ট’ বা নেমিসের ‘'সন অব সলের” সাথে এর তুলনা চলেনা। শেষদৃশ্যের “আমেরিকান ট্যানক’’ অস্কারের পথ সুগম করেছে এ সমালোচনাও আছে। তবে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবিরত শ্লেষ ও অবজ্ঞাই ছবিটিকে সাধারণ হৃদয়ের কাছে নিয়ে আসে। মানুষ যখন সবল সংগঠিত প্রতিরোধ পারেনা,এই অবজ্ঞা ও শ্লেষই তার অস্ত্র।গুইদো তার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।দর্শকের মনে গেঁথে যায় হাসিখুশি গুইদোর প্রেম,সংসার আর বিপর্যয়।মনে থেকে যায় ডোরার সাহস। তীব্র অত্যাচারে পিষ্ট হতে হতে ছেলের সামনে কান্না ঢেকে গুইদোর হোহো হাসি। মনে থেকে যায় মৃত্যুর আগেও জোসুয়ার সামনে দিয়ে দৃঢ়পায়ে গুইদোর মার্চ করে চলে যাওয়া।
আসলে ‘life is beautiful’ উলটো-টা বলে। জীবন অতও সুন্দর নয়। কিন্তু সুন্দরের জন্য,একটু সুষমতার জন্য ব্যক্তি মানুষের প্রতিদিনের লড়াইয়ে কল্পনা জোগানোর দায় এ ছবি নিয়েছে।সেইসঙ্গে ফ্যাসি-নাজি নৃশংসতার দু:খ-যন্ত্রণাময় স্মৃতিভারকে সে খানিকটা ইতিহাসছিন্ন উপকথা করে তুলেছে বটে কিন্তু মানবের যা কিছু আবহমানের সম্পদ ভালবাসা,আশা,প্রতিরোধ ও অশ্রুজল -তার শৈল্পিক চিহ্ন সে তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে।

 লিখেছেন :
লিখেছেন : 



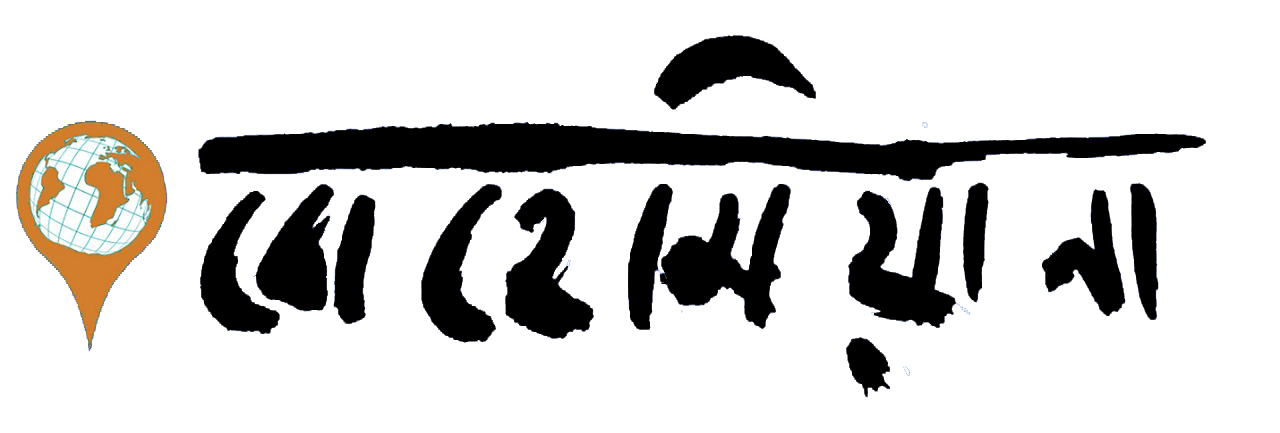
.png)