ভারতীয় রাষ্ট্রে চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত ন্যারেটিভ নির্মাণের প্রধান অস্ত্র। এই ন্যারেটিভ আজ নিরপেক্ষ থাকে না; বরং একটি বিশেষ আদর্শ ও শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। একবিংশ শতকে এসে যখন ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ধর্ম, জাতিসত্তা ও জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম সংজ্ঞা প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে সেই জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক বাহক। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে ‘দি কেরালা স্টোরি’ নামক একটি চলচ্চিত্র, যা ২০২৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে ঘনঘোর বিতর্কের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। এই বিতর্ক শুধুমাত্র সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, বরং রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার গূঢ় খেলার প্রতিফলন।
সিনেমাটির মুখ্য অভিযোগ হচ্ছে এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ‘ইসলামোফোবিয়া’ ছড়ায়। কেরালার মতো একটি প্রগতিশীল, শিক্ষিত এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের রাজ্যকে ‘ধর্মান্তরকারী জেহাদি গোষ্ঠী’-র অভয়ারণ্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যেখানে মুসলিম যুবকেরা হিন্দু ও খ্রিস্টান মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে ‘লাভ জিহাদ’-এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে, তারপর তাদের সিরিয়া পাঠিয়ে আইসিসে যুক্ত করে। এই ধারণা ‘রাষ্ট্রবিরোধী’, ‘গণতন্ত্রবিরোধী’ ও ‘সহানুভূতির অপমৃত্যু’। বাস্তবে এই সিনেমায় বলা ‘৩২,০০০ নারী নিখোঁজ’ হওয়ার অভিযোগটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং স্বীকৃত সরকারি তথ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অথচ এই মিথ্যাকে একটি ‘ভয়ের বাস্তবতা’ রূপে চিত্রিত করা হয়, যা কল্পনার চেয়ে ভয়াবহতর।
এই ‘ভয়ের রাজনীতি’ একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অংশ। যে কৌশলের মূল ভিত্তি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করা, যাতে তারা ‘অন্য’ সম্প্রদায়কে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি ভাবে। এই হুমকির চিত্রায়ন কখনও হয় ‘জেহাদি’, কখনও ‘আতঙ্কবাদী’, কখনও ‘অসভ্য সংস্কৃতি বহনকারী’। ‘দি কেরালা স্টোরি’ সেই ধারার একটি সুনির্মিত সংস্করণ, যা সিনেমার আড়ালে আদর্শগত যুদ্ধ ঘোষণা করে।
এই যুদ্ধ কেবল আদর্শগত নয়, রাষ্ট্রীয় স্তরেও তার স্বীকৃতি তৈরি হয়। যখন এই চলচ্চিত্রকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়, তখন তা কেবল শৈল্পিক মূল্যায়নের বিষয় থাকে না, বরং রাষ্ট্রের পক্ষপাত ও সাংস্কৃতিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের পুরস্কার নির্বাচন কমিটি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব—যারা এই সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—তাদের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ এক প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের রূপ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ধর্ম ও সম্প্রদায়কে সাংস্কৃতিকভাবে কলুষিত করার অনুমোদন দেয়।
ভারতীয় গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো—যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক সাম্য—এই ধরনের সিনেমা ও তার রাষ্ট্রীয় সমর্থনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেসব দর্শক এই চলচ্চিত্র দেখে মনে করেন ‘মুসলিম সম্প্রদায় একটি ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী’, তাদের মনোজগতে বিভেদ জন্ম নেয়। এটি দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক সহাবস্থানের জন্য বিপজ্জনক। জাতি, ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি এখানে চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে সাংস্কৃতিক বৈধতা পায়। অর্থাৎ ‘দি কেরালা স্টোরি’ শুধু একটি সিনেমা নয়—এ এক সাংস্কৃতিক অস্ত্র, যার উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদের একচোখা ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করা।
এই সিনেমাটি নারী শরীর ও স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেছে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামোর প্রচারের জন্য। হিন্দু ও খ্রিস্টান নারীদের ‘অবুঝ’, ‘মগজধোলাই করা সহজ’ এবং ‘রক্ষার দাবি রাখে’—এই ধরনের ধারণা নারীবাদ ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। অন্যদিকে মুসলিম পুরুষদের ‘ধূর্ত’, ‘ধর্মান্ধ’, এবং ‘সন্ত্রাসবাদের বাহক’ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা এক ঐতিহাসিক হিংসার ধারাবাহিকতা। নারীর শরীর এখানে রাষ্ট্রের হেফাজতের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিক যুগের ‘উদ্ধার’ ন্যারেটিভের সঙ্গেই মিলে যায়। ব্রিটিশরা যেমন সতীদাহ নিষিদ্ধ করার নামে ভারতীয় সমাজে সংস্কার চালিয়েছিল, বর্তমান কৌশলটিও নারীর দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
এই সিনেমা যখন এক শ্রেণির মধ্যে জনপ্রিয় হয়, তখন তা তাদের বিদ্যমান বিশ্বাসকে ‘নতুন বাস্তবতা’ হিসেবে বৈধতা দেয়। কেউ কেউ বলেন, “সত্যিটা তো দেখালো”। কিন্তু প্রশ্ন হলো—সত্য কী? ব্যক্তিগত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা (যদি সত্যি ঘটে থাকে) কি একটি গোটা সম্প্রদায়ের জন্য চরিত্র-ঘোষণায় পর্যবসিত হতে পারে? যদি তাই হয়, তাহলে যে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেকার অপরাধীদের ব্যবহার করে তাদের সামগ্রিকভাবে অপরাধী বানানো বৈধ হয়ে যায়। এটি এক মারাত্মক প্রবণতা, যা গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে সংকটে ফেলে।
রাষ্ট্রের যখন দায়বদ্ধ থাকা উচিত সংবিধানের প্রতি, তখন সেই রাষ্ট্র নিজেই যখন চলচ্চিত্রের আড়ালে একধরনের আদর্শগত আগ্রাসন চালায়, তখন তা আর কেবল রাজনৈতিক ঘটনা নয়; তা সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর টানাপোড়েন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে আমরা ‘গরিবি হঠাও’, ‘রাম জন্মভূমি’, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ডিজিটাল ভারত’ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ন্যারেটিভ দেখেছি, যেগুলোর প্রত্যেকটিতে কিছু নির্দিষ্ট সিনেমা প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে ধরনের চলচ্চিত্রকে রাষ্ট্রীয় সমর্থন দেওয়া হচ্ছে—যেমন ‘কাশ্মীর ফাইলস’, ‘গোদরা ফাইলস’, এবং ‘দি কেরালা স্টোরি’—তা এক ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে। এখানে রাষ্ট্র নিজেই একটি ভয়ের চিত্র নির্মাণ করে এবং সেই ভয়কে নির্মাণ করে সিনেমার মাধ্যমে, যা জনগণের মনে অবচেতনে প্রভাব ফেলে।
এই সিনেমাগুলোর মূল উদ্দেশ্য তথ্য সরবরাহ নয়, বরং আবেগ সৃষ্টি। এই আবেগ যুক্তিহীন, তীব্র, দ্রুত সংক্রমণশীল, এবং রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারযোগ্য। এরকম আবেগজনিত রাজনীতিকে বলে ‘অ্যাফেক্টিভ ন্যাশনালিজম’। এই জাতীয়তাবাদ যুক্তি, ইতিহাস বা মানবিকতা চায় না—তা চায় শত্রু, ভয়, বিভক্তি ও আবেগ।
আজকের রাষ্ট্রব্যবস্থা এই ধরনের আবেগকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক লাভ তোলে, নির্বাচনের সময় প্রোপাগান্ডা তৈরি করে, এবং বিরোধী মত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করে। ‘দি কেরালা স্টোরি’ এই আবেগতাড়িত রাজনীতির একটি প্রতিনিধিত্বকারী সিনেমা।
এই ধরনের চলচ্চিত্র ভারতীয় সমাজে একটি বিপজ্জনক মানসিকতা তৈরি করছে—যেখানে কেউ প্রশ্ন করলে তাকে দেশদ্রোহী, শহিদদের অসম্মানকারী বা ‘ইউরোপীয় চিন্তার দাস’ বলে দোষারোপ করা হয়। অথচ প্রশ্ন করাই গণতন্ত্রের প্রাণ। রাষ্ট্র যদি সেই প্রশ্ন করাকে দমন করে, বরং ঘৃণাকেই পুরস্কৃত করে, তাহলে সেই রাষ্ট্রের গঠনমূলক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।
‘দি কেরালা স্টোরি’ সেই ভবিষ্যতের দিকেই আমাদের সতর্ক করছে—যেখানে সিনেমা, মিডিয়া ও রাষ্ট্র একত্র হয়ে তৈরি করছে একটি বিশুদ্ধতাবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং তথ্যহীন রাজনৈতিক বাস্তবতা। সেই বাস্তবতা যত দ্রুত চিনে ফেলা যায়, ততই আমাদের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল। নিঃসন্দেহে এই সিনেমা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে, তবে তা গৌরবের নয়—বরং এক অন্ধকার সময়ের নিঃশব্দ অথচ তীব্র স্মারক হিসেবে।
১. চলচ্চিত্রটির সারাংশ ও প্রেক্ষাপট
ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যখন চলচ্চিত্র এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন সিনেমার বিষয়বস্তু, তা নির্মাণের পেছনের প্রেক্ষাপট এবং রাষ্ট্রীয় সমর্থনের ধরণ—সবই গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি চলচ্চিত্র দি কেরালা স্টোরি, পরিচালনায় সুধীপ্ত সেন এবং প্রযোজনায় বিক্রম মালহোত্রা, এই ধরনের একটি বহুচর্চিত এবং বিতর্কিত চলচ্চিত্র।
এই সিনেমার কেন্দ্রীয় আখ্যান নির্মিত হয়েছে এমন এক বয়ানের ওপর, যা কেরালার তিনজন অমুসলিম তরুণীর ‘লাভ জিহাদ’, ধর্মান্তর এবং ইসলামিক স্টেটের (আইএসআইএস) সদস্য হয়ে যাওয়ার গল্প তুলে ধরে। প্রচারণার সময় এ-ও দাবি করা হয়, কেরালার ৩২,০০০ তরুণী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সন্ত্রাসী সংগঠনে নিযুক্ত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান শোনা মাত্র যে কোনও বিবেকবান মানুষের প্রশ্ন জাগার কথা—এত বিশাল সংখ্যার ঘটনা ঘটলেও কীভাবে তা এতদিন রাষ্ট্রীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে অজানা থেকে গেল? বাস্তবতা অনুসন্ধান করলেই দেখা যায়, ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা কেরালা পুলিশ—কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষই এমন কোনো তথ্য কখনও প্রকাশ করেনি। বরং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে কেরালায় আইএসআইএস সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে মোট ১৭ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়, যাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন ধর্মান্তরিত।
এই অসত্য পরিসংখ্যানকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং তার প্রচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও গেরুয়া রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকা এই সিনেমাটিকে নিছক একটি ‘শৈল্পিক কল্পনা’ না বলে একটি ‘রাজনৈতিক প্রকল্প’ হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য করে। এখানে একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য কাজ করে—একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলিম সমাজকে ভয়ানক, বিপজ্জনক এবং সমাজবিরোধী হিসেবে তুলে ধরা। এই কাজটি চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভ, চিত্রনাট্য ও দৃশ্যায়নের মাধ্যমে এমনভাবে করা হয়, যেন ইসলাম একটি সহিংস ও ষড়যন্ত্রপ্রবণ ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং মুসলিম সম্প্রদায় হয়ে ওঠে ভারতের নিরাপত্তা, সংস্কৃতি ও নারীর স্বাধীনতার প্রধান হুমকি।
এই চলচ্চিত্রটি মুক্তির আগেই তার ট্রেলারে যে দাবি করা হয়েছিল, তা ছিল কেরালার ৩২,০০০ তরুণীর ইসলামিক স্টেটের সদস্য হওয়ার গল্প। এই ভয়ংকর পরিসংখ্যান বহু মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে এবং মুসলিম সমাজ সম্পর্কে এক গভীর সন্দেহ ও ঘৃণার বীজ বপন করে। বাস্তবিক অর্থে এই ধরনের ভুয়া তথ্য এক ধরনের সাংস্কৃতিক হিংসার জন্ম দেয়, যা সরাসরি সামাজিক সহিষ্ণুতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ককে ভেঙে দেয়। প্রশ্ন হল, এই মিথ্যার উৎপত্তি কোথায় এবং কেন রাষ্ট্র তা প্রচার ও পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে বৈধতা দেয়?
এর পেছনে আছে রাজনৈতিক ও আদর্শগত গতি। বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রে যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা বিরাজ করছে, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পরিচয়ের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। সেই নিরাপত্তাহীনতা নিরসনের জন্য প্রয়োজন এক ‘অপর’—এক শত্রু। এই শত্রু হয়ে ওঠে মুসলিম, যারা ‘ভিনধর্মী’, ‘সন্ত্রাসবাদী’, ‘সংস্কৃতিবিরোধী’, এবং ‘নারী-বিদ্বেষী’। দি কেরালা স্টোরি এই ভাবনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, যেখানে মুসলিম পুরুষদের চিত্রায়িত করা হয় ‘লাভ জিহাদি’ ও ‘জেহাদি’ হিসেবে এবং মুসলিম নারীরাও হয়ে ওঠে ‘মগজধোলাইয়ের শিকার’। হিন্দু ও খ্রিস্টান তরুণীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে, ধর্মান্তরিত করে, ইসলাম গ্রহণ করিয়ে তাদের সিরিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়—এই কাহিনি এক ধরনের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক কল্পনাপ্রসূত ভয়, যার বাস্তব ভিত্তি নেই।
এই সিনেমার ভয়াবহতা শুধু তথ্যবিকৃতি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিততায় সীমাবদ্ধ নয়—এটি নারী শরীর ও নারীর স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার এক পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ন্যারেটিভকেও তুলে ধরে। যখন বলা হয়, মুসলিম পুরুষরা হিন্দু নারীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করছে, তখন সেখানে নারীকে একটি বুদ্ধিহীন, দুর্বল, আবেগপ্রবণ ও রক্ষার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উপর নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই ধারণা নারীর স্বাবলম্বন ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে এবং পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে ‘রক্ষা’ নামে বৈধতা দেয়।
এই কৌশল নতুন নয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা যেমন ভারতীয় নারীকে ‘উদ্ধার’-এর প্রতীকে পরিণত করে নিজেদের সংস্কারনীতিকে জারি করেছিল, আজকের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিও সেই পুরনো পথেই হাঁটে—নারীর ‘সম্মান’ রক্ষার নামে মুসলিমদের ‘অপমান’ ও ‘অপরাধী’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দুই বিপরীত অবস্থানকে একত্রে সিনেমার মাধ্যমে প্রচার করাই ‘দি কেরালা স্টোরি’র অন্যতম কৌশল।
চলচ্চিত্রের এই প্রভাব নিছক দর্শকের মনে সীমাবদ্ধ থাকে না। সিনেমার মতো জনপ্রিয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে সমাজে যে বয়ান চালু হয়, তা দীর্ঘমেয়াদে জনমানসে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে। যখন একটি সিনেমা মুসলিমদের অপরাধী করে তোলে, তখন তা ব্যক্তি মুসলমানদের জীবনকেও বিপন্ন করে তোলে। তারা সামাজিক সন্দেহ, রাজনৈতিক বঞ্চনা ও রাষ্ট্রীয় দমননীতির শিকার হন। মুসলমান পরিচয় হয়ে পড়ে দোষের, লজ্জার ও বিপদের প্রতীক। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এই ভয়ানক সামাজিক বার্তাকে শুধু বৈধতা দেয় না, বরং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।
প্রশ্ন উঠতে পারে—এমন চলচ্চিত্র কি রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত হওয়া উচিত? উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ভারতের সংবিধানের মূল চেতনায়। ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যায়ের নীতি, এবং নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি দেয়। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র নিজেই কিছু বিশেষ সাংস্কৃতিক পণ্যকে পুরস্কৃত করছে, যেগুলোর প্রকৃত অর্থ রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা, এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়া।
রাষ্ট্র যখন কোনো সিনেমাকে জাতীয় পুরস্কার দেয়, তখন তা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে একটি বার্তা দেয়—এই সিনেমা ‘জাতীয় স্বার্থে’ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি সেই সিনেমা তথ্য বিকৃতি করে, মিথ্যা দাবি করে, এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীকে লক্ষ করে ঘৃণা ছড়ায়, তাহলে সেই ‘জাতীয় স্বার্থ’ আসলে কার স্বার্থ? এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করা মানে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করা।
দি কেরালা স্টোরি একটি বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির প্রতিফলন, যেখানে সত্য নয়, বরং শত্রু-সৃষ্টি মুখ্য। এই সংস্কৃতি যুক্তি, তথ্য, ও মানবিক মূল্যবোধ নয়—বরং আবেগ, আতঙ্ক ও ঘৃণাকে পুঁজি করে। এই প্রবণতা ভারতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য, তার ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিপন্থী।
চলচ্চিত্র সমাজের আয়না হতে পারে, কিন্তু সেই আয়না যদি বিকৃত হয়, তাহলে সমাজ নিজের মুখ নিজেই চিনতে পারে না। দি কেরালা স্টোরি সেই বিকৃত আয়নার একটি উদাহরণ—যেখানে প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্রের পক্ষপাত, গোষ্ঠীগত ঘৃণা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই ধরনের চলচ্চিত্র ও রাষ্ট্রীয় সমর্থন গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক বার্তা বহন করে। এজন্যই, এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কেবল একটি সিনেমা নয়—বরং সেই বৃহৎ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চক্রান্ত, যা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর করে তুলছে।
২. জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং বিতর্কের সূচনা
জাতীয় পুরস্কার জুরির মধ্যেই যখন ভিন্নমত দেখা যায়, তখন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রদীপ নায়ার, যিনি এই পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন, প্রকাশ্যে জানান যে তিনি দি কেরালা স্টোরিকে পুরস্কার দেওয়ার বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী, এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রোপাগান্ডা ছবি, যা ধর্মীয় বিভেদ উস্কে দেয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করে। অন্যদিকে জুরির বাকি অংশ দাবি করেন—এই সিনেমাটি ‘সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ’ ইস্যু তুলে ধরেছে। এখানেই মূল সংঘাতটি নিহিত: রাষ্ট্রীয় ‘গুরুত্ব’ মানে কী? সামাজিক গুরুত্ব মানেই কি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভয় এবং আতঙ্ককে বৈধতা দেওয়া?
এই ধরনের সামাজিক গুরুত্ব আসলে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশ মাত্র। দি কেরালা স্টোরি ঠিক এই ‘ভয়ের রাজনীতি’কে কেন্দ্র করেই নির্মিত। সিনেমাটি একধরনের রাজনৈতিক আবেগ তৈরি করে—যেখানে মুসলিম পরিচয় নিজেই হয়ে ওঠে সন্দেহজনক, ভীতিকর এবং দেশদ্রোহী। এই আবেগ যুক্তিভিত্তিক নয়, বরং আবেগনির্ভর। রাষ্ট্র যখন এই আবেগনির্ভর বিভাজনকে পুরস্কৃত করে, তখন তা সমাজে একটি সাংঘর্ষিক বার্তা পৌঁছে দেয়—যেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয় এবং সংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
এই সিনেমাটির পুরস্কারপ্রাপ্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ এটি কোনো বেসরকারি অ্যাওয়ার্ড নয়, বরং ভারতের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র সম্মান। এই পুরস্কার কোনও চলচ্চিত্রকে শুধু আর্থিক বা মানসিক স্বীকৃতি দেয় না, বরং তার ‘জাতীয় গুরুত্ব’ প্রতিষ্ঠা করে। রাষ্ট্র যখন একটি বিভেদমূলক, প্রোপাগান্ডামূলক সিনেমাকে ‘সেরা’ বলে ঘোষণা করে, তখন তার পরোক্ষ অর্থ দাঁড়ায়—এই সিনেমায় ব্যক্ত হয়ে থাকা ধর্মীয় পক্ষপাত এবং ঘৃণামূলক বার্তাকেই ‘জাতীয় মানসিকতা’ হিসেবে তুলে ধরা।
এই পরিস্থিতিতে শিল্পের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও প্রশ্নের মুখে পড়ে। কারণ, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সাধারণত পরিচালকের নান্দনিক দক্ষতা, বিষয়বস্তুর মৌলিকতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় নিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু দি কেরালা স্টোরি-এর ক্ষেত্রে এই মানবিক মূল্যবোধ কোথায়? একটি গোটা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ‘সন্ত্রাসের প্রতীক’ হিসেবে চিত্রিত করে, নারীর স্বাধীনতাকে এক পুরুষতান্ত্রিক হেফাজতের কাঠামোয় বন্দি করে, এবং একটি ভিত্তিহীন পরিসংখ্যানের উপর দাঁড়িয়ে জনমনে ঘৃণা ও সন্দেহ ছড়ায়—এই চলচ্চিত্রকে শিল্পের শুদ্ধতা বলে মানা যায় না।
রাষ্ট্র যদি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তবে এই ধরনের চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করার আগে তার নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পুরস্কারের মতো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিগুলিও আজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট ধরনের আদর্শিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত সিনেমাগুলিই বেশি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—কাশ্মীর ফাইলস, গোধরা ফাইলস অথবা দি কেরালা স্টোরি—সবকটি সিনেমারই একটি মিল রয়েছে: এগুলো মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনমনে শত্রুতা তৈরি করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পরিচয়ের আতঙ্ককে উসকে দেয়।
একটি প্রশ্ন এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—যে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যেও মতভেদ ছিল, তারা কিভাবে শেষপর্যন্ত এই সিনেমাকে পুরস্কার দিতে সম্মত হলেন? এর উত্তর হয়তো প্রকাশ্য পাওয়া যাবে না, তবে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের চাপ বা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব যে এই সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ একটি সাংস্কৃতিক পণ্যকে রাষ্ট্র যখন সম্মানিত করে, তখন সেটি নিছক শিল্পকর্ম থাকে না—তা হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক বার্তা।
এই বার্তা ভারতের সংবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলে। কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান একটি ভুয়া পরিসংখ্যান ও বিভেদমূলক কাহিনির উপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমাকে পুরস্কৃত করে, তখন তা শুধু সংবিধানের মূল চেতনার বিরুদ্ধে যায় না—বরং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে।
দি কেরালা স্টোরি এবং তার পুরস্কারপ্রাপ্তি একটি বহুবর্ণ, বহুভাষিক, বহুধর্মীয় সমাজে রাষ্ট্র কী ধরনের সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে—সেই প্রশ্নের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। এই প্রশ্ন শুধু সিনেমা নিয়ে নয়, বরং ভারতীয় গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং সমাজচেতনার মৌলিক ভিত্তি নিয়ে। রাষ্ট্র যখন সিনেমার মাধ্যমে বিভাজন, আতঙ্ক এবং ঘৃণাকে উৎসাহ দেয়, তখন তা শুধু সাংস্কৃতিক দুর্বিপাক নয়—বরং এক সাংবিধানিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস।
এই চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র হয়ত একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মনরঞ্জন করেছে, কিন্তু তাতে দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা ও ধর্মীয় সহনশীলতার যে পরম্পরা, তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই প্রবণতা যদি চলতেই থাকে, তাহলে ভারতের চলচ্চিত্র আর শিল্পের মাধ্যম হিসেবে নয়—বরং রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হবে। যা শেষপর্যন্ত আমাদের সমাজকে আরও বিভাজিত, অসহিষ্ণু এবং আত্মপরিচয়-সংকটের দিকে ঠেলে দেবে।
৩. ইসলামোফোবিয়া ও ‘লাভ জিহাদ’ প্রচার: একটি কৃত্রিম শত্রু নির্মাণ
ভারতীয় রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ‘লাভ জিহাদ’ নামক একটি বিভেদমূলক ধারণাকে ঘিরে এক সুকৌশলী সামাজিক ও রাজনৈতিক আখ্যান নির্মিত হচ্ছে, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে চলচ্চিত্র, মিডিয়া ও জনমনে। এই কথিত তত্ত্ব অনুসারে মুসলিম পুরুষেরা হিন্দু নারীদের প্রেমের ছলে ধর্মান্তরিত করে এবং পরে তাদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে। বাস্তবে এই ধারণার কোনও সরকারি ভিত্তি নেই, নেই নিরপেক্ষ আদালতের স্বীকৃতি, বরং ভারতীয় বিচারব্যবস্থা একাধিকবার এই ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। তবু, এই তত্ত্বকে চলচ্চিত্রের মতো জনপ্রিয় মাধ্যমে এনে একটি প্রজন্মের মনোজগতে স্থায়ী করে তোলার চেষ্টাই আজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে চলেছে।
এই প্রেক্ষাপটে দি কেরালা স্টোরি নামক চলচ্চিত্রটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় ন্যারেটিভই ছিল তথাকথিত ‘লাভ জিহাদ’। সিনেমাটিতে দাবি করা হয়, কেরালার অমুসলিম তরুণীরা মুসলিম পুরুষদের প্রেমে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তারপর তাদের পাঠানো হয় সিরিয়ায় আইএসআইএস-এর জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য।
সিনেমাটির প্রচারে বারবার বলা হয়েছে যে ৩২,০০০ তরুণী কেরালায় এই ধরনের ‘ধর্মান্তর ও সন্ত্রাসে’ যুক্ত হয়েছে। অথচ বাস্তবতার নিরিখে এই সংখ্যা সম্পূর্ণ ভুয়া ও ভিত্তিহীন। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA), কেরালা পুলিশ—কোনও সরকারি সংস্থা কখনও এমন কোনও পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। উপরন্তু, সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্টে ‘লাভ জিহাদ’ বিষয়ক মামলাগুলিতে পরপর রায়ে বলা হয়েছে, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর ও আন্তঃধর্ম বিবাহ আইনসম্মত এবং রাষ্ট্র এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এমনকি কেরালা হাইকোর্ট একাধিক রায়ে এই ‘লাভ জিহাদ’ ধারণাকে ‘রূঢ় প্রোপাগান্ডা’ বলে আখ্যা দিয়েছে।
তা সত্ত্বেও ‘দি কেরালা স্টোরি’-এর মতো একটি চলচ্চিত্রকে যখন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়, তখন তা নিছক শৈল্পিক বা কাহিনিনির্ভর স্বীকৃতি থাকে না—বরং তা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক বার্তা হয়ে ওঠে। এটি একটি সাংস্কৃতিক কৌশল, যার উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের প্রতি জনমানসে ভয়, ঘৃণা ও অবিশ্বাস তৈরি করা। রাষ্ট্র যখন এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, তখন তা তার নিরপেক্ষতা হারায় এবং একচোখা জাতীয়তাবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে।
এই সিনেমায় কেরালাকে যে আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বাস্তবতার কেরালার ঠিক উল্টো। কেরালা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত রাজ্য, যেখানে সাক্ষরতার হার ৯৬ শতাংশের কাছাকাছি। এই রাজ্যে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে। কেরালার রাজনৈতিক সংস্কৃতিও যুক্তিনির্ভর ও প্রগতিশীল, যেখানে ধর্ম নয়—মানবিকতা ও শ্রেণিচেতনা বেশি গুরুত্ব পায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেরালাকে জঙ্গি নির্মাণের আঁতুড়ঘর হিসেবে দেখানো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও আপমানজনক।
তবে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিকটি হলো—রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসরে এই ধরনের প্রোপাগান্ডা ক্রমশ ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে এই সিনেমার প্রশংসা করছেন, নির্বাচনী প্রচারে এর ব্যবহার ঘটছে, এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে এই প্রবণতা ভয়ংকর। কারণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ হলো যুক্তিভিত্তিক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং বিভেদ নয়, সমন্বয়ের মাধ্য দিয়ে জাতির ঐক্য রক্ষা করা। কিন্তু যদি রাষ্ট্র নিজেই ‘লাভ জিহাদ’-এর মতো একটি ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তোলে, তাহলে তা আর গণতন্ত্র নয়—বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভয়ের উপর দাঁড়ানো এক ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রব্যবস্থা।
মিডিয়া এবং চলচ্চিত্র—এই দুই শক্তিশালী মাধ্যম যখন একসঙ্গে কাজ করে, তখন জনমানসে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। দি কেরালা স্টোরি এই দুই মাধ্যমের মিলিত ব্যবহারেই এক ধরনের ‘সাংস্কৃতিক আতঙ্ক’ তৈরি করেছে। এই আতঙ্ক যুক্তির নয়, তথ্যের নয়—বরং আবেগ, রটনা ও ধর্মীয় ভয়ের উপর নির্ভরশীল। এই আবেগই সহজে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে রাজনৈতিক নির্বাচনী প্রচারে, যেখানে বাস্তব সমস্যাগুলি যেমন—বেকারত্ব, নারী নিপীড়ন, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুর্বলতা—এইগুলো ঢেকে দেওয়া যায় একটি ‘অন্যের ষড়যন্ত্র’ নামক ধোঁয়াশায়।
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি কখনও স্থায়ী সমাধান দেয়নি—বরং তা প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সংঘাতকেই বাড়িয়েছে। যেসব সমাজে ধর্মীয় বিভেদ গভীর হয়, সেখানে নাগরিক পরিচয়ের চেয়ে ধর্মীয় পরিচয় বড় হয়ে ওঠে। দি কেরালা স্টোরি-এর মতো সিনেমা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা রাষ্ট্রকে একটি সমন্বয়বাদী কাঠামো থেকে সরিয়ে সাম্প্রদায়িক একাধিপত্যের দিকে ঠেলে দেয়।
এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজের, বুদ্ধিজীবীদের, চলচ্চিত্র সমালোচকদের এবং মানবিকতাবাদীদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। তারা যেন নীরব না থাকেন, যেন ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে এই প্রোপাগান্ডার মুখোশ উন্মোচন করেন। ইতিমধ্যেই বহু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এই সিনেমাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মোড়কে সাম্প্রদায়িক প্রচারণার বৈধতা বলেই আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এটি একটি সাংস্কৃতিক হুমকি, যা ভারতের সংবিধানিক মূল্যবোধ—ধর্মনিরপেক্ষতা, সহিষ্ণুতা, ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী।
৪. ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ
এই সিনেমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র ও অর্থবহ প্রতিবাদ আসে ভারতের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (FTII)-এর ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে। তাঁরা এক লিখিত বিবৃতিতে সোজাসুজি বলেন—এই ছবি কোনো চলচ্চিত্র নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক অস্ত্র, যা রাষ্ট্রীয় মদতে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ‘শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই বক্তব্য নিছক রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং একটি গভীর সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। যখন সিনেমা 'শত্রু'-নির্মাণের হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন তা আর শিল্প থাকে না—তা হয়ে ওঠে যুদ্ধের ভাষা, ঘৃণার চর্চা, এবং ঐক্যের ভিত্তি ধ্বংসের উপকরণ।
এই সময়ের বাস্তবতা হচ্ছে—‘ইসলামোফোবিয়া’ আজ আর ব্যক্তিগত গোঁড়ামি নয়; বরং তা এখন রাষ্ট্রীয় বৈধতা পাচ্ছে, পুরস্কৃত হচ্ছে, এবং জনচেতনার অংশ হয়ে উঠছে। দি কেরালা স্টোরি-এর জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সেই ভয়ংকর বার্তাই জনসাধারণের সামনে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—যে এখন একটি ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো ‘শিল্প’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। এই মানসিকতা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি উৎসাহিত হয়, তাহলে তা কেবল চলচ্চিত্র নয়, সমগ্র গণতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর জন্য হুমকি।
যারা সিনেমাটির সমর্থনে দাঁড়ান, তাঁরা বলেন এটি ‘সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক ইস্যু’। এই যুক্তি খুবই বিপজ্জনক, কারণ এর মানে দাঁড়ায়—সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা আজ সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে জনভীতির প্রসারে নির্ভর করছে। অর্থাৎ ‘ভয়’ একটি সামাজিক মূল্য হয়ে উঠেছে, এবং সেই ভয় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের হয়, তবে তা বৈধ, স্বীকৃত এবং পুরস্কারযোগ্য। এই ভাবনাচক্র একরকম বর্ণবাদী ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সাংস্কৃতিক পুনরুৎপাদন।
এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অনেক পরিচালক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্রকর্মীর প্রতিবাদ স্বাভাবিক এবং জরুরি। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, লিখেছেন—যখন গবেষণানির্ভর, মানবিক এবং সত্যভিত্তিক সিনেমাগুলি উপেক্ষিত হয়, তখন একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রোপাগান্ডা ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়, তার মানে হলো রাষ্ট্র নিজেই ঘৃণার রাজনীতিকে সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি দিচ্ছে। এটা শুধু নৈতিক ব্যর্থতা নয়, বরং এক গভীর সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনা।
এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কেবল একজন শিল্পী বা একটি ছবির স্বীকৃতি নয়—তা এক জাতির সাংস্কৃতিক অবস্থানের প্রতিচ্ছবি। এই পুরস্কার একটি বার্তা বহন করে—জাতি কোন মূল্যবোধকে গ্রহণ করছে, কোন আদর্শকে উৎসাহ দিচ্ছে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কী শেখাতে চাইছে। যদি সেই বার্তা হয়—”ইসলামোফোবিয়া এখন পুরস্কারযোগ্য”, তাহলে তা একটি জাতির সাংস্কৃতিক আত্মহত্যা।
এই সময়ের প্রেক্ষিতে FTII-এর ছাত্রদের প্রতিবাদ এক ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা। তাঁরা কেবল চলচ্চিত্র সমালোচনা করেননি, বরং একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তাঁরাই আজ সেই যুবসমাজের প্রতিনিধি, যারা জানে কোন সিনেমা শিল্প, কোনটা অস্ত্র। তাদের প্রতিবাদ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়—যে রাষ্ট্র যখন ইসলামোফোবিক সিনেমাকে পুরস্কৃত করে, তখন তা একটি নিরীহ কর্মকাণ্ড নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক অভিসন্ধি।
এই অবস্থায় জরুরি হয়ে পড়েছে জনসাধারণ, শিক্ষিত নাগরিক ও চিন্তাশীল সমাজের এগিয়ে আসা। আমরা কি সত্যিই চাই আমাদের চলচ্চিত্র এমন এক অস্ত্র হয়ে উঠুক, যা বিভাজনের বিষ ছড়ায়? আমরা কি চাই রাষ্ট্র সেই বিষ ছড়িয়ে সমাজকে ধ্বংস করুক? এই প্রশ্ন শুধু সিনেমা নয়, আমাদের নৈতিক বোধ, সাংবিধানিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। যদি আমরা নীরব থাকি, তাহলে সেই নীরবতা হবে সম্মতির নামান্তর।
সবশেষে, দি কেরালা স্টোরি ও তার জাতীয় স্বীকৃতি আমাদের ইতিহাসে একটি অন্ধকার পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এর বিপরীতে যারা প্রতিবাদ করেছেন, তারা কেবল শিল্পের সৎ অভিভাবক নন—তাঁরা ভবিষ্যতের গণতন্ত্রের সম্ভাবনাও রক্ষা করছেন। এই মুহূর্তে আমাদের বেছে নিতে হবে—আমরা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারকে একটি সাংস্কৃতিক শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে দেখব, না কি প্রোপাগান্ডার মঞ্চ হিসেবে মেনে নেব। উত্তরটা শুধু আমাদের বিবেক নয়, আমাদের ভবিষ্যতের ভিত্তিও নির্ধারণ করবে।
৫. কেরালা রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়া ও রাজনীতিক মন্তব্য
ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু একটি সাংবিধানিক পরিভাষা নয়—এটি একটি গভীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতা, যা দেশের বহু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিকে এক সুতোয় গেঁথে রাখে। এই ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার উপর যখন সাংস্কৃতিক আঘাত আসে, তখন তা নিছক একটি সিনেমা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এক জাতির আত্মপরিচয় ও মৌলিক আদর্শের উপর আক্রমণ বলে বিবেচিত হয়। এই বাস্তবতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে দি কেরালা স্টোরি চলচ্চিত্র এবং তার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তিকে ঘিরে যে তীব্র বিতর্ক ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়।
কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারায়ি বিজয়নের প্রতিক্রিয়া এই বিতর্ককে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই চলচ্চিত্র কেরালাকে অপমান করেছে এবং গোটা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার উপর আঘাত হেনেছে। তিনি আরো বলেন, যারা ছবিটির প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যা তথ্য সম্পর্কে অবগত, তারাও যখন এর পুরস্কারপ্রাপ্তির সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করেন, তখন তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও গভীর উদ্বেগের বিষয়। তাঁর এই মন্তব্য কেবল এক রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থান নয়—বরং এক জাতির আদর্শগত সংকটের প্রতি ইঙ্গিত।
এই প্রসঙ্গে কেরালার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও স্মরণীয়। এর আগেও উল্লেখ করেছি যে কেরালা এমন একটি রাজ্য, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখানে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পারস্পরিক সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে। সামাজিক সূচকগুলিতে কেরালার অবস্থান দেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ—সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য, নারীর নিরাপত্তা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে এই রাজ্যের অগ্রগতি ব্যতিক্রমী। অথচ সেই কেরালাকেই দি কেরালা স্টোরি-তে তুলে ধরা হয় একধরনের মৌলবাদী আতঙ্কের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে।
কেরালার বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস—রাজনীতির দুই বিপরীত মেরুর এই দুই দলই যখন একই সুরে এই চলচ্চিত্রের সমালোচনা করেন, তখন তা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ নয়, বরং একটি আদর্শগত অবস্থান। উভয় পক্ষই এই সিনেমাকে রাষ্ট্রীয় মদতে পরিচালিত এক পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা বলে চিহ্নিত করেন, যার মূল উদ্দেশ্য হলো এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সমাজের কাছে শত্রুরূপে উপস্থাপন করা এবং জনগণের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভেদ সৃষ্টি করা। তাঁদের বক্তব্যে একটি স্পষ্ট বার্তা ফুটে ওঠে—এই ধরনের প্রচার কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাতিয়ার নয়, এটি ভারতের সংবিধানের মূল চেতনার সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।
একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কি এতটাই উন্মুক্ত যে তার আড়ালে মিথ্যা প্রচার, প্রোপাগান্ডা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং ঘৃণার বীজ বপন বৈধ হয়ে যায়? উত্তর স্পষ্ট—না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যখন অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করে, ঘৃণাকে উৎসাহ দেয় এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন তা আর গণতন্ত্রের গৌরব নয়, বরং এক গণতান্ত্রিক পরাজয়।
কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য এই সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর কথায় ফুটে ওঠে একটি আশঙ্কা—এই ধরনের প্রোপাগান্ডা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত হতে থাকে, তবে তা ভবিষ্যতের জন্য একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই অবস্থায় সত্যভিত্তিক, মানবিক ও গবেষণানির্ভর চলচ্চিত্রগুলি প্রান্তে চলে যায়, উপেক্ষিত হয়। যার ফলে সাংস্কৃতিক জগতে একটি সংকোচন শুরু হয়—যেখানে মতের বৈচিত্র্য, আদর্শগত বহুস্তরতা এবং মানবিক সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়।
এমন এক সময়ে যখন দেশে রাজনৈতিক মেরুকরণ চরমে, তখন শিল্প ও সংস্কৃতি হওয়ার কথা ছিল সংহতির মাধ্যম, চিন্তার মুক্তি এবং প্রগতিশীলতার বাহক। কিন্তু রাষ্ট্র যখন সেই শিল্পকে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, তখন তা সাংস্কৃতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। দি কেরালা স্টোরি-এর ঘটনাপ্রবাহ এই পরিবর্তনেরই প্রতীক—যেখানে সিনেমা আর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং তা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরি এক প্রোপাগান্ডামূলক পণ্য।
এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে প্রয়োজন বৃহত্তর সচেতনতা, জনমত তৈরি এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ। কারণ ভারত কেবল একটি রাষ্ট্র নয়—এটি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান এবং বহুত্ববাদের চর্চা রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস জুড়ে। এই ইতিহাস রক্ষার দায় আমাদের সবার।
৬. মাধ্যম ও বিতরণ: কর-মুক্তি ও রাষ্ট্রীয় প্রচারণা
দি কেরালা স্টোরি-র মিথ্যাচারকে রাষ্ট্রীয় সমর্থনের মাধ্যমে জোরদার করা হয়েছিল আরও কয়েক ধাপে। প্রথমত, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো—মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড এবং মহারাষ্ট্রে এই সিনেমাকে কর-মুক্ত ঘোষণা করা হয়। সাধারণত কর-মুক্ত করা হয় এমন চলচ্চিত্রকে, যেগুলি জনসচেতনতামূলক, শিক্ষামূলক কিংবা মানবিক বিষয়ে অবদান রাখে। কিন্তু দি কেরালা স্টোরি-এর ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত একেবারে ব্যতিক্রমী এবং প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ এটি কোনো গবেষণাধর্মী, তথ্যনিষ্ঠ বা মানবিক ভিত্তিতে নির্মিত ছবি নয়, বরং একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা, যার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে একটি কল্পিত ষড়যন্ত্রতত্ত্ব।
এই কর-মুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র মূলত সিনেমাটিকে বৈধতা ও গুরুত্ব প্রদান করে। এটি একটি সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি, যা বলে, “এই বার্তাটি রাষ্ট্র অনুমোদিত, এই চিন্তাধারাটি গ্রহণযোগ্য।” ফলে যে বার্তাটি আসছে তা হল—মুসলিম সমাজ ‘অপর’, তারা বিপজ্জনক, এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে এই ‘অপর’ থেকে রক্ষা করা। এটি শুধু একটি চলচ্চিত্রের প্রচার নয়, বরং এক ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় ন্যারেটিভ নির্মাণ।
এই প্রচার আরও বিস্তৃত হয় সামাজিক মাধ্যমে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব—সবখানেই এই ছবির প্রচার চলে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তায়। ট্রেলারের ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার গোষ্ঠীতে, যেখানে বারবার বলা হয়—‘রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে’, ‘নারীরা বিপন্ন’, ‘ধর্মান্তরের ভয়ংকর নেটওয়ার্ক সক্রিয়’, এবং ‘সত্য লুকানো হচ্ছে’। এই ধরণের বক্তব্য, যেগুলি কোনোভাবেই নিরপেক্ষ তথ্য বা আদালতের পর্যবেক্ষণে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়নি, তা-ই ব্যবহার করা হয় জনমনে আতঙ্ক ও ঘৃণা তৈরির জন্য।
এই ভয় ও ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে ভিত্তি করে যে প্রচার চলে, তা বাস্তবতা নয়—বরং একটি ‘ভুয়া শত্রু’ নির্মাণ। রাষ্ট্র যখন নিজের শত্রু নিজেই বানিয়ে নেয়, তখন তার উদ্দেশ্য একটাই—ভয় দেখিয়ে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং রাজনৈতিক সুবিধা তোলা। দি কেরালা স্টোরি-এর ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজকে ‘অভ্যন্তরীণ শত্রু’ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। আর নারী-শরীরকে ব্যবহার করা হয়েছে ‘সংস্কৃতি রক্ষার’ একটি আবেগময় ট্রিগার হিসেবে।
এই প্রচারের ধরণটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেসব চলচ্চিত্র বা মিডিয়া কনটেন্ট মুসলিম বিরোধী চিন্তা ছড়ায়, তাদেরই রাষ্ট্রীয় প্রশংসা, উৎসাহ, কর-মুক্ত সুবিধা এবং পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, মানবিকতা ও তথ্যনিষ্ঠতা-ভিত্তিক চলচ্চিত্র যেমন পিঙ্ক, আর্টিকেল ১৫ বা প্যারচুন—যেগুলি বাস্তব সমস্যাগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদের হয় উপেক্ষা করা হয়, নয়তো সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।
রাষ্ট্রের এই সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ চলচ্চিত্র শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। আজ একপ্রকার নীরব সেন্সরশিপ চালু হয়েছে—যেখানে কেউ সরাসরি নিষেধ করছে না, কিন্তু কোন চিন্তা গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়—তা রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দিচ্ছে প্রমোশন, কর-মুক্ত ঘোষণা ও পুরস্কারের মাধ্যমে। এর ফলে চলচ্চিত্র নির্মাতারা নিরপেক্ষ, মানবিক কিংবা বাস্তবসম্মত বিষয়ে কাজ করতে সাহস হারাচ্ছেন, কারণ তাঁরা জানেন, তাতে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব নয়।
এই প্রেক্ষাপটে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। সত্য যাচাই করার সংস্কৃতি, সমালোচনামূলক চিন্তাধারা, এবং প্রশ্ন তোলার সাহস না থাকলে সমাজ ধীরে ধীরে একটি ‘মতান্ধ রাষ্ট্র’-এ পরিণত হয়। দি কেরালা স্টোরি-এর কর-মুক্ত ঘোষণা, ব্যাপক প্রচার ও রাষ্ট্রীয় উৎসাহ দেখে যে আতঙ্ক তৈরি হয়, তা এই আশঙ্কাকে প্রবল করে তোলে—যে এই রাষ্ট্র নিজেই আজ ঘৃণার চর্চাকে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের প্রতীক বানাতে চাইছে।
সবশেষে বলা যায়, দি কেরালা স্টোরি শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়—এটি এক দীর্ঘমেয়াদি প্রোপাগান্ডা প্রকল্পের অংশ, যার উদ্দেশ্য সামাজিক বাস্তবতা বিকৃত করা, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত দুর্বল করা, এবং একটি ‘ভয়ের সংস্কৃতি’ তৈরি করে সেই ভয়ের উপর রাজনীতি দাঁড় করানো। এর প্রমোশনাল কৌশল, কর-মুক্ত সুবিধা, এবং রাষ্ট্রীয় প্রশংসা—সবকিছু মিলে এই প্রকল্পকে গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে সচেতন নাগরিকদের কণ্ঠই একমাত্র প্রতিরোধের আশ্রয়স্থল। সমাজ যদি প্রশ্ন করতে শেখে, প্রমাণ চাইতে শেখে, মিথ্যার বদলে যুক্তির পথে হাঁটে—তবেই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। নইলে সিনেমার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রোপাগান্ডা বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে।
৭. জাতীয় পুরস্কার: সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি না রাজনৈতিক স্বার্থ?
ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এক সময় ছিল সত্য, ন্যায়ের প্রতীক এবং শিল্পের শুদ্ধতম রূপের স্বীকৃতি। এই পুরস্কার কেবলমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাণের কারিগরি উৎকর্ষতা নয়, বরং তার নৈতিক দায়বদ্ধতা, মানবিক গভীরতা এবং সমাজচিন্তার উপরেই মূলত নির্ভর করত। এই পুরস্কারের ইতিহাসে আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, শ্যাম বেনেগাল, অপর্ণা সেন, গিরিশ কাসারাভালির মতো চলচ্চিত্রকারেরা সমাজের বাস্তবতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মানবিক চেতনার জটিলতাকে তুলে ধরার জন্য এই সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু আজ যখন এই পুরস্কার এমন একটি চলচ্চিত্রকে দেওয়া হয়, যার বুনট গড়া হয়েছে ভিত্তিহীন তথ্য, ঘৃণার আখ্যান ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের উপর, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে—এই পুরস্কার কি এখনও তার সেই গৌরব ধরে রেখেছে, নাকি তা আজ রাজনৈতিক অনুগত্যের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে?
দি কেরালা স্টোরি চলচ্চিত্রটির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি এই প্রশ্নকে আরও জোরালো করে তোলে। একটি চলচ্চিত্র, যা কল্পিত ও যাচাই-বিহীন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একটি রাজ্য ও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দোষারোপ করে, তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘সেরা’ বলে ঘোষণা করা একটি রাজনৈতিক বার্তা। এবং সেই বার্তা হল—সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ এবং পুরস্কারযোগ্য। এই বার্তা কেবলমাত্র চলচ্চিত্র জগতেই নয়, বরং বৃহত্তর সমাজেও এক ধরনের স্বীকৃত ঘৃণার সংস্কৃতি তৈরি করে।
স্মরণে রাখতে হবে, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কেবলমাত্র একটি সরকারি পদক নয়। এটি একটি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতীক, যা দেশকে বলে দেয়—কোন শিল্প রাষ্ট্রের চোখে মূল্যবান, কোন শিল্প রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উৎসাহিত হওয়ার যোগ্য। তাই যখন সত্য, ন্যায্যতা, মানবিকতা ও গবেষণাভিত্তিক শিল্প উপেক্ষিত হয়, এবং তার পরিবর্তে প্রোপাগান্ডা, বিকৃত সত্য ও ঘৃণাপূর্ণ আখ্যান পুরস্কৃত হয়, তখন সেই রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের ভারসাম্য ভেঙে পড়ে।
১৯৭০ ও ৮০–এর দশকে যখন সত্যজিৎ রায়ের ‘জন অরণ্য’, ঋত্বিক ঘটকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ বা মৃণাল সেনের ‘ভুবন সোম’ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেত, তখন তা ছিল এক প্রতিবাদী শিল্পের স্বীকৃতি। সেইসব চলচ্চিত্র ছিল নিঃশব্দে উচ্চারিত এক সামাজিক প্রতিবাদ—শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে, অসমতার বিরুদ্ধে। আজ যখন দি কেরালা স্টোরি-র মতো এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভাজনমূলক চলচ্চিত্র জাতীয় স্বীকৃতি পায়, তখন স্পষ্ট হয়ে যায়—রাষ্ট্র আর সেই একই শিল্পবোধে বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্র আজ এমন এক সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিচ্ছে, যা সত্য নয়, বরং আতঙ্ক তৈরি করে, শত্রু বানায়, এবং মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়ায়।
এই বাস্তবতায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আর সেই গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সমাবেশের প্রতীক থাকে না। বরং তা হয়ে ওঠে ক্ষমতাসীন মতাদর্শের হাতিয়ার, যেখানে পুরস্কারের বিচার কেবল শৈল্পিক গুণ নয়, বরং রাজনৈতিক ‘সহমত’-এর উপর নির্ভরশীল। আজকের রাষ্ট্র যখন দি কেরালা স্টোরি-কে ‘সেরা পরিচালক’ ও ‘সেরা চিত্রগ্রাহক’-এর মতো বিভাগে পুরস্কৃত করে, তখন সে আসলে ঘোষণা করে দেয়—ঘৃণা ও বিভাজন এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে মূল্যবান শিল্প।
প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ভবিষ্যতে আর নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে দাঁড়াবে না? উত্তর কঠিন, কিন্তু বাস্তববাদী হলে বলতে হয়—বর্তমানে রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিখিত নিয়ন্ত্রণে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই পুরস্কার ব্যবস্থায় জুরিদের মতানৈক্যও যে গুরুত্ব পায় না, তা এই বছরের ঘটনাতেই স্পষ্ট। প্রদীপ নায়ার, যিনি জাতীয় পুরস্কারের জুরি সদস্য ছিলেন, তিনি নিজেই জানিয়েছেন—দি কেরালা স্টোরি-কে পুরস্কার দেওয়া নিয়ে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আপত্তি বিবেচনায় না এনে অন্য সদস্যদের ‘সামাজিক গুরুত্ব’-এর দোহাই তুলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।
এখানেই আসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—‘সামাজিক গুরুত্ব’ কথাটির দোহাই দিয়ে আজ রাষ্ট্র এমন শিল্পকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, যা ঘৃণার রাজনীতি, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব, এবং ধর্মীয় অবিশ্বাসকে উসকে দেয়। অথচ বাস্তবের সমাজে যে আসল সমস্যা বিদ্যমান—নারী নির্যাতন, শিক্ষার সংকট, কর্মহীনতা, পরিবেশ সংকট, কিংবা স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভাঙন—এইসব নিয়ে কথা বলা চলচ্চিত্রগুলি আজ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের তালিকা থেকেই বাদ পড়ে যাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ব্যাকরণটিই বদলে যাচ্ছে—সত্য নয়, এখন রাষ্ট্র ‘সহমতের শিল্প’ চায়।
এই পরিবর্তন কেবল একটি প্রজন্মের সংস্কৃতি ও মননকেই প্রভাবিত করছে না, বরং ইতিহাসের সামনে রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসযোগ্যতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কারণ ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদেরা যখন এই সময়ের পুরস্কার তালিকা দেখবেন, তখন তাঁরা দেখতে পাবেন—এক সময় যে পুরস্কার সত্যজিতের পথের পাঁচালী বা গিরিশ কাসারাভালির ঘাটাশ্রদ্ধা পেয়েছিল, পরে সেই একই পুরস্কার পেয়েছে এমন এক চলচ্চিত্র, যার ভিত্তি মিথ্যা পরিসংখ্যান, ভিত্তিহীন ‘লাভ জিহাদ’ তত্ত্ব এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কৌশল। এই বৈপরীত্য এক জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্জনার নির্দেশক হয়ে থাকবে।
এই প্রেক্ষাপটে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ‘কোন শিল্পকে’ স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, এবং প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করা। যারা বলেন, “শিল্পে মতাদর্শ থাকে না”—তাঁদের ভুল প্রমাণ করেছে রাষ্ট্র নিজেই। আজ রাষ্ট্র শিল্পকে ব্যবহার করছে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। অতএব, মতাদর্শহীন শিল্প নয়, বরং সচেতন, সমালোচনামূলক, মানবিক ও প্রগতিশীল শিল্পই এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।
তাই বলা যায়, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এক সময় ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক বিবেকের প্রতীক। কিন্তু আজ তা আর নিখাদ শিল্পসম্মান নয়—বরং এক ধরনের সাংস্কৃতিক শৈথিল্য ও রাজনৈতিক চাপের প্রতিফলন। রাষ্ট্র যখন তার স্বীকৃতি দেওয়ার নীতিমালার মধ্যে থেকে সত্যকে বাদ দিয়ে বিভেদকে স্থান দেয়, তখন সেই রাষ্ট্র কেবল এক পুরস্কারব্যবস্থা নয়, বরং তার সাংস্কৃতিক আত্মাকে হারিয়ে ফেলে। এই আত্মার প্রত্যাবর্তন শুধু চলচ্চিত্রকারদের উপর নয়—বরং আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের উপর নির্ভর করে, যারা সংস্কৃতির মধ্যে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতাকে পুনরুদ্ধার করতে চায়।
৮. সাংস্কৃতিক বিভাজনের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল
একটি রাষ্ট্র যখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভাজনমূলক কোনও চলচ্চিত্রকে তার সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি দেয়, তখন তা কেবল একটি পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নয়—বরং সমাজকে একটি স্পষ্ট বার্তা। সেই বার্তা হলো, রাষ্ট্র এখন সত্যের চাইতে ভয়ের আখ্যানকে, মানবিকতার চাইতে ঘৃণাকে, এবং বহুত্ববাদের চাইতে বিভেদকে উৎসাহ দিচ্ছে। দি কেরালা স্টোরি এই বার্তারই একটি সাংস্কৃতিক প্রকাশ, এবং এর পুরস্কারপ্রাপ্তি কেবল একটি সিনেমার গুণগত মান নয়, বরং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অবস্থানকেও প্রকাশ করে।
এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হলো—এর পরিণতি কী? রাষ্ট্রের সম্মানিত পুরস্কার যদি এমন একটি চলচ্চিত্রকে দেওয়া হয়, যার ভিত্তি মিথ্যা তথ্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ন্যারেটিভ, এবং যার মূল উদ্দেশ্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত করা, তাহলে সেই পুরস্কার সমাজে কী রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? উত্তরটা সরল নয়, কিন্তু তা স্পষ্টতই বিপজ্জনক।
প্রথমত, এই ধরনের স্বীকৃতি একটি প্রজন্মের মানসগঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। কিশোর-কিশোরীরা, যারা এখনো ইতিহাস, রাজনীতি বা ধর্মীয় বৈচিত্র্যের জটিলতা বুঝে ওঠেনি, তারা যদি দেখে রাষ্ট্র এমন একটি চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করছে, তাহলে তারা সেটিকেই ‘সত্য’ হিসেবে মেনে নেয়। তারা ভাবতে শেখে, মুসলমান মানেই সন্দেহজনক, হিন্দু নারী মানেই বিপন্ন, এবং প্রেমের সম্পর্ক মানেই ধর্মান্তরের ছলনা। এই চিন্তাগুলো কিশোর বয়সে রোপিত হলে তা সহজেই বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক ও নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
দ্বিতীয়ত, এই বিভাজন কেবল মনস্তাত্ত্বিক নয়—এর বাস্তব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি আছে। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই দেখা যাচ্ছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার ঘটনা, গোরক্ষার নামে গণপিটুনি, ধর্মীয় উস্কানি, নির্বাচনী প্রচারে মুসলিম বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ২০১৪ থেকে 2024 সালের মধ্যেই একাধিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ভারতে হেট ক্রাইম বা ঘৃণাভিত্তিক অপরাধের হার আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে, এবং ভুক্তভোগীদের একটা বড় অংশই মুসলিম।
এই বাস্তবতায় দি কেরালা স্টোরি-র মতো চলচ্চিত্র একটি ‘সাংস্কৃতিক ঘৃণার সংবিধান’ নির্মাণ করে। রাষ্ট্র যখন এই ঘৃণাকে পুরস্কৃত করে, তখন সে কার্যত এই অপরাধগুলোকেও মৌন সমর্থন দিয়ে দেয়। যেসব ঘৃণাপ্রচার আগে প্রান্তিক ছিল, তা এখন রাষ্ট্রীয় মূলস্রোতের অংশ হয়ে যায়। মুসলমানদের সম্পর্কে অসত্য, বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে ‘নতুন বাস্তবতা’ হয়ে ওঠে, যা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাগরিক সাম্যের ভাবনাকে ভিতর থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। “
এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি “ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র” হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার মানে কেবল আইন নয়, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণেও রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু যদি রাষ্ট্র নিজেই ঘৃণার রাজনীতিকে উৎসাহ দেয়, বিভেদমূলক আখ্যানকে সম্মান জানায়, তাহলে সে তার সংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে না। রাষ্ট্র তখন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিপরীত।
এই পরিস্থিতি শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের জন্যও বিপজ্জনক। কারণ রাষ্ট্র যখন ভুয়া শত্রু তৈরি করে সমাজকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়, তখন সেই সমাজ আর বাস্তব সমস্যা—দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দুর্দশা—এইসব নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। বরং তারা নিজেদের নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির মিথ্যা সংকটে ডুবে গিয়ে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার প্রশ্নহীন সমর্থকে পরিণত হয়। বিভাজনের রাজনীতি এইভাবেই কৌশলে জনগণের সচেতনতা হরণ করে নেয়।
সিনেমার সামাজিক শক্তি বিপুল। এটা একটি গণমাধ্যম, যা জনচেতনা গঠনের এক প্রধান হাতিয়ার। সিনেমা ইতিহাসকে তুলে ধরতে পারে, সংস্কৃতির বহুত্বকে উদযাপন করতে পারে, অথবা মানুষকে সহানুভূতির জায়গা থেকে ভাবতে শেখাতে পারে। কিন্তু যখন সিনেমাকে ভয়ের, ষড়যন্ত্রের, ধর্মীয় ঘৃণার বাহনে পরিণত করা হয়, তখন তা আর শিল্প থাকে না—তা হয়ে ওঠে সামাজিক অপসংস্কৃতির ট্রিগার।
ভারতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সহনশীলতা ও সত্যভিত্তিক চর্চা। রাষ্ট্র যদি সত্য, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তি-নির্ভর চিন্তার পৃষ্ঠপোষক না হয়ে উল্টো ঘৃণার বার্তাবাহী সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, তাহলে তা কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে অস্থির করে তোলে। গণমাধ্যম, সিনেমা ও রাষ্ট্রের এই মিলিত অপব্যবহার একটি অস্থির, সহিংস ও অপরিণত সমাজ তৈরি করে, যেখানে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় তার নাগরিক অধিকার থেকে বড় হয়ে ওঠে।
এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রের নীরবতা একরকম সম্মতি। রাষ্ট্র চাইলে সিনেমার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা দিতে পারে। মদার ইন্ডিয়া, মুল্ক, আর্টিকেল ১৫ এর মতো সিনেমাগুলিকে উৎসাহ দিতে পারে, যারা মানবিকতা ও সংবিধানিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে। কিন্তু তা না করে, রাষ্ট্র যদি এমন এক সিনেমাকে পুরস্কৃত করে, যেটি ঘৃণাকে উপহার দেয়, মিথ্যাকে প্রচার করে, এবং বিভাজনকে বৈধতা দেয়, তাহলে সে নিজের আদর্শ থেকেই সরে আসছে।
তাই বলা যায়, দি কেরালা স্টোরি-এর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি একটি গভীর সামাজিক বিপদের সূচক। এর প্রভাব সরলভাবে একটি সিনেমার মর্মে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সামাজিক মনোজগতে, কিশোর-কিশোরীর চিন্তায়, এবং নাগরিকদের সম্পর্কের ভিতরে শিকড় গাঁথতে শুরু করে। এই অবস্থায় যদি আমরা প্রশ্ন না তুলি, প্রতিবাদ না করি, তাহলে সেই নীরবতা হবে ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। একদিন এই সময়কে ফিরে দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়তো বলবে—ঘৃণার সংস্কৃতি যখন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেল, তখন সমাজের বিবেক কোথায় ছিল? সেই বিবেককে জাগিয়ে রাখাই আজকের সবচেয়ে বড় দায়।
৯. রাষ্ট্র বনাম বাস্তবতা
দি কেরালা স্টোরি বিশেষভাবে বিপজ্জনক কারণ এটি নারীবিরোধী রাজনীতিকে ধর্মীয় শত্রু-নির্মাণের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এখানে নারী কেবলই রক্ষার জন্য উপযোগী একটি ‘দুর্বল সত্তা’, যাকে মুসলিম পুরুষের ষড়যন্ত্র থেকে ‘বাঁচাতে’ হবে। প্রেম, পছন্দ বা সিদ্ধান্ত—এইসবকে উপেক্ষা করে নারীকে একটি জিনিসে পরিণত করা হয়, যার উপর পুরুষতান্ত্রিক হেফাজত প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য। প্রেম এখানে প্রেম নয়—তা হয়ে যায় ধর্মান্তরের হাতিয়ার। স্বাধীনতা এখানে স্বাধীনতা নয়—তা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় অসভ্যতার শিকার হওয়ার সুযোগ। এই জাতীয় বয়ান শুধু মুসলিম বিরোধী নয়—এটি নারীর স্বাধীনতাকেও ধ্বংস করে।
রাষ্ট্র যখন এমন একটি সিনেমাকে পুরস্কৃত করে, তখন সে দুটি বার্তা দেয়। প্রথমত, মুসলিম সমাজ ‘অপর’—তাদের বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র এখন এমন কনস্পিরেসি থিওরি গ্রহণযোগ্য করছে, যা আগে কেবল চরম দক্ষিণপন্থী প্রপাগান্ডার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই রাষ্ট্রীয় অনুমোদন একটি সাংস্কৃতিক বৈধতা দেয়—জনগণ ভাবে, “যদি সরকার এই সিনেমাকে প্রশংসা করে, তবে এর ভেতরে নিশ্চয়ই সত্য আছে।” এইভাবেই ঘৃণার আখ্যান সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক স্থান পায়।
তবে এই ঘটনার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো—এই বার্তাগুলো যাদের উদ্দেশে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তারা মূলত কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা গঠনের প্রক্রিয়াতেই ঢুকে পড়ছে এই বিভেদমূলক বার্তা। এই প্রজন্ম যখন নিজেদের মুসলিম সহপাঠী, শিক্ষক বা প্রতিবেশীর প্রতি সন্দেহ করতে শুরু করে, তখন সমাজে স্থায়ীভাবে বিভাজনের ভিত রচিত হয়। এটি কেবল একটি চলচ্চিত্রের প্রভাব নয়—এটি ভবিষ্যৎ সমাজ কাঠামোর উপর বিষাক্ত ছায়া।
ইতিমধ্যে ভারতে মুসলিমবিরোধী ঘৃণাভিত্তিক অপরাধ ক্রমবর্ধমান। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং দেশের একাধিক মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, বিগত দশকে ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত সহিংসতা, গণপিটুনি এবং বৈষম্যের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। সিনেমা, মিডিয়া ও রাজনৈতিক ভাষণ এই ঘৃণাকে শুধু উসকে দেয় না—তা একে ‘স্বাভাবিকতা’র চেহারা দেয়। দি কেরালা স্টোরি সেই 'স্বাভাবিক ঘৃণা'র একটি স্থাপনামূলক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা যখন পুরস্কৃত হয়, তখন তা কেবল প্রস্তাব নয়—তা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় নীতির এক প্রতীক।
এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠবেই—রাষ্ট্র কি সত্যিকারের ন্যায় ও সাম্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে? নাকি সে আজ রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক বিভাজনকেই প্রতিষ্ঠা করছে? রাষ্ট্র যদি সত্যভিত্তিক, মানবিক এবং যুক্তিনির্ভর চলচ্চিত্রকে উপেক্ষা করে এবং মিথ্যার ওপর দাঁড়ানো আখ্যানকে উৎসাহিত করে, তাহলে তার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ব কোথায় থাকে? রাষ্ট্র কি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত? সে কি এখনও সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় আস্থাবান?
সিনেমা যদি সমাজের আয়না হয়, তবে সেই আয়নার স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। সেই আয়না যদি বিকৃত হয়, তবে আমরা নিজেদেরকে ভুলভাবে দেখতে শিখি। আমরা ‘অপর’কে আতঙ্ক হিসেবে দেখবো, ‘প্রেম’কে ষড়যন্ত্র হিসেবে, এবং ‘ভিন্নমত’কে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করবো। এই বিকৃতি প্রতিরোধ করা শুধু শিল্পীদের দায়িত্ব নয়—এটি নাগরিক সমাজের, শিক্ষকের, সাংবাদিকের, এবং সব সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব।
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র যখন সিনেমাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, তখন আমাদের দায়িত্ব হলো সেই অস্ত্রকে চিনে নেওয়া। বুঝে নেওয়া—এটি একটি মিথ্যার আবরণ, যা ঘৃণাকে শিল্পের মুখোশ পরিয়ে সমাজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন সত্যভিত্তিক, মানবিক ও সহিষ্ণু শিল্পচর্চা—যা আমাদের ইতিহাস, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জটিলতাকে তুলে ধরবে বিকৃতি নয়, স্বচ্ছতার মাধ্যমে।
সত্য, শিল্প ও মানবিকতা আজ যুদ্ধে নেমেছে ঘৃণা, বিভাজন ও মিথ্যার বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে রাষ্ট্র যদি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নাগরিকদেরই হতে হবে প্রতিরোধের মুখ। সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো মানে কেবল প্রতিবাদ নয়—এটি ভবিষ্যতের পক্ষে বিনিয়োগ। দি কেরালা স্টোরি আমাদের যে প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড় করায়, তার উত্তর আমরা এখন না দিলে, ভবিষ্যৎ আর প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে না। সমাজ তখন বিভাজনে বিভ্রান্ত, রাষ্ট্র তখন পক্ষপাতদুষ্ট, এবং সত্য তখন নির্বাক হয়ে থাকবে পর্দার আড়ালে। সেই বিপর্যয় এড়াতেই আমাদের এখন রুখে দাঁড়াতে হবে—প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে, বিকৃত আয়নার বিরুদ্ধে, এবং মিথ্যার রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।

 লিখেছেন :
লিখেছেন : 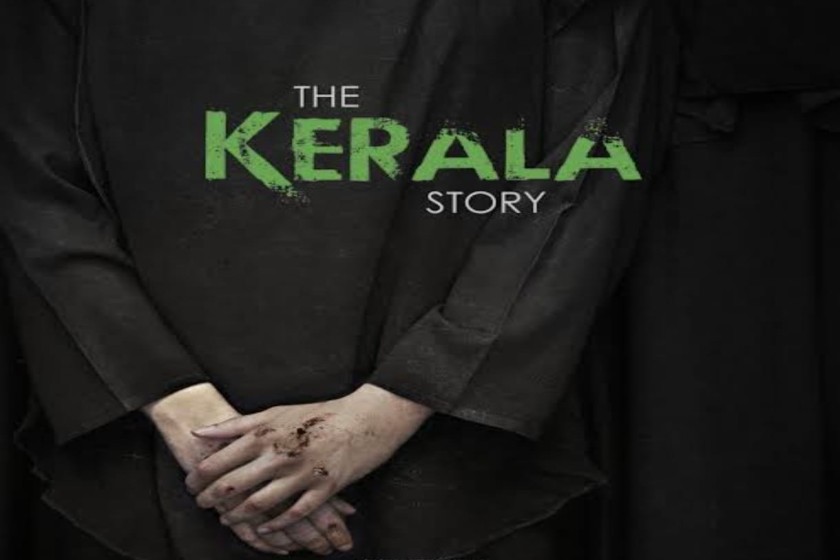



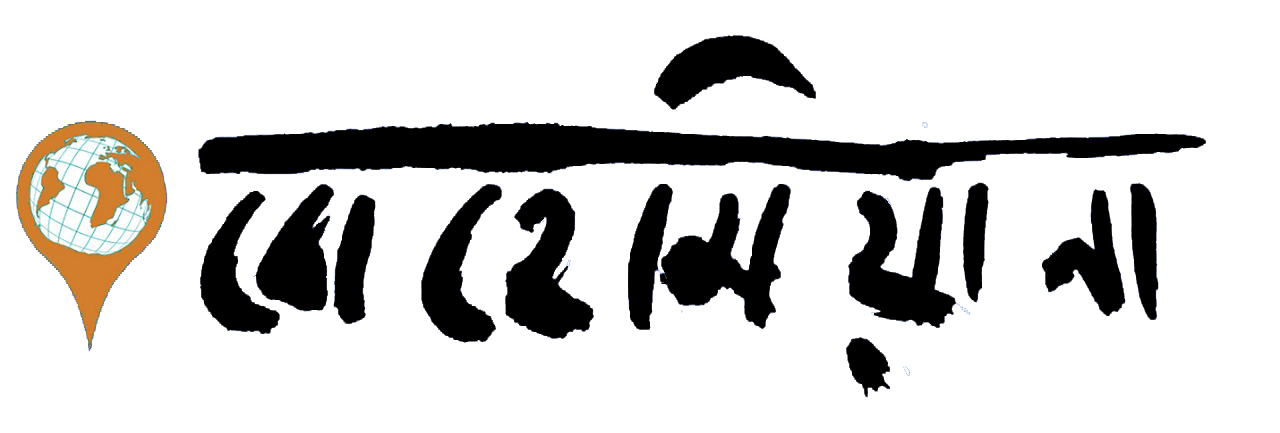
.png)