‘আর্য’ ও ‘হিন্দু’ শব্দের উৎপত্তির সাথে ‘জাতি’ ও ‘ধর্মের’ কোন যোগ ছিল না, পুরো ব্যাপারটাই ছিল এক ‘ভাষা’ গত ব্যাপার। এবং এই দুটি শব্দের উৎপত্তির সাথে বিদেশ তথা ‘ইরাণের’ নাম জড়িয়ে আছে। এখানে আমরা সেই ‘হিন্দু’ শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। হিন্দু আজ শুধুমাত্র কিছু মানুষের ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা জাতিয়তাবাদ থেকে উগ্রজাতিয়তাবাদে এবং ধর্মীয় মৌলবাদে পরিণত হয়েছে। যে কারণেই ঐতিহাসিক D. N. Jha তিনি তাঁর ‘Against the Grain’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘হিন্দু পরিচিতি আজ যারা সত্যিকারের ভারতীয় তাদের সকলের কাছে ফ্রাঙ্কেইনস্টাইনের দানবের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে”। এখন দেখে নেওয়া যাক এই হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে। শব্দগত দিক দিয়ে যদি দেখা যায় এই হিন্দু শব্দের ভারতে কিন্তু খুব একটা প্রাচীন ইতিহাস নেই। এমন কি ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋকবেদে কিন্তু একবারের জন্য ও এই হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই। হিন্দু শব্দের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ইরাণীদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ‘জেন্দ আভেস্তা’তে। পারসিকরা ভারতের নিম্নসিন্ধু অঞ্চল খ্রিষ্ঠিয় পঞ্চম শতকে জয় করেছিল। ইরাণি ভাষায় ‘স’ এর উচ্চারণ নেই তারা তার পরিবর্তে বলেন ‘হ’। ফলে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চল হয়ে গেল ‘হিদুস’ হিসাবে। আর ইরাণের হুখামনিশদের শিলালিপিতে পাওয়াযায় হি (ন) দু শব্দ টি। আর ‘হিন্দুস্থান’ শব্দটি পাওয়া যায় সামানদের শিলালিপিতে। হিন্দু বা হিন্দুস্থান ছিল প্রাচীন ইরাণীয় সাম্রাজ্যের এক ‘সিন্ধু প্রদেশ’। এই ইরাণীয়দের সিন্ধুর পরিবর্তে হিন্দু নাম দেওয়ার পেছনে কোন ধর্মীয় উদেশ্য বা ইতিহাস ও ছিল না, পুরোটাই ছিল ভাষাগত ব্যাপার। যেরকম ভাবে ‘আর্যজাতি’ হিসাবে ভারতের বৈদিক জনগোষ্ঠির মানুষদেরকে একটা তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়, বাস্তবে ‘আর্য’ যে কোন জাতি নয় ‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ ভাষাগোষ্ঠির মানুষের এক অংশ যারা ‘ইরাণ’ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে খ্রিঃপূঃ ১৫০০ অব্দ নাগাদ, একই রকম ভাবে হিন্দু শব্দের সাথে ও কোন ধর্মীয় ব্যাপার জড়িত ছিল না। তা ছিল পুরোটাই এক ভাষাগত ব্যাপার। বৈদিক জন গোষ্ঠির ভারতে আগমনের সাথে যেমন ‘ইরাণ’ সেই মত হিন্দু শব্দের উৎপত্তির পেছনে ও সেই বিদেশী ‘ইরাণে’র নাম জড়িয়ে থাকছে। বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতির সাথে সাথে ইতিহাসের নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্কারের কারণে ঐতিহাসিকরা আজ এই হিন্দু শব্দের উৎপত্তি ভারত নয় বিদেশে এবং সেই দেশটি ‘ইরাণ’ এই সিন্ধান্তে এসেছেন।১ আবার ভারতের আর একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ত্ব বিবেকানন্দের নাম আমরা জানি, তিনি বলেছেন ‘আমি হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিনা’ কারণ হিসাবে জানিয়েছেন যে ‘প্রাচীণ পারসিকদের বিকৃত উচ্চারণে ‘সিন্ধু’ শব্দই হিন্দু রুপেই পরিণত হয়। তাঁহারা সিন্ধু নদের অপর তীরবাসী সকলকেই ‘হিন্দু’ বলিতেন এই রূপ হিন্দু শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে’।মুসলমান শাসনকাল হইতেই আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দু বুঝায় না; উহাতে মুসলমান, খ্রিষ্টান, জৈন এবং ভারতের অনান্য অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে।২ আর সেই কারণেই প্রাচীন যেসমস্ত সাহিত্য যেমন ঋকবেদ,বিভিন্ন সংহিতা ও ১৮ টি পুরাণের মধ্যে কোথাও একবারের জন্য ধর্ম হিসাবে দুরের কথা, শব্দ হিসাবেও এই হিন্দু শব্দটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আজকে যারা হিন্দু ধর্মের প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেক গর্ব অনুভব করেন, তারা সেই ভারতের এই প্রাচীন কোন সাহিত্যে হিন্দু শব্দের অনুপস্থিতি নিয়ে একেবারে নিরব। এখনো পর্যন্ত তাঁরা গনেশের ‘প্লাস্টিক সার্জারি’ গোছের কোন কিছু ভ্রান্ত নিদর্শন ও খুঁজে পাননি। প্রচীন সাহিত্য তাদের এই ব্যাপারে একেবারে হতাশ করেছে।
এখন আমরা দেখে নেব এই হিন্দু শব্দ ভারতের বাইরে থেকে এলেও ভারতে কি ভাবে আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার করল এবং তা এক ধর্মীয় রূপ ধারণ করল সেই ব্যাপারে আলোকপাত করবো। একাদশ শতকের আলবেরুনির ‘কিতাব-উল-হিন্দ’। চতূর্দশ শতকে জিয়াউদ্দিন বারানির ‘তারিখ-ই-ফিরোজশাহী’। এই দুটি গ্রন্থে হিন্দু শব্দটির ব্যবহার দেখা গেছে। কিন্তু এই দুটি গ্রন্থ নেহাতই অনেক পরবর্তীকালের। সে আবার একেবারে মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখনিতে। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত ভারতের কোন রাজা গর্ব করে বলে যান নি বা কোন লিখিত বা খোদিত প্রমাণ রেখে যান নি, আমি ‘হিন্দু’ বা ‘হিন্দু ধর্মের’ শাসক বলে। এখন আমরা দেখে নেব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। হিন্দু ধর্মের সাথে সংস্কৃত ভাষার যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা বলা হয় সেই সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দের উল্লেখ আমরা কোন সময় দেখতে পাবো, সেটাই এখন দেখে নেবো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রিচার্ড সলোমন তিনি তাঁর ‘ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফি’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন ভারতে সিন্ধু লিপির পরবর্তীকালে প্রায় ১৭৫০ বিসি থেকে ২৬০ বিসি পর্যন্ত ভারতের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় নি। ২৬০ বিসির পর ভারতে যে লিপি পাওয়া গেছে তা হল ব্রাহ্মীলিপি যা অশোকের সময়কালে বলে ঐতিহাসিকরা তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আর ভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রথম বিকাশ লাভ করেছে খ্রিষ্টিয় প্রথম থেকে চতূর্থ শতকের মধ্যে। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম লিপির ব্যবহার দেখা যায় খ্রিঃপূঃ প্রথম শতকে অযোদ্ধা, ঘোসুন্ধি এবং হাথিবাদা স্টোন লিপিতে।৩ সেই সময় থেকে ধরলে প্রায় ১৩০০ বছর ধরে ভারতে যে সমস্ত সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছে তার কোনটাতেই এই ‘হিন্দু’ নামটির উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আর এই সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৩৫২ খ্রিঃ বিজয়নগর রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক বুক্কার খোদিত লিপিতে। ঐ লিপিতে তিনি নিজেকে একগুচ্ছ উপাধিতে ভুষিত করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘হিন্দুরায় সুরাত্রান’ ( হিন্দু রাজাদের মধ্যে সুলতান) পরবর্তী আড়াইশ বছর ধরে তার উত্তরসূরিরা এই উপাধি ব্যবহার করেছেন।
এর পরবর্তিকালে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত দশটি গৌড়ীয় পুঁথি পরীক্ষা করে হিন্দু শব্দটি পাওয়াগেছে মোট একচল্লিশবার। হিন্দু ধর্মের কথা পাওয়াগেছে সাতবার। কিন্তু এই কথা টা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই দশটি পুঁথির পাঁচটির মধ্যে থাকা আশি হাজার শ্লোক ঘেঁটে এই শব্দগুলি পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে এই পুঁথিগুলো ঘেঁটে হিন্দু বা হিন্দু ধর্ম নিয়ে পরিষ্কার কোন আলোচনা ও মেলে নি।৪ ঐতিহাসিক ডি. এন. ঝা তিনি তাঁর ‘prehistory of Hindu Identity’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ‘হিন্দুত্ত্ববাদ’ শব্দটি প্রথম ভারতে ব্যবহার করেছেন চার্লস গ্রান্ট ১৭৮৭ সালে। কিন্তু উনবিংশ শতকে ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক স্বার্থে একে ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনা তে ভারতীয় নাগরিকদের দুটো ভাগে ভাগ করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই দু ভাবে ভাগ করে ঢুকিয়ে দেয়।৫ ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়, যিনি অনেকটা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজে কিছু সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন সেই জন্য তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা এবং ১৮৩০ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিই ভারতীয় হিসাবে প্রথম ‘হিন্দুত্ববাদ’ কথাটি ব্যবহার করেছিলেন ১৮১৬ সালে। কিন্তু তিনি প্রাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুসারী হয়েও ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করার সাথে সাথে ভারতের সমাজে বহুবিবাহ প্রথা, সতীদাহ প্রথার মতো কু-প্রথার বিরুদ্ধে লড়াইও করেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ সরকার ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং-এর সময় আইন করে সেই সতীদাহ প্রথা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।
রামমোহনের পরবর্তিকালে হিন্দুত্ববাদকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সহযোগী রাজনারায়ন বসু। তিনি ১৮৬০ সালে জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী সভা ও ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের সাথে “হিন্দু মেলা” প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু দেশাত্ববোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করলেন। আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই-এর অংশ হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে একটি ‘জাতি’ হিসাবে উল্লেখ করলেন। আর এখানেই থেমে থাকেন নি ১৮৮১ সালে মুসলমানরা যখন ‘ন্যশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন’-এ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, সেই সময় হিন্দুদের ও ‘মহা হিন্দু সমিতি’ গঠন করা উচিত বলে প্রচার শুরু করলেন। এই হিন্দু মহা সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানালেন যে অতীতের গরিমাময় হিন্দু ধর্মের উপর ভিত্তি করে হিন্দু জাতি গঠন। ‘হিন্দু জাতি’ ও হিন্দু সমিতি অভিন্ন কিছু নয়, এখানে মুসলমানদের কোন স্থান নেই।৬ অতএব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতির আত্মপ্রকাশ হচ্ছে তাই নয় মুসলমান দের থেকে ও দেশের এই জনগণ কে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। দেশের মুল শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইতে ও তাদের আর নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতএব হিন্দুত্ববাদের বিকাশের সাথে সাথে তা ভারতীয় সমাজ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে মুলত ধর্মকে কেন্দ্র করে।
সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম আমরা জানি। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যেমে হিন্দুদের মাহাত্ব প্রচার করতে গিয়ে ব্রিটিশের গুনগান শুধু বর্ননা করেছেন এমন নয় তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে ‘darty bastards’৭ বলেছেন। শুধু এখানেই থেমে থাকেন নি তিনি তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে বিদ্রোহী ‘সন্নাসী’দের গুনগান করলেও ‘ফকির’ সম্প্রদায়কে সেই আন্দোলন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হিসাবে অত্যাচারী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ছাড় দিয়ে পুতুল মুসলিম নবাবকেই এই মন্বন্তরের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। আর ‘হিন্দু’ সন্তান নেতা সত্যানন্দকে দিয়ে বলিয়েছেন, কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়াই তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই’। তার পরেই সেই সন্তান দলকেই ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্র উচ্চারণ করে ‘মসজিদ’ ভেঙে ‘রাধামাধবের মন্দির’ গড়ার স্বপ্ন দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদের’ যে চিত্র অঙ্কন করলেন তার প্রভাব হিন্দু মানসে গভীরে প্রভাব বিস্তার করল।
মুসলিম বিদ্বেষের প্রচারের ক্ষেত্রে সাহিত্য ক্ষেত্রে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয় আর একজন হিন্দি সাহিত্যের জনক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের(১৮৫০-৮৫) নাম আমরা জানি তিনিও এই ব্যাপারে কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। ঐতিহাসিক D.N.Jha তিনি ‘Against the grain’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ‘ He depicted Muslim characters in his works as cruel, cowaradly, treacherous, bigots and uniformly depraved.’ His contemporaries described Muslim rule “as a chronicle of rape and abduction of Hindu Women, the slaughter of sacred cows, and defilement of temples”. এবং সমসাময়িক মারাঠি সাহিত্যিকরা ও এক রকম ভাবে মধ্যযুগে ভাতের মুসলমান শাসনকে উল্লেখ করেছেন, ‘the overall degradation of the Hindus”
হিন্দুত্ববাদের বিকাশ ও মুসলিম বিদ্বেষ শুধুমাত্র সাহিত্য জগতে প্রভাব বিস্তার করল তা নয় তা ধর্মীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনেও নতুনভাবে আবির্ভূত হল। এইক্ষেত্রে সবার থেকে এগিয়েছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। যিনি ১৮৭৫ সালে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এই আন্দোলনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনান্য বিদেশী ধর্মের আগ্রাসন থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার উপর জোরদেন। ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ নামক পুস্তকে হিন্দু ধর্মকে অনান্য ধর্ম থেকে রক্ষার্থে অন্য ধর্মগুলির উপর তীব্র সমালোচনা করেন। এর ফলে সাম্প্রদায়ীক মনোভাব ও ধর্মের ধর্মের মধ্যে তীব্র ভেদাভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি শুরু করেন ‘শুদ্ধি’ আন্দোলন। অর্থাৎ যে সমস্ত(বিশেষত শিখ, নীচু জাত ও অস্পৃশ্যদের) মানুষ হিন্দু ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহন করেছেন তাদেরকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা। অনেকে মনে করেন ১৯৯০ সাল নাগাদ বিশ্বহিন্দু পরিষদ শুদ্ধি করণের নামে যে ‘ঘর ওয়াপসি’ অভিযান শুরু করেছে বর্তমানে যা পুরোদমে চলছে, ‘শুদ্ধি অভিযানের’ নামে তার সূত্রপাত করেছিলেন সেই দয়ানন্দ সরস্বতী। এর পর দয়ানন্দ গোরক্ষার জন্য সারা ভারত ঘুরে প্রচার চালান গোহত্যা বন্ধের জন্য এবং ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘গোরক্ষিণী সভা’। এই গরুকে হিন্দুদের সংগঠিত করার এক হাতিয়ারে পরিনত করেন। এইভাবে গরুকে ‘হিন্দু সমাজ’ ও ‘হিন্দু জাতির’ এক প্রতিক করে তোলা হয়। দয়ানন্দের মতে এদেশে বিদেশীদের আগমন ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েতোলার উপযুক্ত হাতিয়ার হল গোরক্ষা। দয়ানন্দ সরস্বতী ও তাঁর আর্যসমাজের আন্দোলনের ফলেই ভারতে সাম্প্রদায়ীক বিদ্বেষ ও বিভাজন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৮০-র দশক থেকেই পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে যে ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে ছিল তা দেশের ইতিহাসে অভুতপূর্ব, এবং তা গোরক্ষার মত বিষককে কেন্দ্র করেই ঘটে। এই দাঙ্গা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উত্তর ভারতে। আর এই ‘গোরক্ষা আন্দোলন’ হয়ে উঠে লাগাতার সাম্প্রদায়ীক সংঘর্ষের অন্যতম কারণ।১০ হিন্দু ধর্মের নাম নিয়ে আজ আমরা গোরক্ষার যে আন্দোলন ও অত্যাচার, খুন , এমন কি বাড়িতে গোমাংশ রাখার সন্দেহে মহম্মদ আখলাক কে হত্যা পর্যন্ত করা হল। এই সমস্ত ঘটনার সূত্রপাত কিন্তু হঠাৎ করে আজ হচ্ছে এমন নয়, এর সূত্রপাত কিন্তু সেই উনবিংশ শতক থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমানে তার ধরণ ও তীব্রতা পাল্টে গেছে এই যা। জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা মতিলাল নেহেরুকেও এরা ‘হিন্দু বিরোধী ও গোমাংশ ভক্ষক’ বলেও অবমাননা করেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁর ছেলে জওহরলাল নেহেরুকে এক চিঠিতে এই হিন্দুত্ববাদী শক্তির থেকে সচেতন থাকার ও পরামর্শ দিয়েছিলেন।
দয়ানন্দ সরস্বতীর মত অনেকটা একই ধরণের চিন্তা প্রচার করেগেছেন স্বামীবিবেকানন্দ। তিনি প্রাচীন ভারতের বেদ উপনিষদের মত বিষয়কে গৌরান্বিত করেছেন। এবং তিনি মনে করেন সেই আদর্শ অনুষারে ভারতে প্রায় ২০০০ বছর ধরে ‘শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতী’ ব্যপক ভাবে হয়েছিল। যদিও দয়ানন্দের মতো গোরক্ষার আন্দোলকে তিনি কোন দিন সমর্থন করেন নি, উলটে বলেছেন, ‘Young man in India to eat beef in order to develop muscles’.১১ কিন্তু আবার দয়ানন্দের মত অনান্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিতদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। কারণ বিবেকানন্দ মনে করতেন, ‘আমাদের ধর্ম অনান্য ধর্মের থেকে আরো খাঁটি, কারণ তা কোনদিন রক্তপাত ঘটায় নি’ তিনি এর সাথে আরো যোগ করলেন যে মুসলমানদের ভারতে আসার আগে ভারত তরবারি, হত্যা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কাকে বলে জানত না। মুসলমানরাই ভারতে এসব এনেছে। মুসলমান আক্রমনের আগে হিন্দুরা জানত না ধর্মের জন্য নির্যাতন কাকে বলে। যখন বিদেশীরা নির্যাতন, হিন্দুদের উপর আরম্ভ করিল, তখনই হিন্দুদের এই অভিজ্ঞতা হইল”।তিনি হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে প্রচার করলেন, “হে আমার স্বদেশবাসীগণ… আমি পৃথিবীর যে সকল জাতি দেখিয়াছি, সেই বিভিন্ন জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছি যে আমাদের হিন্দু জাতিও মোটের উপর অনান্য জাতি অপেক্ষা নীতিপরায়ন ও ধার্মিক”।১২ নিজের জাতিকে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করার উদগ্র ইচ্ছা ও আদর্শকে আমরা দেখেছি মুসোলিনী ও হিটলারের আদর্শের মধ্যে। বিবেকানন্দ নিজের হিন্দু জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি হিসাবে গন্য করলেও নিজেই কিন্তু সতীদাহ প্রথার মত এক প্রাচীন নারকীয় প্রথার ঘোর সমর্থক ছিলেন। গঙ্গায় কন্যাসন্তান বিসর্জনকে তিনি অস্বীকার করেছেন। বিধবা বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরের উদ্যোগকে তিনি কোনদিন গুরুত্ব দেননি। অধিকাংশ স্থানে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতা করেছেন, বৈধব্যকে গৌরবময় ও কাম্য বলে মনে করেছেন। বাল্যবিবাহ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন কারণ খুঁজে পাননি। তাঁর কাছে হিন্দু নারীর আদর্শ হল সীতা। কারণ সীতা সর্বংসহা ও পতিপরায়নতার প্রতিক। আবার তিনি বলেছেন নারী জাতিকে শাসনে রাখিতে এখনো পুরুষের প্রয়োজন। জাতি বিভাগ অনন্ত কালের জন্য থাকিয়া যাইবে। কারণ জাতি বিভাগ প্রকৃতির নিয়ম। ‘ব্রাহ্মণ’ হিন্দু জাতির পূর্বপুরুষের আদর্শ ছিলেন, এবং বর্তমানেও হিন্দু জাতির আদর্শ হল ব্রাহ্মণ।
বালগঙ্গাধর তিলক যাকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসক ব্রটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক অন্যতম নেতা হিসাবে জানি। ব্রিটিশ সরকার সেই তিলককে গ্রেপ্তার করলে তার প্রতিবাদে বম্বের শ্রমিকরা যে ধর্মঘট ডেকেছিল তা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বটে। কিন্তু সেই তিলক ও হিন্দু ধর্মের উত্থান ও বিকাশে বেশ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালে তৈরী করলেন ‘গোহত্যা নিবারণী সভা’ । সেই গোহত্যার জন্য সেখানে তিনি মুসলিমদের সরা সরি অভিযুক্ত করলেন। ১৮৯৪ সালে তিলক মহারাষ্ট্রে চালু করলেন ‘গনপতি’ ও ‘শিবাজী’ উৎসব। ঘোষিত লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লোক জোড় করা। কিন্তু এটা এমন একটা সময়ে ডাক দেওয়া হয়েছিল যখন এর ঠিক আগেই বম্বেতে ও অন্যত্র সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা ঘটে গেছে। এমনকি বম্বের শ্রমিকরাও সেই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এই উৎসব দুই সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাকে আরো প্রসারিত করল। আর শিবাজী উৎসবের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী হিন্দু জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলা। এর পর শিবাজী যেভাবে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি আফজল খাঁ কে হত্যা করেছিলেন তাকে গৌরন্বান্বিত করে শিবাজীকে মুসলমান বিরোধী হিন্দু শাসক ও গোরক্ষক হিসাবে বর্ণিত করা। তিনি আহ্বান জানালেন দেশের ছোটো ছোটো শক্তি গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক হিন্দু নেশান তৈরী করা। আর প্রত্যেক হিন্দুর এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আবার আর্যদের আবির্ভাব সম্পর্কে ও এক নতুন তথ্য হাজির করলেন। ভারতে বৈদিক যুগকে গৌরবান্বিত করে আর্যদের ভারতে আগমনের সময়কাল প্রথমে ১৫০০ খ্রিঃ অব্দ থেকে পিছিয়ে ৪০০০ খ্রিঃ অব্দঃ , এবং তার পর আরো পিছিয়ে দিয়ে ৮০০০ খ্রিঃ অব্দঃ করে দিলেন এক অবৈজ্ঞানিক তথ্য হাজির করে। এবং পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার উদ্ভব এই আর্যরাই করেছেন বলে তিনি দাবী করে বসলেন। এই ভাবে তিলক একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন সেটা যেভাবে প্রচারের আলোয় আসে অন্যদিকে তিনি যে মুসলমান শাসন বিরোধী পুনরুত্থানবাদী গোঁড়া রক্ষনশীল এক হিন্দু, এক ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী’ বা ‘হিন্দু নেশান’ তথা ‘হিন্দু রাষ্ট’ গঠনে নিবেদিত প্রাণ এক হিন্দু পরিচয় –দূর্ভাগ্যজনক ভাবে তা আড়ালে থেকে যায়।১৪
ভিনায়ক দামোদর সাভারকার, দক্ষিনপন্থী সংগঠন হিন্দু মহাসভার সাত বারের সভাপতি যিনি আজকের হিন্দুত্ব আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। তাঁর এই হিন্দুত্বের আদর্শ বোঝাবার জন্য ১৯২৩ সালে প্রকাশ করলেন ‘Hindutva: who is Hindu’? এই বইতে তিনি হিন্দুত্বের বৈশিষ্ঠ ব্যখ্যা করে দেখালেন যে ‘হিন্দুত্ব কোনও শব্দ নয়, এটি একটি ইতিহাস। শুধু আমাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ইতিহাস নয়, বরং সামগ্রিক ইতিহাস”। আর এই সাভারকারের ব্যখ্যা অনুযায়ী হিন্দুত্ব গঠনকারী উপাদানগুলির অন্যতম হল ‘এক সাধারণ রাষ্ট্র, সাধারণ জাতি ও সাধারণ সংস্কৃতি’। আর এই ‘সাধারণ রাষ্ট্র’ হল এক ‘হিন্দু রাষ্ট্র’। যেখানে শুধু হিন্দুরাই বসবাসের অধিকারী। আর এই হিন্দুরাই একমাত্র হিন্দুত্বের ধারক, কারণ তারা অতীতের ‘আর্য জাতি’ থেকে অদ্ভুত। আর মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা এই রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না কারণ ‘ যখন থেকে তারা এক নতুন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তারা সামগ্রিকভাবে হিন্দু সংস্কৃতিকে তাদের নিজেদের বলে মেনে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এই ভাবে ভিন্ন জাতি মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের ভারতীয় জাতিয়তার অংশ হিসাবে গন্য করার সমস্ত সম্ভাবনাকে নাকচ করা হল। এমনকি তাদের ‘পিতৃভুমি’ ও ‘পুন্যভূমি’ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তাদের বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করা হল। ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদের হিন্দু মহাসভার ১৯ তম অধিবেশনে সাভারকার জানালেন যে, “বর্তমানের ভারতকে একটি এককেন্দ্রিক ও সমসত্ব জাতি হিসাবে ধরে নিলে চলবে না, এখানে প্রধানত দুটি জাতি আছে হিন্দু ও মুসলমান”। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাভারকার এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে আবির্ভূত হলেন। এছাড়াও ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগস্ট সাভারকর নাগপুরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, “ মিঃ জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের সাথে আমার কোন কলহ নেই। আমরা, হিন্দুরা, নিজেরাই একটি জাতি এবং এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি জাতি”। উপরের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের জন্য শুধু মুসলিম লিগ দ্বায়ী নয় হিন্দু মহাসভার ভূমিকা ও কোন অংশে কম ছিল না। দেশ বিভাগের পর যেহেতু সমস্ত হিন্দুকে নিয়ে ভারত বা সমস্ত মুসলিমদের নিয়ে পাকিস্থান গঠন হয় নি যা সম্ভব ও ছিলনা ১০-১২ শতাংশ মুসলিম ভারতে থেকে গেল তাই সাভারকার দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষনা করলেন ‘সমস্ত রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ করো, হিন্দুদের সামরিকীকরণ করো’।১৫ সেই লক্ষ্য কে সামনে রেখে ভারতের রাজনীতি যে অনেকটাই এগিয়েছে বর্তমানে আমাদের ভারতে ধর্ম আর রাজনীতি যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে সমাজ জীবনে তা আমরা প্রতি মূহুর্তে অনুভব করতে পারছি।
হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুত্ববাদের প্রসারের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ত্ব তাদের নানা সাহিত্য কর্ম নানা ভাবে কাজ করেছে সেই মত কিছু ঐতিহাসিক ও এই ব্যাপারে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ঐতিহাসিকদের মধ্যে এক পরিশ্রমী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ত্ব। তাঁর এই প্রভাব শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু আধিপত্যবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তিনি মুসলিম বিরোধী এক অন্যতম ঐতিহাসিক ও বটে। ভারতের হিন্দুত্ব বাদের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যপারে প্রাচীনকাল থেকে কিভাবে ভারত থেকে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার ও এক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন। এই ব্যাপারে আর.এস.এস এর প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওকার এর বক্তব্যের সাথে তার বক্তব্য ও হুবহু মিলে যায়। ঐতিহাসিক ডি এন ঝা তিনি তাঁর ‘against the Grain’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ‘ He credited the Hindus for their “spirit of religious toleration” and denigrated the Muslims for their intolerant and oppressive rule and for destroying Hindu temples’. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতো আর একজন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর তিনি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি ভারতের এই মধ্যযুগের সময়কালকে বর্ণনা করেছেন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী সংঘর্ষের ইতিহাস। তিনি এও বলেছেন যে এই সমগ্র মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের মুল লক্ষ্যছিল ‘the conversion of the entire population to Islam’। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে মধ্যযুগের এই শাসনকালকে ‘মুসলিম শাসন’ বলে উল্লেখ করেছেন। আর এই মুসলিম শাসনের কি কি খারাপ দিক ছিল তার সবিস্তার উল্লেখ করেছন। এই মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে শিবাজির উত্থানকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান বলে বর্ণনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে সমগ্র মুসলমান শাসনকে তিনি দেখিয়েছেন ‘Muslim as oppressors, and inherently intolerant of Hindus” হিসাবে।
এই অত্যাচারী ও অসহিষ্ণু মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারের অঙ্গ হিসাবে আর এস এস এবং তাদের অনান্য সংগঠন গুলো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে হঠাৎ করে ব্যপক পরিমানে প্রচার পেতে থাকে। ১৯৮০ র দশকে এসে দেশের সরকারী চ্যানেল তাদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে ভারতের দুটি হিন্দু ধর্মের মহাকাব্য ‘রামায়ন’ ও ‘মহাভারত’ এর প্রচার শুরু হয় ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ এই সময়কালের মধ্যে। আশ্বর্যজনকভাবে ঐ সময় থেকে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তাদের দাবী আরো তীব্র করতে থাকে হিন্দু ধর্মীয়স্থানকে মুক্ত করার জন্য। তারমধ্যে অন্যতম হল অযোদ্ধা। আর এই অযোদ্ধাই হল রামায়ণের রামের সঠিক জন্মস্থান। ঠিক এর পরেই আমরা দেখলাম সংঘ পরিবার এবং তাদের অনান্য সংগঠনগুলো ভারতে ১৫২৭-৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে গড়েওঠা এক প্রাচীন মসজিদ কে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন। দেশে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকার বর্তমান। পুলিশ ও প্রশাসন উভয়ের উপস্থিতীতে বিজেপি ও অনান্য হিন্দু সংগঠনের নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ বছরের এক মসজিদকে ভেঙে ফেলা হল। প্রাবন্ধিক অশোক মুখোপাধ্যায় তিনি তাঁর ‘মন্দির মসজিদ বিসম্বাদ’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ‘এই “রামন্মভূমি” উদ্ধার ও রামমন্দির প্রতিষ্ঠার উন্মত্ততাকে এই জঙ্গি মৌলবাদী চক্র এমন একটা উচ্চগ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল যে তাদের সামনে অযোদ্ধা বা উত্তর প্রদেশে কেউ এই কাঠামোটিকে “বাবরি মসজিদ” বললেও তাকে মার খেতে হচ্ছিল। সুতরাং যাকে ওরা ভেঙেছে সেটা যে মসজিদ, তা-ও প্রমান-সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে পড়েছিল”।১৬ সারা ভারত সহ বিশ্বের সমস্ত দেশের মানুষ সেই ছবি টিভিতে দেখতে পেল কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করার জন্য দেশের কোন সরকারই এগিয়ে এলনা। এবং বর্তমানে দেশের বিচার ব্যবস্থায় কেউ সেই ঘটনার জন্য কোন শাস্তি ও পেলনা। প্রাবন্ধিক অশোক মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে বেশ স্মরনীয়,
“বাবরের নামে মসজিদ নাকি রামনামি মন্দির –
আমার কি বল, ফল যাই হোক বিচারের সন্ধির?
যে শিশু মরেছে পুষ্টি না পেয়ে ক্ষুধা রোগ অনাদরে
দেখেছ কি বাছা খোদা ঈশ্বর – কার ছিল সুনজরে?”১৭
মিথ্যা প্রচার হিন্দুত্ববাদী শক্তির এক বড় হাতিয়ার। ভারতবর্ষ আগামীদিনে মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে যাবে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই শক্তির এটা একটা মিথ্যা প্রচারের এক বড় হাতিয়ার। এই প্রচার শুধু এখন হচ্ছে এমন নয় আজ থেকে ১০০ বছর আগেও এই মিথ্যা প্রচার ছিল। আমি একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ১৯০৯ সালে কলকাতার ইউ. এন. মুখার্জি ‘হিন্দুজঃ এ ডায়িং রেস’ নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করে সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুদের ক্রমহ্রাসমান অবস্থা দেখালেন। ১৯১২ সালে আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সাথে এক স্বাক্ষাতকারে তিনি বললেন, যে হারে হিন্দু হ্রাস পাচ্ছে, তার ফলে নাকি আগামী ৪২০ বছরের মধ্যে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর পর তারা একজোট হয়ে আর্য সমাজের নেতৃত্বে ধর্মান্তরিত করার কর্মসূচীতে আরো জোর দিলেন।১৮ অর্থাৎ বর্তমানকালে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে যেভাবে সোচ্চার ও সক্রিয় তার যাত্রা ১০০ বছর আগেই শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যার হার ৭৯.৮%, মুসলিম ১৪.২%। আর যদি জনসংখ্যার হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে ১৯১২ সালের থেকে বর্তমানে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা হিন্দুত্ববাদী নেতাদের কথামত কমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াত দূরের কথা প্রায় তিন গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন উৎসাহী ব্যক্তি চাইলেই ১৯১১ সালের সেনসাস ও ২০১১ সালের সেনসাসের রিপোর্ট দেখে নিতে পারেন।
আজকের এই হিন্দুত্ববাদ শুধুমাত্র ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আজ আমাদের দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি অর্থনীতি সহ জীবনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে জড়িত। দেশের নাগরিক হিসাবে কার কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সবকিছুই সে আজ ঠিক করে দিচ্ছে। ঐতিহাসিক ডি এন ঝার কথা মতো, ‘They censure anything that does not fit into their scheme’. ভীন্ন মতাবলম্বী বই পোড়ানো, সিনেমাকে বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো এবং সমস্ত ব্যপারে অসহীষ্ণুতার মতো এক সংস্কৃতিকে আরো উজ্জীবিত করা। যে কোন ব্যক্তিকে জোর করে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করা গরুমাংশ খাওয়া, বাড়িতে গরুমাংস রাখা এবং গরু কে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় অত্যাচার এবং হত্যা পর্যন্ত করছে। এটাই এখন ভারতের হিন্দুত্ববাদের সংস্কৃতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপরের এই সমস্ত অত্যাচারের মুল উদ্দেশ্য হল দেশে হিন্দুত্ববাদ কে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই ডি এন ঝার এক উক্তি এই প্রসঙ্গে বেশ প্রাসঙ্গিক, “Hindu Identity has now become a Frankenstein’s monster for all that is truly Indian”.
তথ্য সূত্র-
১। ডি এন ঝা- হিন্দুদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে- পৃ-৩২।
২। স্বামী বিবেকানন্দ বানী ও রচনা – ৫ খন্ড- জাফনা বক্তৃতা।
৩। Richard Solomon - Epigraphy In India- oxford university press. p-10-33
৪। সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদ। ভিত্তি উদ্ভব বিকাশ- আপডেট স্টাডিগ্রুপ- সেতু প্রকাশনি- পৃ- ১৭।
৫। D. N. Jha- Against The Grain- Notes on Identity, Intolarance and History. 2021. P-13.
৬। সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদ- পৃ-৯৫।
৭। D. N. Jha- Against the Grain- p-17.
৮। সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদ –পৃ- ১১৬-১১৯।
৯। D. N. Jha- Against the Grain- p-17.
১০। Gyanendra Pandey- The constraction of communalism in colonial North India- New delhi- Oxford University press- p- 163.
১১। D. N. Jha- Against the Grain- p-16.
১২। সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদ- পৃ- ১২৪।
১৩। ঐ- পৃ- ১২৬-১২৭।
১৪। ঐ – পৃ- ১০৮-১১১।
১৫। ঐ – পৃ- ১৮৫-১৯০।
১৬। অশোক মুখোপাধ্যায়- মন্দির মসজিদ বিসম্বাদ- প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস বনাম হিন্দুত্ববাদী মিথ্যাচার- বহুবচন প্রকাশনি- কলকাতা- পৃ- ১১।
১৭। ঐ – পৃ- ১০।
১৮। সংঘ পরিবার ও হিন্দুত্ববাদ- পৃ-১৪২।
১৯। D. N. Jha- Against the Grain- p-২৯।

 লিখেছেন :
লিখেছেন : 



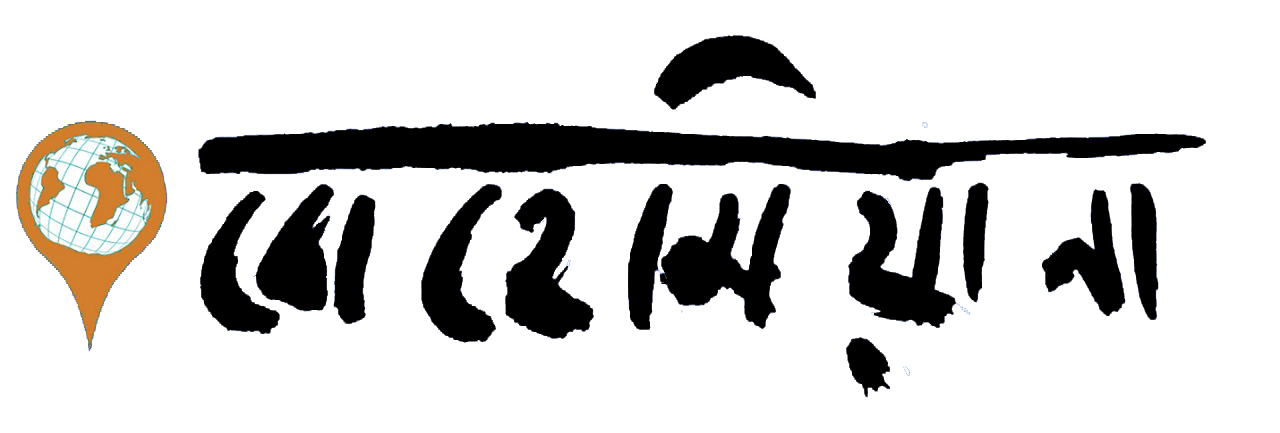
.png)