স্বাধীনতার নামে বাবুদের বিকিকিনি আর শিকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা প্রজন্মের পর প্রজন্ম পেরিয়েও আজও মিলিয়ে যায়নি। তারই মধ্যে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার মতো বাঙালিকে আবারও সন্দেহভাজন হিসেবে দেগে দেওয়া চলছে সর্বত্র। আর তাই আজো বাংলার শ্রমজীবি মানুষ যারা হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কাজের খোঁজে গেছেন, যে উদ্বাস্তু মানুষ অনেক কষ্টে দেশ ছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা বুকে চেপে ঘর বেঁধেছিলেন নতুন করে তাদের আজো কাঁটাতারের ভূত তাড়া করে বেড়াচ্ছে।
মহারাষ্ট্রে কাজ করতে যাওয়া মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ছেলে নাজিমুদ্দিন মণ্ডল এখন আর উঠে দাঁড়াতেই পারছেন না। তাঁর বাড়িতে কোনওরকমে উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে তিনি কাঁপতে থাকেন। জুন মাসের প্রথম দিকে তাঁর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার স্মৃতিরোমন্থন করতেও তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়। "আমার শুধু মনে আছে, মুম্বাইয়ের কানাকিয়া পুলিশ স্টেশনের লোকেরা আমাদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপর কড়া নিরাপতার মধ্যে আগরতলার বিমানে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারা আমাদের উলঙ্গ করে, তল্লাশি চালায়, বেধড়ক মারধর করে। তারপর, সেই দুঃস্বপ্নের রাতে, বিএসএফ আমাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটি জলাভূমিতে নিয়ে গিয়ে সেখানে ফেলে রাখে।
শুধু নাজিমুদ্দিন নয়, এই বাংলার শ্রমিক সামিম খান, দেবাশিস দাস, উত্তম ব্রজবাসী সহ অনেকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই ঝড়। আবারও কোটি কোটি মানুষ দেশহীন হওযার মুখে দাঁড়িয়ে। মালদার শ্রমিক আমির শেখকে তো পে লোডার দিয়ে কাঁটাতারের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বি এস এফ। এ কোন গণতন্ত্র যেখানে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধে নামে রাষ্ট্র?
এদিকে স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে মিডিয়া চিৎকার জুড়ে দিল নেপাল, বাংলাদেশ আর বার্মা থেকে নাকি কোটি কোটি লোক বিহারের ভোটার লিস্টে ঢুকে গেছে। পাশাপাশি কিছুদিন পরেই কে বা কারা বলা শুরু করলো, ৪১ লক্ষ মানুষকে নাকি খুজে পাওনা যায়নি তাঁদের আবাসস্থলে, তাই এনারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন। ওদিকে যখন বিহারের ভোটার তালিকার ভিনদেশী ছেঁকে তোলার খেলা চলছে, তখন বাংলায় একই ভাবে কখনো ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী, কখনো ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাদের গল্প আসছে। বিহারে এই করে প্রায় ৬৬ লক্ষ মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। বলা বাহুল্য তাঁর মধ্যে বেশীরভাগই নিম্নবর্গের মানুষ। তাহলে গণতন্ত্রের সার্বজনীন ভোটাধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চায় এই ফ্যাসিস্তরা। অদ্ভুত নীরবতা পালন করছে সিপিআইএম এই বিষয়ে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে তাঁরাও এই অনুপ্রবেশের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। এদিকে বাংলার শাসকদল বাঙালী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন এবং ভোটার তালিকা সংশোধনকে নির্বাচনী ইস্যু বানিয়ে বাংলার অস্মিতার নামে শপথ নেওয়ার নাটক ভালোই করল। কিন্তু নিঃশব্দে স্কুলে স্কুলে টিচারদের বি এল ও-র ডিউটি অর্থাৎ ভোটার তালিকা সংশোধনের ডিউটি দেওয়াও চলছে সরকারিভাবেই। বাংলার সংস্কৃতির দফা রফা করে জগন্নাথ মন্দির থেকে হনুমান মন্দির, হিন্দিতে ভাষণ সবই চলছে এই বাংলায়। সর্বোপরি ভুলে গেলে চলবে না অটল বিহারী বাজপেয়ীর কালে এন আর সি-র পথ প্রশস্ত করতে যে ২০০৩ এর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আসে তাতে সই করে তৃণমূল, সিপিএম, ডি এম কে সহ প্রায় প্রত্যেকটি বিজেপি বিরোধী বড় বড় দল। ফলে নেতাদের কথায় না ভরসা করে বাস্তবটা বোঝার নিশ্চই দরকার আছে। অনেকে বলছেন আইন বিষয় সচেতন করা দরকার জনগণকে। এদিকে প্রত্যেকটি নাগরিকত্ব আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা তা নিয়ে বহুধা বিভক্ত। মোদ্দা যেটুকু বোঝা গেছে তা হল ১৯৫৫ সালের প্রথম নাগরিকত্ব আইনে যে নিঃশর্ত অন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয় ছিল তা তারপর থেকে আসা সমস্ত সংশোধনীতেই নাকচ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রত্যেকটিই (১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩, ২০০৫, ২০১৫, ১০১৯) জন বিরোধী। এবার তার মধ্যে ২০০৩ এর আইনে প্রথম নাগরিক পঞ্জি গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল ফলে ওই আইন প্রাশ হওয়ায় এন আর সির রাস্তা তৈরি হয়।
২০০৩ সালে পাশ হওয়া এই আইন সকলের জন্যই বিপজ্জনক। প্রথম বিপদ বুঝতে পেরেই পথে নামেন উদ্বাস্তু মানুষ যাঁদের একটা বড় অংশ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। তাঁদের “অনুপ্রবেশকারী” হিসেবে দেখার ফলে নানাভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। তবে বিপদ সব্বার। যে দেশে মেকী উন্নয়নের বলি হয়ে ২০ কোটি মানুষ উচ্ছেদ হয়, প্রতিবছর ঝড়ে-বন্যায়-নদী ভাঙনে শয়ে শয়ে মানুষের ঘর ভেসে যায়, যে দেশে ৪০-৫০ শতাংশ মানুষের হাতে আজো জমি-বাড়ির মালিকানাই নেই সেখানে বাড়ি-জমির দলিল, মা-বাবার জন্মের সার্টিফিকেট কজনই বা দেখাবেন। কি হবে জনজাতির মানুষের? তাদের কাছেই বা নথি কোথায়? কে সুরক্ষিত রেখেছে এসব? রাখা সম্ভব আদৌ? জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের যা যা প্রমাণ দাবি করা হয়েছে, ২০০৩ সালের আইলের ২(১) বি বা ১৪-এ ধারায় তা দেখানো অসম্ভব বেশীরভাগ মানুষের পক্ষেই, বিশেষত সমস্ত 'প্রান্তিক ' মানুষের পক্ষে তো বটেই।
সিএএ-র বিধি কার্যকর হয়েছে ২০২৪ এ। বিধি দেখলে বোঝা যাবে সি এ এ আসলে উদবাস্তু দলিত মানুষের সামনে একটা টোপ। যা যা নথি চাওয়া হয়েছে তা প্রায় কোনো উদবাস্তু মানুষই দেখাতে পারবেন না। জে পি সি রিপোর্ট বলছে কেবলমাত্র ৩১,৩১৩ জন যাদের কাছে ভিন্ দেশ থেকে আসার প্রমান আছে তারাই কেবল নাগরিকত্ব পাবেন। তাই উদ্বাস্তু মানুষের কাছে আর্জি সি এ এ-র চক্করে পড়ে নিজেই নিজেকে বিদেশী ঘোষণা করতে যাবেন না। এত কথা বলার কারণ একটাই কাগজ জড়ো করার মধ্যে আপনার সুরক্ষা লুকিয়ে নেই। আপনি কোনোদিনই ওদের নথি দেখিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারবেননা। মনে রাখতে হবে আসামে যে ১৯ লাখ বাঙালীর নাগরিকত্ব হরণ হয়েছিল, তার মধ্যে মুসলমান- অমুসলমান সকল বাঙালী ছিলেন। সে ছবিটা মনে করে আজকে আবার উপলব্ধি করার সময় এসেছে আইনি জটিলতা আর শর্তের জালে আপলার মুক্তি নেই, বরং প্রশ্ন করুন ওরা আপনার কাছে প্রমাণ চাইছে কোন অধিকারে? বার বার একটাই দাবী তুলুন একজনকেও বেনাগরিক করা চলবে না, প্রত্যেকটি জন বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে, নাগরিকত্ব সুরক্ষিত করুক সরকার, প্রমাণ দেবার দায় জনগণের নয়।
আর প্রশ্ন করুন এই কাঁটাতারকে যা আজো আপনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। কাদের স্বার্থে একটা জাতির বুক চিরে দু'টুকরো করা হল। বাংলার আপামর দলিত, মুসলমান, জন জাতির মানুষ যারা আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের মত নেওয়া হয়েছিল তখন? আসুন এই সংকটের মুহূর্তকালে ফিরে দেখি সেই কাঁটাতার পূর্ব বাংলাকে। কাদের স্বার্থে কাদের হাত ধরে এই টুকরো জাতিকে পেলাম আমরা তা বুঝতে গেলে বাংলার ক্ষমতা বিন্যাস, ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরে ভদ্রলোক বাবুদের উত্থান, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের দালালী এবং স্বার্থ আর দিল্লির চোখরাঙ্গানি এবং দখলদারী এই সম্পূর্ণ ইতিহাসটা মনে হয় বিশেষ জরুরি। তাই শুরু করছি একেবারে পলাশীর সময় থেকেই।
পলাশীর পর থেকেই বর্ণহিন্দু, মুসলমান এবং দলিত এই বিভাজন রেখা নতুন চেহারায় আরও প্রকট হতে থাকে। এক শ্রেণির স্বার্থ আবার একে জল-সার জোগায়। আগেই বলেছি ১৭৫৭-এর পর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পর্যন্ত এক শ্রেণির বর্ণহিন্দু গ্রাম থেকে শহরে এসে কোলকাতা, চুঁচুড়া চন্দননগর ইত্যাদি জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের বেনিয়া হিসেবে কাজ করে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার জমিতে টাকা ঢালেন। মোদ্দা হল ইংরেজদের সম্পূর্ণ সহায়তায়, এক নব্য জমিদার শ্রেণি গড়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে তা আরও পাকাপাকি ভাবে গেঁড়ে বসে। আর একদিকে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু 'বাবু সম্প্রদায়' গড়ে ওঠে যারা মূলত ব্রিটিশ অফিস-কাছারির কেরানি। এদিকে সদ্য নবাবী আমলের অবসানের ফলে সেই সময় মুসলমানরা কিন্তু ব্রিটিশদের তেমন আস্থাভাজন নয়। তারাও অভিমানে পশ্চিমী শিক্ষা থেকে মুখ ঘুরিয়েই রেখেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন বা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বর্ণহিন্দু আধিপত্যের একটা ছাপ ধারাবাহিকভাবে থেকেছে। মুসলমান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধারা আলাদাই থেকেছে কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাদের স্থানও দেওয়া হয়নি আর তাদের অবদানও ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থেকেছে। আমাদের অবচেতনে 'বাঙালি' বলতে বর্ণহিন্দু বাঙালি-এই ভাবটাই গেঁড়ে বসেছে। আর তাদের মনস্তত্ত্বের নিরিখেই সব কিছুকে বিচার করার প্রবণতা কাজ করেছে আমাদের মধ্যে। ব্রিটিশদের কেরানি এই বাবু সম্প্রদায় ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার বুকে উত্থান ঘটে আর একটি প্রভাবশালী শ্রেণির- মাড়োয়ারি বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি। ১৮৪০-এর দশকে কোলকাতার বড়বাজারে ৪৭ জন তুলোর ব্যবসায়ীর মধ্যে মাত্র ৮ জন ছিলেন বাঙালি। ব্যাঙ্কিং ব্যবসাও ছিল অবাঙালিদের হাতে। পাট ছিল বাংলার বাণিজ্যিক ফসল। সমগ্র পৃথিবীতে পাটের উৎপাদন ছিল বাংলার প্রায় একচেটিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাড়োয়ারি আড়তদারের ভিড় জমল। পাটের ব্যবসার বড় অংশ চলে গেল মাড়োয়ারিদের দখলে। চাষিরা দেনার দায় ডুবে থাকত আর এই মাড়োয়ারি মজুতদার আর ব্যবসায়ীরা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। গোয়েঙ্কা, বিড়লা, বাজোরিয়া, কানোরিয়ার মতো মাড়োয়ারি-গুজরাটি পুঁজিপতিদের পরিচয় আর ব্রিটিশের সাথে তাদের সখ্যতার কথা তো আগেই বলেছি। এবার দেখব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন গ্রামের কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়, তখন এই মাড়োয়ারি চটকল মালিক, ব্যবসায়িদের কী বিপুল পরিমাণে মুনাফা বেড়েছে।
যুদ্ধের বছরগুলোতে চার বছরে চার গুণ সম্পদ বৃদ্ধি হয় বিড়লার। চোখে পড়ার মতো বিষয় হল শতকরা ৯০ জন জমিদার ছিলেন বর্ণহিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষক ছিলেন মুসলিম বা দলিত অর্থাৎ নিম্নবর্গের। রংপুর গ্রামের আবেদ আলি মিয়াঁ পাট চাষিদের শোষণের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর ভাষাতেই শুনি-
"মাড়োয়ারিরা লাখ পতি, হাল ঠেলেও ভাই ভাত পাবে না।
আছে তাদের চক্ষে জ্যোতি, চুনে নিছে বঙ্গের মতি।...
দিনে দিনে দেখতে পাবে,
মাড়োয়ারিদের হাতে যাবে; তোঘরা দেশে কলা খাবে, কান্দবে ঋণ হিসাবের দিনা।
দেখবে তোরা দুদিন পরে; সব যাবে মাড়োয়ারির ঘরে।"
গ্রামের গরিব মুসলমান চাষির ঘৃণার সঙ্গত কারণ রয়েছে।
তবে বিড়লা, গোয়েঙ্কার মতো মাড়োয়ারি মুৎসুদ্দি ছাড়াও ইসফাহানি, স্যার রফিউদ্দিনের মতো মুসলমান বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও ছিল বাংলায়। এই মুসলমান ব্যবসায়ীদের অনেকে উত্তর ও পশ্চিম ভারত থেকে আবার কেউ কেউ ইরান বা কাবুল থেকে আসা। এদের মূল ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল কোলকাতা। ইসফাহানি চা, নীল, চামড়া, তুলো, চট ইত্যাদি রপ্তানি করতেন। আদমজী হাজী দাউদ পাট রপ্তানি করতেন আর চটকলও স্থাপন করেছিলেন।
‘হিন্দু’ এবং মুসলিম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো সাম্প্রদায়িক চেতনায় আচ্ছন্ন ছিল দুটো কারণে। তাদের মধ্যে পুরনো ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি সহজাত আনুগত্য যেমন ছিল তেমন কিছু স্বার্থও ছিল। ধর্মকে তারা ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বধর্মীদের সমাবেশিত করতে। শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেই ধর্মকে তারা ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। মাড়োয়ারি-গুজরাটি-পার্সি পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় মুসলিম শিল্পগোষ্ঠীগুলো ছিল অনেকটাই দুর্বল। ১৯২৭ এ ফিকি তৈরি হওয়া থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ২১ বছরে মাত্র দুবার দুজন মুসলিম ব্যবসায়ী এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছিলেন। ঘনশ্যামদাস বিড়লা এবং
পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী- তাঁরাই মূলত চালাতেন এই ধরনের সংস্থা। ইসপাহানি লিখেছেন-"১৯৪৭-এর আগে ভারতে ব্যবসা ও শিল্প ‘হিন্দু’ বেনিয়া এবং ব্রিটিশ শিল্পপতির প্রায় একচেটিয়া ছিল।"বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবেই চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এর গুরুত্ব অপরিসীম। শাসন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে চাকরি ক্ষেত্রে আসন ভাগাভাগি ছাড়াও এটা নির্দিষ্ট ভাবে ঠিক হয়- হিন্দুরা মন্দিরের সামনে বাজনা বাজাবে না এবং মুসলমানরাও হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে এমনভাবে গো হত্যা করবেন না। ১৯২৩-এ কংগ্রেস এই চুক্তিকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। বল্লবভাই প্যাটেলের যুক্তি ছিল এই চুক্তিতে মুসলমানদের বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবে শুধু প্যাটেলই নন এই প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দিতে বাংলার গভর্নর লিটন থেকে শুরু করে বিড়লারাও চেষ্টার কসুর করেননি। মদনমোহন মালব্যেরও ইন্ধন ছিল একে ব্যর্থ করার পিছনে। এর পরবর্তীতেও ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাব ঐক্যের যেকোনো সম্ভবনাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে নেমেছে বিড়লাদের মতো মাড়োয়ারি-গুজরাটি দালাল পুঁজিপতি, ব্রিটিশ এবং হিন্দুত্ববাদী নেতারা। হিন্দু-মুসলিমের ঐক্য যেন দানা না বাঁধতে পারে তার জন্য ব্রিটিশরাও সচেতনভাবে নানান চাল চালছিল। মুসলমানদের পৃথক সাম্প্রদায়িক সংগঠন বানানোর জন্য উস্কানি দিচ্ছিল ব্রিটিশরা। সরকার সমর্থক মুসলিম সংগঠকদের নানা সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিধান রায় এবং নলিনী সরকার ছিলেন ব্রিটিশদের বিশ্বস্ত সহযোগী। এমন কি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ও বিধান রায় নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছেন ব্রিটিশদের। এঁরা বিড়লারও বিশেষ আস্থা ভাজন ছিলেন।
১৯৩৬-এ ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গড়ে ওঠা এবং ১৯৩৭সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর শাসনকাল বাংলার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক প্রজা পার্টি তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা কমানো, কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব করা, বাংলার স্বায়ত্তশাসন, দমন মূলক আইন বাতিল এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবির মতো প্রগতিশীল দাবি রেখেছিল। নিম্নবর্গের কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ফজলুল হক মন্ত্রীসভা। কৃষক সালিশি বোর্ড গঠন, হাট বসানোর জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা এবং নতুন নতুন হাটবাজার তৈরি করা, সুদখোরদের লাইসেন্স ব্যবস্থা এবং সুদের হার বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের পদক্ষেপ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের খুব একটা পছন্দের হওয়ার কথা নয়। ফজলুল হক কংগ্রেসের সমর্থন চেয়েছিলেন। শরৎ বসুর মতো বাংলার কংগ্রেস নেতার মতও ছিল সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গড়ার পক্ষে। কিন্তু কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল অন্যরকম। কার্যত ফজলুল হককে মুসলিম লীগের দিকে জোর করেই ঠেলে দেওয়া হয়, অসহযোগিতা করে। আরেকটি বিষয় হল সংযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের যে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল হিন্দু এবং পার্সি শিল্পপতিরা তা চায়নি। তারা চেয়েছিল শক্তিশালী কেন্দ্র। এদিকে মুসলিম ব্যবসায়ীরা চেয়েছিলেন প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসন এবং সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্র- যা প্রদেশগুলোর অধিকার ক্ষুন্ন করবে না। ১৯৪৬-৪৭ এর সময়টাতে বল্লভভাই প্যাটেল অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন বিড়লা সহ মাড়োয়ারি-গুজরাটি শিল্পপতিদের- এ কথা আগেও বলেছি। ব্রিটিশদের কাছে এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে তখন গান্ধীর চেয়েও বিশ্বস্ত তিনি। শেষ পর্যায়ে তাই প্যাটেলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা না করলে অনেক কথাই অজানা থেকে যাবে। কোলকাতার হত্যালীলা এবং নোয়াখালী দাঙ্গার পর স্ট্যাফোর্ড ক্রিন্সকে প্যাটেল লিখছেন- "কোলকাতার বিরাট হত্যালীলা সম্পর্কে আপনি শুনেছেন মনে হয়। কিন্তু এখন পূর্ববঙ্গে যা ঘটছে তা আরও অনেক খারাপ এবং নোয়াখালির কাছে কোলকাতা একেবারে স্নান হয়ে যায়। কোলকাতায় হিন্দুরাই জয়ী হয়েছে... কিন্তু নোয়াখালী কি তার বদলা?" কয়েকদিন পরে মীরাটে বললেন- "তরবারি দিয়েই তরবারির জবাব দেওয়া হবে"। নিশ্চই খুব সহজেই বুঝতে পারছেন আজ নরেন্দ্র মোদীর পছন্দের আইকন কেন বল্লভভাই প্যাটেল, কেনই বা 'ভারতের লৌহ পুরুষ' নাম দিয়ে গুজরাটে ৩০০০ কোটি টাকা খরচা করে তাঁর মূর্তি তৈরি করা হল? সেই সময় হিন্দু মহাসভা বা শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় কোনও জনভিত্তি ছিল না, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল বা বিড়লাদের যথেষ্ট পছন্দের লোক। বাংলায় বিভিন্ন নেতাদের কাছে লেখা প্যাটেলের চিঠি থেকে পরিষ্কার যে শ্যামাপ্রসাদের হাত ধরে হিন্দু মহাসভার বাংলা ভাগের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় প্যাটেলের হাত ছিল। ওদিকে জিন্না এবং লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন অবিভক্ত বাংলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি বাংলার ঐক্য এবং সংহতির জন্য আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। ১৯৪২ সাল থেকে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু ধর্মকে জাতির লক্ষণ হিসেবে ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা মাথায় রেখে তারা 'পাকিস্তান প্রস্তাবকে'ও সমর্থন করে বসে। পরে ১৯৪৫-৪৬ এ তারা সেই ভুল আবার সংশোধন করে। বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বেশ কিছু জনসভাও করে কমিউনিস্ট পার্টি। নিম্নবর্গের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল গণভোটের যে প্রস্তাব তুলেছিলেন তাও নাকচ হয় কংগ্রেস অর্থাৎ প্যাটেল বা নেহেরু এর বিপক্ষে ছিলেন বলে। ১৯৩৮ সাল থেকেই বিড়লারা বাংলা ভাগ চাইছে। কিন্তু তারা ছাড়াও গান্ধীর একটি চিঠি থেকে দেখা যায় টাটার সিনিয়র ডিরেক্টর স্যার হোমি মোদীও ভারত ভাগ এবং বাংলা ভাগের পক্ষে। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হবার পর আমরা দেখতে পাব বিড়লার উল্লাস। প্যাটেলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি লিখেছেন- "আপনি যা চেয়েছিলেন সেভাবেই সব ঘটেছে। বাংলাকে বিভক্ত করার প্রশ্নটাও যে আপনি সমাধান করেছেন তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত।"
বাংলা ভাগের কারণ সার্বিকভাবে অনুসন্ধান করা এই স্বল্প পরিসরে কখনই সম্ভব নয়। নানা জটিলতায় ধোঁয়াশায় ছেয়ে থাকা সেই সময়কে বুঝতে অনেক গভীর অনুসন্ধান জরুরি। তবে বাংলা ভাগের পিছনের অর্থনৈতিক দিক বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ কিভাবে জড়িয়ে ছিল সেটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য।
এরপর পিঠে কাঁটাতারের ক্ষত বয়ে স্বজন হারানো, সর্বশ্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মরিয়া বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হল কলোনিতে- কলোনিতে, ক্যাম্পে, রেশন দোকানের লাইনে, দণ্ডকারণ্যে অথবা আন্দামানে। অভুক্ত, অসুস্থ মানুষগুলোর আশ্রয় হত সামরিক ছাউনি, পরিত্যক্ত বাড়ি বা জবরদখল করা জমিতে গড়ে ওঠা কলোনিতে। তাঁদের যন্ত্রণাময় জীবনের আখ্যান মুখে মুখে ফিরেছে কয়েক প্রজন্ম ধরে। তবে কলোনিতে বেড়ে ওঠার কিছু ভালো দিকও আছে। জাত-পাত ছোঁয়াছুঁয়ি শিথিল হয়ে যুথবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয় কলোনির মানুষ। সমস্ত কলোনির চরিত্র এক ছিল না বা সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের সামাজিক অবস্থানও এক ধরনের ছিল না। আর বাংলাভাগের আঘাতটা শুধু ৪৭-এই এসে পড়েছিল তা নয়। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে ধাপে ধাপে মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। ওপার থেকে এপারে এসেছে কোটি কোটি মানুষ। আবার এপারের মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বড় অংশও কিন্তু উদ্বাস্তু হয়ে ওপারে গেছে। ৪৭-এ আসা মানুষের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা ছিল বেশি। তবে ১৯৫০ এর দাঙ্গার পর বিশাল সংখ্যক নিম্নবর্গের হিন্দু বিশেষত নমশূদ্র সপ্রদায়ের মানুষ এদেশে আসে যাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সত্যি কথা বলতে বছরের পর বছর ধরে এরাই আসলে বলি হয়েছে এই কাঁটাতারের যন্ত্রণায়। এদের না ছিল ব্যক্তিগত পুঁজি, না আশ্রয়, না সামাজিক ক্ষমতা বা নিরাপত্তার কোনও উৎস। সমস্ত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে যে সরকারের ব্যবহার সমান ছিল তাও নয়। সেখানেও ছিল বৈষম্য। এই দলিত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে অন্যায় অবিচারও কম হয়নি। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে হাত গুটিয়ে নিয়েছে সরকার। এদিকে সরকার উচ্ছেদ আইন এনে জবরদখল করা কলোনিগুলো থেকে উৎখাত করে বারে বারে ভিটে ছাড়া করেছে এই সব মানুষকে। তাঁদের এই যন্ত্রণার আর্তনাদ দণ্ডকারণ্যের কলোনি থেকে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে গিয়ে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারও তাঁদের সাবলম্বী হয়ে ওঠার দন্তকে সহ্য করেনি তাই তাঁদের ঠাঁই সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের জমিতে বা খালের জলে কুমিরের পেটে। সরকারি পরিভাষায় তারা আজও নিখোঁজ। দেশভাগের আতঙ্ক, যন্ত্রণা আর অন্ধকার আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাদের। এই কাঁটাতার বয়ে এনেছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের ধরে রক্ত আর চোখের জল। আজও এস আই আর বা ভোটারকার্ড সংশোধনের নামে 'এন আর সি'র খাঁড়া ঝুলছে এই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সামনে আর তার সঙ্গে 'সি এ এ'-র নামে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। তাদের চোখে পুরনো আতঙ্কের দিনগুলোকে আবার সজীব করে তুলেছে নাগরিকত্বের এই সংকট। নতুন করে দেশহীন হয়ে যাবার ভয়ে জোট বাঁধছে মানুষ। কিন্তু দেশভাগ এত জটিলতা আর ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে রেখেছে যে ব্রিটিশদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুলের' বিষ নিয়ে এখনও খেলতে পারছে আজকের জগৎ শেঠ-প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদদের উত্তরসূরিরা। আবারও স্বাধীনতার লড়াইয়ের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলার আপামর মানুষ এবং বিশেষত বাংলার দলিত, মুসলমান এবং আদিবাসী খেটে খাওয়া মানুষ।
তথ্যসূত্র
১। ঘোষ সুনীতি কুমার। ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য রাজ ১৯১৯-১৯৪৭ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড। কোলকাতাঃ প্রাচী, ১৯৮৯।
২। ঘোষ সুনীতি কুমার। বাংলা বিভাজনের রাজনীতি ও অর্থনীতি। ঢাকাঃজাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।
৩। ঘোষ সুনীতি কুমার। ইন্ডিয়ান বিগ বুর্জোয়া। কোলকাতাঃ সুবর্ণরেখা, ১৯৮৫।
৪। মেনন ভি পি। দ্য ট্যান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া। নিউ জার্সিঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭।
৫। ওয়েডারবার্ন স্যার উইলিয়াম। অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ১৮২৯-১৯১২। লন্ডনঃ আডেলফি টেরেস, ১৯১৩।
৬। থারুর শশী। অ্যান এরা অফ ডার্কনেস। নিউ দিল্লিঃ আলেফ বুক কোম্পানি, ২০১৬।
৭। বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর। পলাশী থেকে পার্টিশান। হায়দ্রাবাদঃ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৮।
৮। বন্দোপাধ্যায় শেখর, বসু রায়চৌধুরী অনুসুয়া। কাস্ট অ্যান্ড পার্টিশান ইন বেঙ্গল, দ্য স্টোরি অফ দলিত রিফিউজিস, ১৯৪৬-১৯৬১। লন্ডনঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২২।
৯। এবং অন্যকথা, একবিংশ বর্ষ, জানুয়ারি ২০১৯, সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, জলধি হালদার, অতিথি সম্পাদক সুশীল সাহা
১০। গোলওয়ালকার এম এস। উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড। নিউ দিল্লিঃ ফারোস মিডিয়া অ্যান্ড পাব্লিশিং কোং, ২০০৬।
১১। সমগ্র সাভারকার ওয়াঙ্গামায়াঃ হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, খন্ড ৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দুসভা, পুনা, ১৯৬৩

 লিখেছেন :
লিখেছেন : 



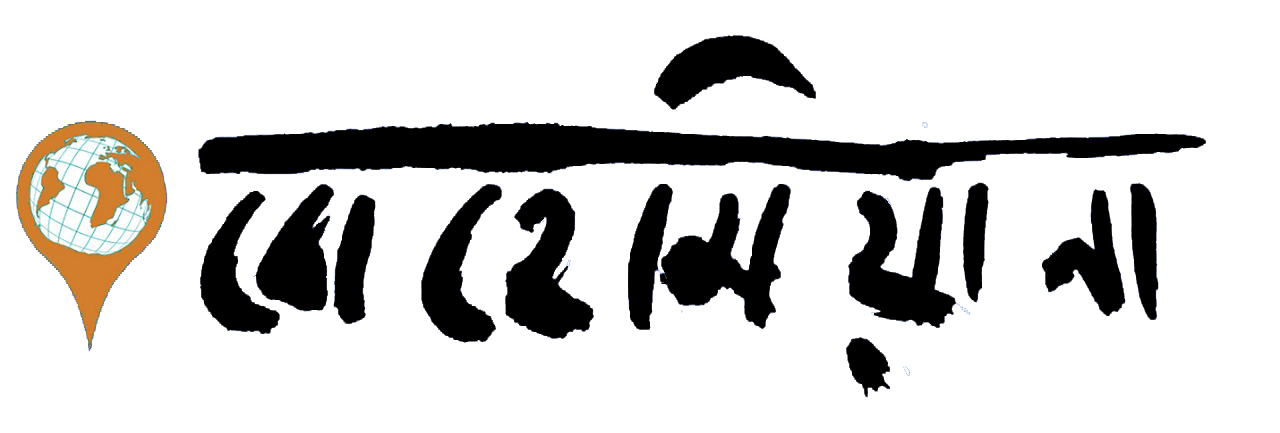
.png)