বাংলা বলার মানে কি আজ অপরাধ? মাতৃভাষা বাংলা বললেই তুমি সন্দেহভাজন, বহিরাগত কিংবা অনুপ্রবেশকারী?”—এই প্রশ্ন আজ নিছক ভাষাগত নয়, বরং গভীর রাজনৈতিক সংকেত। একদিকে ভারতকে বলা হয় বহু ভাষার দেশ, অন্যদিকে হিন্দি ও ইংরেজির আধিপত্যে বাংলা ভাষা ও তার ভাষাভাষী মানুষদের ক্রমাগত অপমান, হেনস্তা ও সন্দেহের মুখে পড়তে হচ্ছে। দিল্লি মেট্রোতে “বাংলা বলো না”, কর্ণাটকে ছাত্রদের শাস্তি, আর আসামের মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন “মাতৃভাষা বাংলা মানেই বিদেশি”, তখন স্পষ্ট বোঝা যায়—ভাষা এখানে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং নাগরিকত্ব, পরিচয় ও অধিকার নিয়ে শাসকের নির্মম রাজনীতি। এই প্রবন্ধ সেই ভাষার রাজনীতির মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টাই করব—যেখানে বাংলা শুধু ভাষা নয়, অস্তিত্বের প্রশ্ন।
ভারতীয় রাষ্ট্রে হিন্দি ও ইংরেজির রাষ্ট্রীয় আধিপত্য
ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকেই ভাষার রাজনীতি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল বিষয়। সংবিধান ‘হিন্দি’কে ‘রাজভাষা’ এবং ‘ইংরেজি’কে ‘সহায়ক ভাষা’ হিসেবে চিহ্নিত করলেও বাস্তব চিত্রটি অনেক গভীর। রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দি ও ইংরেজি যেন "জাতীয় ঐক্য"র বাহক। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের বহু ভাষিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। দক্ষিণ ভারত, উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা পূর্ব ভারতের মতো অঞ্চলগুলোতে হিন্দির আধিপত্য একরকম সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলেই মনে করা হয়।
এই প্রেক্ষাপটে বাংলা, যা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা, ক্রমে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে পেছনে পড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষায়, যেমন UPSC, SSC, কিংবা আদালতের কাজে বাংলার উপস্থিতি নামমাত্র। এমনকি সংসদের ভাষণেও বাংলা শুনতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। ফলে একটি স্বতন্ত্র ভাষার পরিচিতি হারিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে।
বাংলা ভাষা—এক আঞ্চলিক গর্বের প্রতীক
বাংলা শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়—এটি এক বিশাল সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের ভাষা এই বাংলা—যা একসময় ভারতের জাতীয় পুনর্জাগরণের মূলে ছিল। বাংলা ভাষা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
আজ এই ভাষা শুধুই এক "আঞ্চলিক" পরিচয়ে আবদ্ধ—যেন তার বৃহত্তর ঐতিহাসিক অবদান বিস্মৃত। বাংলা ভাষার সাহিত্যপ্রেমীরা আজও বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখছেন, কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি সেটিকে প্রান্তিক করেই দেখছে। এই অবস্থার ফলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে বাঙালি সমাজে, বিশেষত যুবসমাজে, যারা নিজেদের ভাষায় কথা বলার জন্য লজ্জিত নয় বরং গর্বিত।
রাষ্ট্রীয় নীতিতে বাংলার অদৃশ্য ভূমিকা
রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলার প্রভাব ক্রমহ্রাসমান। উদাহরণস্বরূপ, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত অধিকাংশ পর্যটন, তথ্য-প্রযুক্তি বা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচারে বাংলা ভাষার অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। ‘ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া’ বা অন্যান্য ব্র্যান্ডিং ক্যাম্পেইনে বাংলার সাংস্কৃতিক উপাদান থাকলেও ভাষাটি প্রায় অনুপস্থিত। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে বাংলা ব্যবহার আজও “ঐচ্ছিক”—কোনও বাধ্যতামূলক দায়িত্ব নয়।
বাংলা ভাষাকে প্রান্তিক করে তোলার এ এক নীরব রাজনৈতিক প্রকল্প, যেখানে বাংলার উপস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলে অন্য ভাষার আধিপত্য স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে। এই ধরনের নীতিগত অবহেলা শুধু ভাষা নয়, বরং এক গোটা জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বত্বাকেই আঘাত করছে।
এবার আসি বাংলায় কথোপকথন করা ভারত এর বিভিন্ন রাজ্যে থাকা মানুষদের নিয়ে—যারা শুধু ভাষাগত কারণে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, কখনও অপমানিত, আবার কখনও নিগৃহীত।
বাংলা ভাষা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হলেও, অনেক রাজ্যে এই ভাষার ব্যবহার আজও প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি যারা বাংলায় কথা বলেন, তারা কখনও রাস্তায়, কখনও স্কুলে, আবার কখনও অফিস বা প্রশাসনে অপমানিত হন—শুধু বাংলা বলার জন্য। এটি একদিকে সাংস্কৃতিক বৈষম্য, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন।
কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনা :-
১. বেঙ্গালুরুতে স্কুলে বাঙালি ছাত্রীর বাংলায় কথা বলায় শাস্তি
কিছুদিন আগে বেঙ্গালুরুর এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির এক বাঙালি ছাত্রীকে বাংলায় সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলার অপরাধে ‘দাঁড় করিয়ে রাখা হয়’ এবং অভিভাবকদের ডেকে সতর্ক করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য: “আমাদের এখানে বাংলা বলার অনুমতি নেই”।
২. মুম্বইয়ের অফিসে ‘বাংলা ভাষা মানেই বাংলাদেশি’ অপবাদ
এক কর্পোরেট অফিসে বাঙালি কর্মচারীকে বাংলা বলার কারণে সহকর্মী তাঁকে ‘বাংলাদেশি’ অনুপ্রবেশকারী বলে অপমান করেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বরং বাংলা ভাষাকে ‘আনঅফিশিয়াল’ ঘোষণা করা হয়।
৩. বাংলা মাতৃভাষা মানেই সন্দেহ?
২০২৫ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক বিতর্কিত মন্তব্যে বলেন—“যে কেউ মাতৃভাষা বাংলা বলবে, বুঝতে হবে সে বিদেশি”। এই বক্তব্যে বাংলা ভাষাকে সরাসরি অনুপ্রবেশের পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মাধ্যমে ভাষাগত পরিচয়কে নাগরিকত্বের প্রশ্নে পরিণত করে, বাঙালিদের ‘অপর’ করে তোলার রাষ্ট্রীয় প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
এই ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত রাজনীতি কী?
এই ঘটনাগুলো নিছক ব্যতিক্রম নয়—এগুলি একটি বৃহত্তর ভাষাগত আধিপত্যবাদের লক্ষণ। হিন্দি এবং ইংরেজিকে ‘ন্যাশনাল নর্ম’ হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে অন্যান্য ভাষাভাষীদের আত্মপরিচয় দমনের চেষ্টা। বাংলা ভাষা তার সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের বাইরে এক সাংস্কৃতিক শক্তি—আর তাই এই ভাষার বিরুদ্ধে এমন প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া।
এছাড়া "বাংলা মানেই বাংলাদেশি"—এই জাতীয়তাবাদী অথচ অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব শুধুই বাংলাভাষীদের প্রতি বিদ্বেষ নয়, বরং একটি ভাষার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও সন্দেহের চোখে দেখা।
ভাষার পেছনে লুকিয়ে থাকা জাতিগত ও রাজনৈতিক সংকট
আসামে বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভাষার রাজনীতি কেবল ভাষার সীমায় আটকে নেই। এখানে অসমীয়া বনাম বাঙালি, ভূমিপুত্র বনাম বহিরাগত ইত্যাদি সঙ্কটও ভাষার মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে গেছে।
বাংলা ভাষাকে এখানে একটি “বহিরাগত ভাষা” বলে মনে করা হয়, যদিও করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ও cachar-এর মতো এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী।
এই পরিস্থিতিতে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতিক শক্তিগুলি বাংলা ভাষার বিস্তারকে একটি "সাংস্কৃতিক দখলদারিত্ব" হিসেবে দেখায়। এর ফলে হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি আসামবাসী—যারা নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলেন—তাঁদের নিজেদের রাজ্যে পরবাসী মনে হয়।
উপসংহার:
একটি গণতান্ত্রিক দেশে ভাষা নির্বাচনের অধিকার মৌলিক অধিকার হওয়া উচিত। বাংলা, যেটি ভারতের ষষ্ঠ বৃহত্তম মাতৃভাষা এবং একটি সাংবিধানিক স্বীকৃত ভাষা, তাকে কথা বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, অপমান করা—এটা শুধু ভাষা নয়, ব্যক্তির অস্তিত্বকেই অপমান করা।
এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন জাতীয় স্তরে ভাষার বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করার রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জনসচেতনতা। বাংলা ভাষা শুধুই ‘বাংলার’ নয়—এটি ভারতের এক অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

 লিখেছেন :
লিখেছেন : .jpeg)



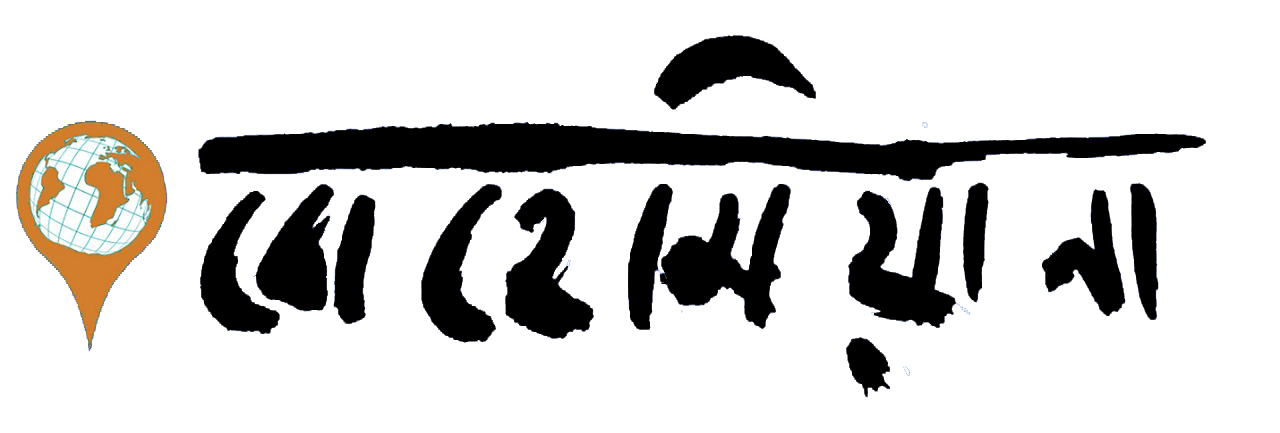
.png)