প্রথম দৃশ্য: মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে বিশাল এক রাজমূর্তি । কোমরে দড়ি পরানো। শিক্ষক,
খনিশ্রমিক, কৃষক,মজুর সবাই মিলে দড়ি ধরে টান মারলো। খানখান হয়ে ধুলিসাৎ হলো
ফ্যাসিবাদের প্রতীক হীরক রাজার মূর্তি।পতন ঘটলো স্বৈরাচারের। স্বৈরশাসকের
বিরূদ্ধে মানুষের শ্বাশ্বত লড়াইয়ের ফল,গণআন্দোলনের জয়। প্রতিবাদের রণহুঙ্কার না
দিয়ে নান্দনিকতার মৃদু উচ্চারণে ফ্যাসিবাদের গালে,অত্যাচারী শাসকের গালে বিরাশি
সিক্কার একটি থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন পরিচালক। ভবিষ্যত পৃথিবীতে,মানুষের সংগ্রামের
ইতিহাসে চিরকাল রয়ে গেল এই সৃজনশীল প্রতিবাদের বার্তা । সাক্ষ্য দেবে সেলুলয়েডের
পর্দা।
দ্বিতীয় দৃশ্য: ১৯৮৫ সাল।লাহোর স্টেডিয়ামের মঞ্চে উঠে এলেন পাকিস্তানের
বিখ্যাত গজল গায়িকা ইকবাল বানো।পরনে কালো শাড়ি! হাজার হাজার দর্শকপূর্ণ
স্টেডিয়ামে দর্শকের উল্লাসধ্বনির মধ্যে ইকবাল বানো গেয়ে উঠলেন,
‘ হাম দেখেঙ্গে, হাম দেখেঙ্গে
লাজিম হ্যায় কি হাম ভি দেখেঙ্গে...’
নিষিদ্ধ কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের গান।যাঁর গান বা কবিতার চর্চা পাকিস্তানে
নিষিদ্ধ করেছিলেন সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউল হক । জিয়াউল হক পাকিস্তানের
নারীদের জন্য ‘হিন্দুয়ানি পোশাক’ শাড়ি পরা নিষিদ্ধ করেছিলেন । সামরিক শাসকের সেই
ফরমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ইকবাল বানো গেয়ে উঠলেন,
‘ স্ব তাজ উছালে জায়েঙ্গে
স্ব তখ্ত গিরায়ে জায়েঙ্গে ...’
সব মুকুট ছুড়ে ফেলা হবে
সব সিংহাসন গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।
পঞ্চাশ হাজার দর্শকের স্টেডিয়াম উন্মত্ত হয়ে উঠল। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠতে লাগল,
‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ।
বলার অপেক্ষা রাখেনা,প্রথম দৃশ্যটি বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ
রায়ের বিখ্যাত ছবি ‘হীরক রাজার দেশে’র। শিশু-কিশোর দের জন্য নির্মিত এই ছবিটিতে
অসামান্য নৈপুণ্যে সত্যজিৎ জ্বেলে দিলেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন, যা
আদপেই বড়দের চিন্তার খোরাক । রূপকথা ও ফ্যান্টাসির আড়ালে সমাজকে তর্জনী তুলে
দেখিয়ে দিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথদিশা । দ্বিতীয় দৃশ্যটি,পাকিস্তানের
তৎকালীন স্বৈরশাসক জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে । দেশ,কাল নির্বিশেষে পৃথিবী জুড়েই
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সৃজনশীল
মানুষ তাঁদের ভিন্নমত জানিয়েছেন তাঁদের সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে। তাঁরা তাঁদের
প্রতিবাদকে স্বাক্ষরিত করেছেন সিনেমা, নাটক,গল্প,কবিতা,উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তা
সে পাকিস্তান হোক বা ভারত, ১৯৮৫ হোক বা ১৯৩৬ । বিশ্বের যে কোন দেশে,যে কোন
কালে ।
১৯৩৬ এর ১৮ জুলাই ফ্রান্সিসকো ফ্র্যাঙ্কো ও অন্যান্য ফ্যাসিস্টদের
নেতৃত্বে স্পেনের প্রজাতন্ত্র ও বৈধ ‘পপুলার ফ্রন্ট’ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র
বিদ্রোহ ঘোষনা করলে স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই গৃহযুদ্ধে সরাসরি
ফ্র্যাঙ্কোকে সমর্থন ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন হিটলার ও ইতালি র মুসোলিনি ।
এই গৃহযুদ্ধে তেত্রিশ মাসে স্পেনে খুন হন পাঁচ লক্ষ মানুষ । আসলে গত শতকের
তিরিশের দশকের শুরু থেকেই সারা পৃথিবী জুড়েই ফ্যাসিবাদের মানবতা বিরোধী অভিযান
বিকশিত হতে থাকে । জার্মানিতে নির্বিকার হত্যা,গ্রেপ্তার, প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে
নাৎসি বর্বরতা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় । ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে চলছে
প্রগতিবাদি ও গণতন্ত্রীদের কন্ঠ রোধ । ক্রমেই হিটলার এবং মুসোলিনির ক্ষমতার
অমানবিক বীভৎস রূপ পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রকাশিত হতে থাকে । ১৯৩৩ এর ২৭
ফেব্রুয়ারি রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগানোর ঘটনা হিটলারের স্বৈরাচারী মনোভাবের নগ্ন
প্রকাশ। এরপর দশ মে বার্লিনের রাজপথে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর দ্বারা বিখ্যাত
লেখকদের বইয়ের বহ্নুৎসব সারা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে নাৎসিরা মানবতার
কত বড় শত্রু !এই পরিস্থিতিতে হিংস্র ফ্যাসিবাদ এবং তার যুদ্ধ আয়োজনকে পরাস্ত
করার জন্য রোমা রোলা, ম্যাক্সিম গোর্কি ও অঁরি বারব্যুস, অগ্রগণ্য প্রগতিশীল,
গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদি সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান এই পরিস্থিতিতে
হিংস্র ফ্যাসিবাদ এবং তার যুদ্ধ আয়োজনকে পরাস্ত করার জন্য রোমা রোলা,
ম্যাক্সিম গোর্কি ও অঁরি বারব্যুস, অগ্রগণ্য প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও
মানবতাবাদি সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত
এই সম্মেলনে যোগ দেন অঁদ্রে জিঁদ, ই.এম ফরস্টার,অলডাস হাক্সলে প্রমুখ যোগ
দেন। এই সম্মেলনের পর লন্ডনে হ্যারল্ড লাস্কি,হারবার্ট রীড, মন্টেগু
স্যুটার,সাজ্জাদ জাহির, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুলকরাজ আনন্দ প্রমুখ ব্রিটিশ
ও ভারতীয় লেখক এবং বুদ্ধিজীবী একটি প্রগতি সাহিত্য সংঘ গঠন করেন।
ভারতবর্ষেও অনুরূপ সাহিত্য সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। লখনৌয়ে জহরলাল
নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কালে ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল
মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে
নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়। মুন্সি প্রেমচন্দ ও সাজ্জাদ জাহির সংঘের
সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন । এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ,ইন্দুলাল ইয়াগনিক, সাগর নিজামীর মত ব্যক্তিত্ব। উপস্থিত
ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। জহরলাল নেহেরু এবং সরোজিনী
নাইডু এই সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। পিছনে সক্রিয় উদ্যোগে সামিল ছিলেন
সেকালের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা এবং অবশ্যই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।
কিছুদিনের মধ্যেই এলাহাবাদ,লখনৌ, আলিগড়, দিল্লি, লাহোর, মুম্বাই,পুনা, দেরাদুন,
ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি শহরে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা গড়ে ওঠে। কোন সন্দেহ নেই যে,
নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকরা প্রাণিত হয়েছিলেন
রোমা রোঁলা,ম্যাক্সিম গোর্কি,অঁরি বারবুস,ই এম ফস্টার সহ প্রগতিশীল
বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য মানুষকে আহ্বানে।
১৯৩৬ সালের ১৮ জুন মস্কোয় ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়। ১১ জুলাই কলকাতার
এলবার্ট হলে স্মরণসভার আয়োজন করে বাংলার প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক
কমিটি । আহ্বায়ক ছিলেন , সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ
গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয় । ড.নরেশ
সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার যথাক্রমে সংঘের
সভাপতি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।
তৎকালীন বাংলাদেশে ( পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ) ফ্যাসিবাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে
প্রগতি লেখক সংঘ বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশকেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। সেই
সময়কার অধিকাংশ চিন্তাবিদই ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায় প্রগতি লেখক সংঘের
সক্রিয়তায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় এই সংঘের
কাজকর্মের মধ্যে নমনীয়তা, জনপ্রিয় কর্মসূচি এবং প্রয়োগের অনুশীলন
স্বাভাবিকভাবেই সমসময়ের বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল । কম্যুনিস্ট
পার্টির সদস্য বা সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই প্রগতি লেখক সংঘের ভেতর
স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিলেন। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের সামিল করার
ক্ষেত্রে সেই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যোশীর সক্রিয় ভুমিকা
এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ স্তরের একজন
নেতার একজন সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে এই ঐতিহাসিক ভুমিকা ছিল নজিরবিহীন।
পূর্ববঙ্গে মূলত ঢাকা শহরই ছিল ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মূল ভিত্তিভূমি । যদিও
শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী,রংপুর এবং অন্যান্য জেলায় মূলত
কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কৃষক সভার মাধ্যমে এই ফ্যাসিবিরোধী
আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল। কিন্তু ঢাকা ও শ্রী হট্ট ছাড়া অন্য জেলার লেখক-
শিল্পীদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের কোন স্বাক্ষর পাওয়া যায় না । ১৯৪১-এর ২২
জুন হিটলারের নাৎসি বাহিনী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর
ঝাপিয়ে পড়লে প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যরা ফ্যাসিস্ট যুদ্ধবাজদের হঠকারী
আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যবাদ কে
শেষ করার জন্য মানবতাবিরোধী হিটলার কে পরাজিত করা দরকার এই কথাটা মানুষকে
বোঝানোর জন্য প্রগতি লেখকরা বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-যুবদের সভা সংগঠিত করতে শুরু
করেন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা, রাজশাহী,মুন্সিগঞ্জ এবং অন্যান্য অনেক
জায়গাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্দোলন রূপ পেতে থাকে। চারের দশকে
সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বল্পকালের
মধ্যেই ঢাকা শহরে তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি । চারের দশকে সোভিয়েট
ইউনিয়ন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হবার স্বল্পকালের মধ্যেই ঢাকা
শহরে তৈরি হয়েছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। সমিতির সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর
সেনগুপ্ত ও দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনসাধারনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের নতুন সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরার
জন্য ঢাকা শহরের সদরঘাটে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । চিত্র
প্রদর্শনী ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং অধ্যাপক, লেখক,
সংগীত শিল্পী, ক্রীড়াবিদ,বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী
থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ পর্যন্ত সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এই চিত্র
প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করেছিলেন। ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দ এই প্রদর্শনীর
আয়োজনের সঙ্গে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ সালের 8 মার্চ সমিতির
পক্ষ থেকে ঢাকায় ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগ
দিয়েছিলেন বাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা ও প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতারা।
সম্মেলনের শুরুতেই একদল উন্মত্ত ফ্যাসিবাদ সমর্থক এবং দুষ্কৃতিকারী সম্মেলন
পন্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।তখন এইসব দুষ্কৃতীরা সম্মেলনের আগতদের
আক্রমণ করে । ঢাকা শহরের বিশিষ্ট লেখক সোমেন চন্দ একটি মিছিল নেতৃত্ব দিয়ে
সম্মেলনের মঞ্চের দিকে যখন আসছেন তার ওপর এই দুস্কৃতিকারীরা অতর্কিতে
ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দ কে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। এরপর ধীরে ধীরে
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামী মনোভাব স্পষ্ট চেহারা নিতে
শুরু করে। চল্লিশের দশকের শুরুতেই ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের লেখকরা ‘ক্রান্তি’
নামের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সোমেন চন্দের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই ঢাকা
জেলার প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামীর়
সম্পাদনায় ‘প্রতিরোধ’ নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়
মানুষকে সচেতন করতে সময়পযোগী কিছু গণসঙ্গীত রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ।
পাওয়া গেল এক তরুণ, সাধন দাসগুপ্তকে । তিনি গান লিখতেন এবং গাইতেন। মাত্র দু-
চারজন সঙ্গী নিয়ে সেই পূর্ববাংলার নানা সভায় লোকসংগীতের সুরে তিনি স্বদেশপ্রেম
এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী গান পরিবেশন করতেন । সাধারণ মানুষের কাছে এই গানগুলি খুবই
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ বছর প্রকাশিত হয় ঢাকার ‘প্রতিরোধের’ শারদীয়া সংখ্যা। এই
সংখ্যায় ফ্যাসিস্টবিরোধী কতগুলি অসাধারণ কবিতা ছাপা হয়েছিল । সেগুলো অত্যন্ত
জনপ্রিয়ও হয়েছিল । ওই সংখ্যায় কবিতা লিখেছিলেন বিমল চন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র
মৈত্র , সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।
সেসময় বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রগতিশীল পত্রপত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি
ছিল না । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিচয়' এবং
'অগ্রণী'। ‘পরিচয়’ পত্রিকায় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশোভন সরকার
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত কলম ধরেছিলেন। কয়েকজন কমিউনিস্টের উদ্যোগে
১৯৩৯ সালে বামপন্থী মাসিক পত্রিকা ‘অগ্রণী’ আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময় বাঙালি
বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারনা ছিল না।
দেশপ্রেমী বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার স্বপ্ন
দেখতেন। সেই দোলাচলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই সময় ‘অগ্রণী’ ঘোষণা
করেছিল,’সাম্রাজ্যতন্ত্র বিরোধের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত’।
সেই অগ্রণী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত
মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী লিখলেন ‘ফ্যাসিজম ও বুদ্ধি দ্রোহ’।
১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয়
সম্মেলনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। ইন্ডিয়ান
অ্যাসোসিয়েশন হলে সম্মেলনের উদ্বোধনী যে ভাষণ তারাশঙ্কর দেন তাতে তিনি বলেন,
‘আমরা মানব জাতির পক্ষে । যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে,
ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ তাদের বিরুদ্ধে । আজ পর্যন্ত বাংলা
সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ভাষা পাইয়াছে—দেশের এই সংকটও
বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট নাড়া দিয়াছে। আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া
লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন
অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা সুপার ইনকাম
ট্যাক্স দিয়েছে । এই সমস্ত মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহিত্যিক কর্তব্য
পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দু:স্থ দেশকর্মীকে সান্ত্বনা,আশা ও
নতুন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই
লেখক ও শিল্পী সংঘ । এরপর ১৯৪৫ সালের তৃতীয় সম্মেলনে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী
লেখক শিল্পী সংঘ’ পুনরায় 'প্রগতি লেখক সংঘ হয়' এবং তারাশঙ্কর ছিলেন সেই
সম্মেলন পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য।
‘অভিবাদনের’ঐ প্রথম প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় তারাশঙ্কর লিখলেন, 'এই
সাহিত্যিক এবং শিল্পী সংঘেরই মুখের দিকে চেয়ে আছি । আপনাদের কন্ঠোচ্চারিত
বাণীর সঙ্গে আমিও আমার কন্ঠস্বর মিশিয়ে দেব। সারা ভারতের জনগণকে বুঝতে
হবে-- এ সংগ্রাম শুধু তোমার মুক্তি সংগ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি
সংগ্রাম’। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব
বসুর ‘সভ্যতা ও ফ্যাসিজম’ নামের পুস্তিকা। তাতে বুদ্ধদেব বলছেন, ‘জার্মানির যাঁরা
শ্রেষ্ঠ মানব, যাদের নামে জগতের কাছে জার্মানির পরিচয়, নাৎসি শাসন সদ্য ঘুম
ভাঙ্গার কুম্ভকর্ণের মত তাঁদেরই চিবিয়ে খেতে উদ্যত-এ দৃশ্য যখন দেখলুম;যখন
দেখলুম আধুনিক জার্মানির দুই মহামানব আইনস্টাইন আর ফ্রয়েড—তাঁদের মধ্যে
একজন হলেন চৌর্যের অপবাদ নিয়ে বিতাড়িত,আর একজন বার্ধক্যের শেষ অবস্থায়
পাহারাওয়ালা ঘেরাও হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন; যখন দেখলুম জার্মানির সব বড় বড়
লেখক শিল্পী সাঙ্গীতিক নির্বাসনে দুর্দশাগ্রস্ত কিংবা মাতৃভূমিতে বন্দী;যখন কানে
এল ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী, মেয়েদের স্বাধীকার হরণের
ইতিহাস, সমস্ত জাতির চলা-ফেরায়, আচারে-ব্যবহারে, চিন্তায়-রচনায় সর্বপ্রকার
স্বাধীনতা যখন ইস্পাতের হাতে লুণ্ঠিত হলো বুঝলুম পৃথিবীতে খুব বড় রকমের একটা
গোলমাল লেগেছে ।‘ আরও বললেন, ‘বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু
লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের
দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। ১৯৪৪ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী
লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলন পরিচালনার জন্য যে
সভাপতিমন্ডলী গঠিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তার সভাপতি। সভাপতিমণ্ডলীতে
ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শচীন দেব বর্মন, অতুল বসু,
আবুল মনসুর আহমেদ গোপাল হালদার প্রমুখ। প্রারম্ভিক ভাষণে মিত্র বললেন, ‘ যুগে
যুগে মানুষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্নভাবে মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও
তাহা বাধা দিয়াছে। আজ সেই শক্তি নতুন নাম নিয়াছে, তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের
নূতন নামে অভিযান ঘোষিত হইবে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে ।
ফ্যাসিজম মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শত্রু। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে
আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও কাজ করিবার আছে।‘
ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতন্দ্র
প্রহরী। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ফ্যাসিবাদের আক্রমণ শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার মধ্যেই
সীমাবদ্ধ নয় তা বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে এক পৈশাচিক অভিযান। যখনই পৃথিবীর
যেখানেই ফ্যাসিবাদ মাথা তোলার চেষ্টা করেছে,তখনই রবীন্দ্রনাথের লেখনি শানিত
হয়ে উঠেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিশাল বিচিত্র সৃষ্টিধারায়
ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা তাই নিরবচ্ছিন্ন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই
রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের মূল উৎস উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন:
‘সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই
ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন
ঘরে বদ্ধ করেছে,আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচন্ড করে তুলেছে, তার সেই
অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।...’ । বন্ধু চার্লস
ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজকে এক চিঠিতে লেখেন: “ফ্যাসিবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতি সমগ্র
মানবজাতির উদ্বেগের বিষয়। যে আন্দোলন নিষ্ঠুর ভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে
দমন করে, বিবেক বিরোধী কাজ করতে মানুষকে
বাধ্য করে এবং হিংস্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে অপরাধ সংঘঠিত করে—সে
আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি এমন উদ্ভট চিন্তা আসার কোনও কারন
নেই।“ বিশিষ্ট মার্কসবাদী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী অঁরি বারব্যুস ১৯২৭ সালে
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি সহ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাক্ষর চেয়ে
আবেদনপত্র পাঠান। অঁরি বারব্যুস প্রেরিত সেই ঐতিহাসিক চিঠি ও আবেদনপত্রের
উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: বলাই বাহুল্য যে আপনার আবেদনের প্রতি আমার
সহানুভূতি আছে। আমি স্পষ্টই বুঝছি এই আবেদন আরো অসংখ্যের কণ্ঠ ধ্বনিত
করছে--- সভ্যতার অন্তস্থল থেকে হিংসার আকস্মিক বিস্ফোরণে যারা বিষণ্ণ।…”
ফ্যাসিবাদী শক্তির বিকাশ কবিকে উদ্বিগ্ন করেছিল। হিটলারের অভ্যুত্থানের সময়
জার্মানিতে একটি খ্রিস্টান পালা দেখার প্রতিক্রিয়ায় লিখলেন কবিতা ‘শিশুতীর্থ’।
স্পেন,আবিসিনিয়া,চেকোস্লোভাকিয়ায় বিভৎস ফ্যাসিস্ট আক্রমণের ঘটনায় বারবার
গর্জে উঠেছে কবির কলম। স্পেনে ফ্যাসিবাদী প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ
আহ্বান করলেন: ’ স্পেনে আজ বিশ্ব সভ্যতা আক্রান্ত ও পদদলিত। স্পেনের
গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল
দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। শিল্প-সংস্কৃতির
গৌরবকেন্দ্র মাদ্রিদ আজ জ্বলছে। বিদ্রোহীদের বোমার ঘায়ে তার অমূল্য শিল্প
সম্পদ আজ বিধ্বস্ত । …আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই সর্বনাশা প্লাবন রোধ
করতেই হবে। “… এই অন্ধকার সময়েই আমৃত্যু বিশ্বশান্তির পূজারী কবির কন্ঠে
ধ্বনিত হল ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের আকুল আহ্বান:
‘নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস--
বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।‘
লিখলেন,
‘ …শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কন্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী,শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন …
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর খবর পেয়ে কবি বললেন: ‘জার্মানির বর্তমান শাসকের
দাম্ভিক
ন্যায়হীনতায় বিশ্বের বিবেক আজ গভীরভাবে আহত। বর্তমান পরিস্থিতি পূর্বের
অনেকগুলি ক্ষেত্রে দুর্বলের অসহায় পীড়নের চূড়ান্ত পরিণতি।...
আমি কেবলমাত্র এই আশা প্রকাশ করতে পারি যে মানবজাতি এই পরীক্ষায়
জয়যুক্ত হোক। সর্বকালের জন্য জীবনের শুচিতা এবং অত্যাচারিত জনগণের স্বাধীনতা
দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক! পৃথিবী এই রক্তস্নানের ধারায় চিরতরে কালিমামুক্ত
হোক!’
এই সময় কলকাতা থেকে মিহির বসু ও অজয় দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়
গোটা ভারতবর্ষে সম্ভবত প্রথম ফ্যাসিস্টবিরোধী কবিতার প্রথম সংকলন ‘ প্রাচীর ‘।
সংকলনটি উৎসর্গ করা হয় শহীদ সোমেন চন্দের স্মৃতিতে । সংকলনটিতে ‘No
passaron’ নামে একটি ছোট গুরুত্বপূর্ণ গদ্য রচনা ছিল যেটি লিখেছিলেন কবি সুভাষ
মুখোপাধ্যায় । ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে সুভাষ
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ১৬ পৃষ্ঠার ‘ জনযুদ্ধের গান ‘ । প্রথম
সংস্করনে প্রকাশিত হল হিন্দি ও বাংলাভাষার মোট ১২ টি গান।গীতিকার সুভাষ
মুখোপাধ্যায়,বিনয় রায়, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রভাত বসু প্রমুখ। পরবর্তী
সংস্করণগুলিতে বিষ্ণু দে,ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়,গঙ্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুকান্ত
ভট্টাচার্য, অবন্তী সান্যাল, মণীন্দ্র রায় প্রমুখদের লেখা গানও ছাপা হল । বলিষ্ঠ
দেশপ্রেমের সঙ্গে এই গানগুলিতে মিশে ছিল ফ্যাসিজমকে রোখার দুর্জয় সংকল্প আর
মজুর কিষানের জীবনের লড়াইয়ের কথা।
তিরিশের দশক ও চল্লিশের দশকের শুরুর সময়ে যে তীব্র ফ্যাসিবাদ বিরোধীতা
বাংলার শিল্প-সাহিত্যে যে প্রভাব ফেলেছিল তা অনস্বীকার্য। কমিউনিস্ট পার্টির
পরিচালনায় এই কার্যক্রমে সামিল হয়েছিলেন সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের বৃহৎ
অংশ। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের নয় এমন অনেকেই এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও
বিষয়টা শেষ পর্যন্ত একইরকম মসূন থাকেনি । অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারনে
প্রগতি লেখক সংঘের সংশ্রব ত্যাগ করেন। তা সত্বেও সেই উজ্জীবন,সেই নতুন
জীবনের কথা এক নতুন সংস্কৃতির বার্তা বহন করেছিল। সংস্কৃতি চর্চার সেই
নমনীয়তা,সহজ চলন, বাংলা শিল্প সাহিত্য কে গণজীবনের সাথে যুক্ত করেছিল, প্রগতির
পথে আনতে সাহায্য করেছিল এবং ভাবী সংস্কৃতির ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিল এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নেই ।

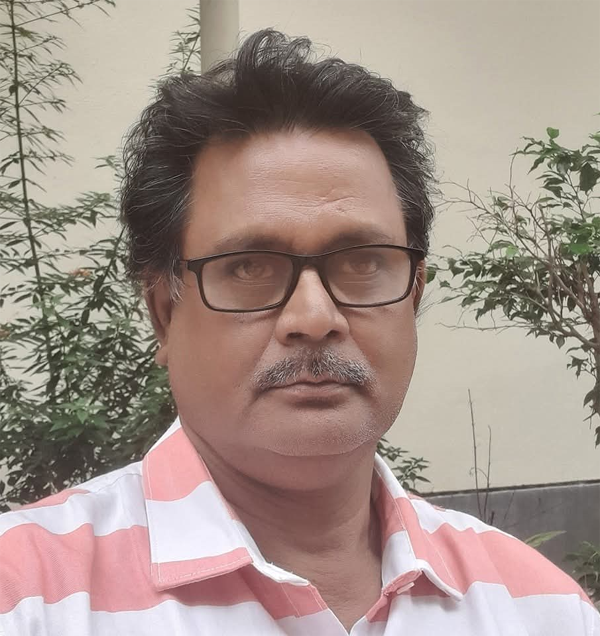 লিখেছেন :
লিখেছেন : 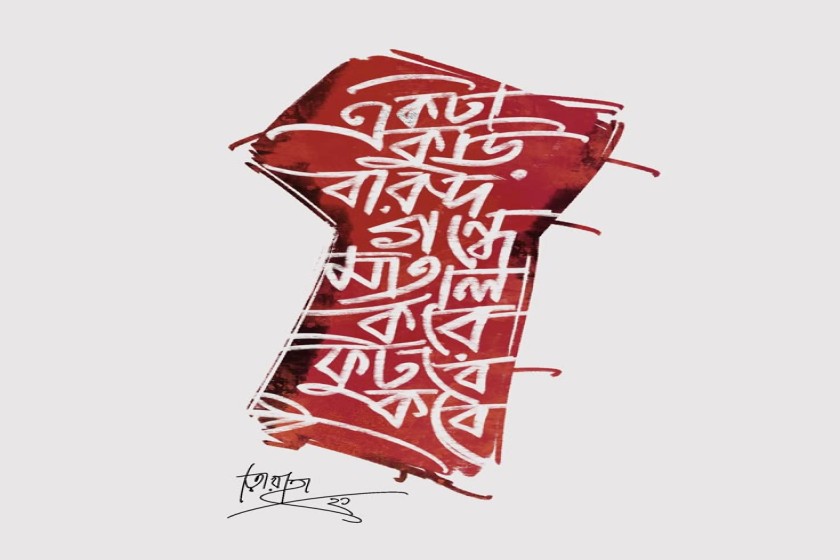



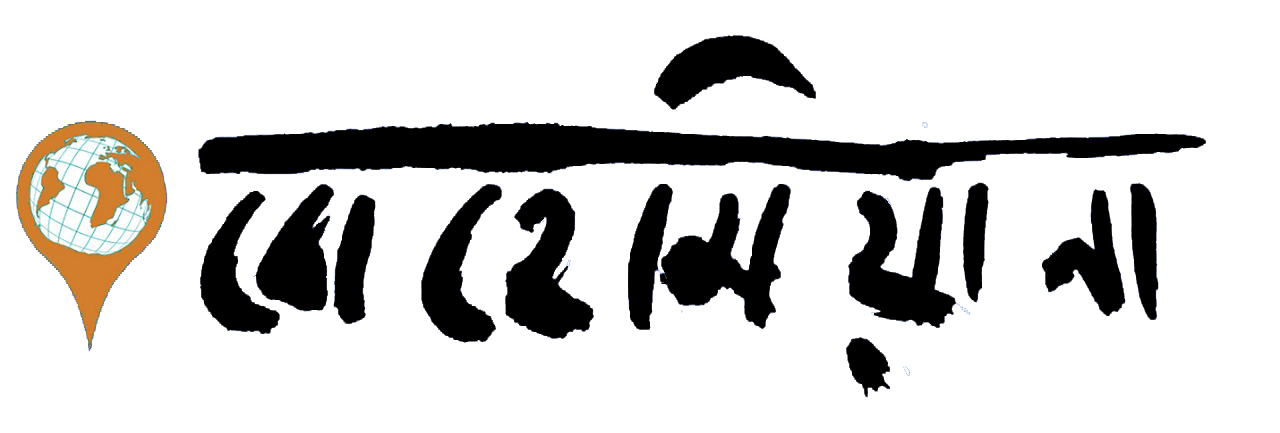
.png)