নান্দী: 'বাঙালি' যাত্রাপালাটির জন্ম হয়েছিল আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে 'The Great Calcutta Killing' এবং তার ঠিক পরে ঘটে যাওয়া নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই। সেই থেকে পালাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের দরবারে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশন করে যাচ্ছে। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সোনাই দীঘি' ও 'নটী বিনোদিনী' পালা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা( এবং সম্ভবত অভিনয়-সংখ্যা)-র বিচারে 'বাঙালি'-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু এখন 'বাঙালি' পালার আলোচনা থাক। ওই পালার একটি বিশেষ চরিত্রই আজ আমার আলোচ্য বিষয়। সেটি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলে নয়, আমার মনে হয় চরিত্রটি এই সময়েও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। অবশ্য পালাসৃষ্টির চল্লিশ বছর পর পর্যন্ত চরিত্রটিকে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় একটি ভাঁড় মনে করা হতো। পালাকারের এক সুহৃদ এবং অনুরাগীও ওই চরিত্রটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন - 'যেন কতকটা পাগলামি। একটি গুরুতর বিষয় এতে এমন হাল্কা হয়ে পড়ে যাতে দর্শকদের মনে সে সম্বন্ধে কোনো রেখাপাতই করা যায় না।'
সেই বিশেষ চরিত্র: চরিত্রটির নাম সত্যপীর। 'বাঙালি' পালায় হিন্দু ছিল, ছিল মুসলমান। সত্যপীর হিন্দুও ছিল না, মুসলমানও ছিল না। সত্যপীর ছিল 'হিন্দুমান' [ 'হিন্দু আর মুসলমানের আরক' ]। অর্থাৎ হিন্দু আর মুসলমানের সমাহার। হিন্দুদের কেউ করে বিষ্ণুর পুজো, কারও দেবতা কালী, কেউ বা ডাকে শিবকে। মুসলমানরা তো সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসই করে না। সত্যপীরের উপাস্য ছিল 'খোদাবান' [ সত্যপীরের ভাষায় 'খোদা আর ভগবানের ঘন্ট''।]। তার 'খোদাবান'-কে ডাকবার পদ্ধতির নাম সে দিয়েছিল 'পূমাজ' [ = পূজা + নমাজ। ]। তার ধর্মমত ছিল 'হিন্দুলাম' [ = হিন্দু + ইসলাম ]।
একটি নূতন ধরণের ভাঁড়কে আসরে হাজির করে যাত্রা জমাবার প্রবণতা ব্রজেন্দ্রকুমারের ছিল না। সে প্রমাণ ছিল 'বাঙালি' পালার বছর চার আগের রচনা 'দেবতার গ্রাস' পালার চন্দ্রচূড় চরিত্রে। ওই যাত্রাপালায় satire, wit এবং humour-সমৃ্দ্ধ সংলাপ প্রয়োগ করে তিনি serio-comic চরিত্র চন্দ্রচূড় সৃষ্টি করে সফল হয়েছিলেন। এমন কি এর দশ বছর আগের সৃষ্টি 'চাঁদের মেয়ে'-র পরিসমাপ্তিতেও তৎকালীন দর্শক[ শ্রোতা ]কে তাৎক্ষণিক আনন্দ দিয়ে মেকি বাহবার পাবার লোভ সংবরণ করে একটি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ মিলনবাণী প্রয়োগ করেছিলেনঃ
'একই অক্ষয় বটের দুটি শাখা তোমরা, একই বাংলা মায়ের দুটি সন্তান তোমরা হিন্দু-মুসলমান, একজনের গায়ে বিস্ফোটক হলে আর একজনকে বিষের জ্বালা সইতে হয়, একের ঘরে আনন্দের স্রোত এলে অপরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, - তবু তোমরা এমনি করে নিজেদের মাংস নিজেরা ছিঁড়ে খাবে ? তোমরা ত বনের পশু নও, তোমরা ত কৃমিকীট নও। তোমরা মানুষ, তোমরা বীর, তোমাদের ভ্রাতৃস্নেহের অমৃতধারায় বাংলার মাটি সরস হয়ে উঠুক - হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিতে বাংলায় একটা মহামানবের জাতি গড়ে উঠুক।' [১] ওই সংলাপে ঈশ্বর ছিল না। ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই মিলনের আহ্বান ছিল। এর আগে যাত্রাপালায় সম্প্রীতির বাণী হতো এই জাতীয় - 'জগতের সকল ধর্মই ঈশ্বর প্রাপ্তির এক একটা ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র,....এর মধ্যে এত হিংসা কিসের ?' বেদ এবং কোরাণ একসঙ্গে পড়িয়ে 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' বোঝানোই বিভেদ দূরীকরণের প্রকৃষ্ট পথ - এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হতো যাত্রাপালায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রার দর্শক[শ্রোতা ]দের বলেছিলেন - 'তাঁকে না ডেকেও যখন নিরাপদে এতবড়ো হয়েছি, তখন শুধু শুধু কেন আর কষ্ট করা ? বোঝাই তো যাচ্ছে, ধর্মটা ওসব ডাকাডাকির মধ্যে নেই।' [ পালা- 'ধর্মের বলি' ]
তাহলে পালাকার সত্যপীর চরিত্রটি কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন ?
হতাশ যুবক: সত্যপীরের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এইভাবে [ সত্যপীরের সংলাপেই প্রকাশিত ] ঃ সত্যপীরের মা ছিল হিন্দু। নিতান্তই বালক সত্যপীরকে রেখে সে মারা যায়। তখন অসহায় ওই ছেলেটিকে এক মুসলমান পালন করেছিল। মায়ের সঙ্গে সত্যপীর পুজোও করেছিল, মুসলমান পালকের পাশাপাশি নমাজও পড়েছিল। [ তার বাবার প্রসঙ্গে সে কিছু বলেনি। অর্থাৎ পিতৃ-পরিচয় তার জানা ছিল না। ] দুই সম্প্রদায়ের আচারের আধিক্য তথা ধর্মান্ধতা তার মনে বিরক্তি এবং বিরাগের জন্ম দিয়েছিল। যৌবনে পৌঁছে দুই সম্প্রদায় সম্পর্কেই সে নিতান্ত হতাশ হয়েছিল এবং সঠিক কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে ওই উদ্ভট ধারণার শিকার হয়েছিল। এটা সত্য যে, প্রত্যেকটি 'ধর্ম'ই সৃষ্টিকালে মানবিকতা-সম্পৃক্ত ছিল এবং ইতিবাচক ভূমিকা করেছিল। কালক্রমে সেগুলো প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে।[ হিন্দু ধর্ম শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, এমন কি কিছু বৌদ্ধ এবং আরও অনেক ছোটো-বড়ো মতের মিশ্রণ। বৈদিক মত ধীরে ধীরে এইসব মতকে গ্রহণ-বর্জন করে বর্তমান রূপ পেয়েছে। অন্যদিকে উল্লিখিত বিভিন্ন মত বৃহৎ হিন্দুমতের ছত্রছায়ায় এসেছে। ]
সত্যপীর আর একটি কথাও বলেছিল, যা এই মুহূর্তের পৃথিবীতে চরম সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সে এক মন্দিরের বারান্দায় বসে জোর গলায় পূমাজ শুরু করেছিল - 'হিন্দুরা ধবংস হক, মুসলমানেরা উচ্ছন্ন যাক, হিন্দুমানের ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হক।' সমগ্র পালাটির গতি-প্রকৃতি বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এইখানে 'হিন্দু' এবং 'মুসলমান' দুটি শব্দের আগেই উহ্য রাখা হয়েছে 'ধর্মান্ধ' শব্দটি। কারণ এর পরেই সত্যপীর তার প্রার্থনার সার প্রকাশ করেছিল - 'যারা মানুষকে ঘৃণা করে, তাদের দফা-রফা কর।' একটু পরেই সে আরও এগিয়ে গিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিল - 'মন্দির আর মসজিদ ভেঙে আমি মনজিদ [ = মন্দির + মসজিদ ] বানাবো।' কারণও সে ব্যাখ্যা করেছিল - 'দুইই অসার; যত খুন-খারাপির আড্ডা।' কয়েক বছর আগে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এক যুবতী একটি ধর্ম গ্রন্থে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তবৃন্দ প্রহারে আধমরা করে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল। [ পৃষ্ঠা ১০, ২২/০৩/২০১৫, একদিন ] 'বাঙালি' পালাতেও সত্যপীর মন্দিরের বারান্দায় 'পূমাজ' পড়ায় মন্দির অপবিত্র হবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল ছবি। তবে ছবির দাদা গণপতি সত্যপীরকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করে নি। কিন্তু এই 'secular' ভারতবর্ষে খ্রিস্টান যাজকদের 'ফাদার' বলবার বিরোধিতা করেছেন একটি সংগঠনের কিছু কর্তা। অন্য এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মসজিদকে ধর্মীয় স্থান না বলে সাধারণ ঘর বলেছেন। তালিবানরা অনেক আগেই বিশ্বের বিস্ময় বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি চূর্ণ করেছে। ধর্মের ঢাল সামনে রেখেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই জাতীয় অপকর্ম করে চলেছে বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর digital বিশ্বে।
সাধারণের চোখে: বাংলার সুবেদারের ছেলে নাসির ছিল গোঁড়া, আরও ভালো করে বললে, ধর্মান্ধ। যাত্রাপালাটির মুখ্য বিবেক ফকির তার সম্বিৎ ফেরাবার জন্য গেয়েছিল - 'শুধু মুষল, শুধুই মানে, / গড়ে না ভাই মুসলমানে।' সত্যপীর বিষ্ণুর উপাসক ছবির কাছে জানতে চেয়েছিল যে, সে তার আরাধ্য দেবতাকে দেখেছে কিনা। নেতিবাচক উত্তর পেয়ে সে তার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল - 'ভগবান নেই।' নাসিরকে তার উপাস্য নিরাকার ঈশ্বরের কথা শুনেছে কিনা প্রশ্ন করেও ইতিবাচক উত্তর পায় নি সত্যপীর। অতঃপর সে জানিয়েছিল যে, ওই কারণেই সে উপাস্যরূপে 'খোদাবান'-কে নির্বাচন করেছে। সত্যপীর কয়েকটি বিষয়ে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয়ও রেখেছিল। তার মতে [ক] 'জীবেই জীব সৃষ্টি করছে'; এবং [খ] 'তোমার আহার আমি জোগাচ্ছি, আমার আহার তুমি জোগাচ্ছ; এর মধ্যে খোদাও নেই, ভগবানও নেই।' তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ দেখান নি পালাকার।
হিন্দু ছবি মনে করে, সত্যপীরের বিচিত্র প্রার্থনার জন্য মন্দির অপবিত্র হয়েছে। 'হিন্দুলাম' ধর্ম প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার দায়ে অভিযুক্ত করে সত্যপীরকে গ্রেপ্তার করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নাসির। নাসির তাকে 'কাফের' ভেবেছিল। পালার যথার্থ ধার্মিক এবং যোগ্য শাসক দায়ুদ অবশ্য ব্যঙ্গ করে সত্যপীরকে বলেছিলেন - '....তুমি এই নাসির খাঁকে শিষ্য করে নাও। এই ভদ্রলোক ভগবানকেও কামড়াতে পারবে, খোদাকেও পথে বসাতে পারবে।' যারা ধর্মমতের ইতিবাচক গুণ ফেলে আচারকে প্রধান করে নিজেদের ঈর্ষা এবং বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে চায়, পরিণামে তারা নিজের ধর্মমতের প্রতি সাধারণ মানুষকে বিরূপ এবং বিমুখ করেই তোলে। দায়ুদের সংলাপ তারই প্রকাশ ছিল।
সঠিক পথে: নাসির সত্যপীরকে কঠোর শাস্তি দেবার জন্য সুবেদার দায়ুদ খাঁ-র কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সত্যপীর অবশ্য নিজেই দায়ুদের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। নাসির সত্যপীরকে পাগলাগারদে পাঠাবার সুপারিশ করেছিল। দায়ুদ বলেছিলেন - 'ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ। যে যে ধর্মই আচরণ করুক, তাতে বাধা দেবার অধিকার কারও নেই।' দায়ুদ সত্যপীরের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলেন যে, সে আধা হিন্দু আধা মুসলমান। তিনি এও বুঝেছিলেন যে, সত্যপীর দৃশ্যমান না হবার জন্যই খোদা আর ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে। সত্যপীরকে দায়ুদের পরামর্শ ছিল - 'তুমি হিন্দু বা মুসলমান হতে যেও না। তুমি হবে মানুষ। তোমায় নমাজও পড়তে হবে না, পুজোও করতে হবে না।' দায়ুদ সত্যপীরের বিভ্রান্তির মূল কারণ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সত্যপীর তাঁর কাছে আক্ষেপ করেছিল - 'হিন্দুরা দেয় না জল, মুসলমানেরা দেয় না পাণি।' [ হিন্দু মায়ের ছেলে মুসলমানের ঘরে প্রতিপালিত হবার জন্য দুই সম্প্রদায়ের কাছেই সে অপাংক্তেয় ছিল। ] দায়ুদ তাকে দেশগঠনে তথা দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বলেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, দায়ুদ নিজে ছিলেন মুসলমান। নিরাকার ঈশ্বরেই ছিল তাঁর বিশ্বাস। মৃত্যুর সময়েও তিনি নমাজ পড়া হল না - বলে আক্ষেপ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সত্যপীরকে মুসলমান হয়ে যাবার জন্য জোর করেন নি। আসলে তিনি 'মসজিদে আমি মুসলমান, মসনদে বাঙালি' - এই নীতিতে একনিষ্ঠ ছিলেন। [ সংলাপটি ব্রজেন্দ্রকুমারের 'বর্গী এল দেশে' পালার আলিবর্দি খাঁ-র। ] এটা সত্য যে, দায়ুদ নিজের চিন্তা থেকে ধর্মমতকে বাদ দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থারও প্রচলন করেছিলেন। দায়ুদের নির্দেশ পেয়েই সত্যপীর তার কল্পনার খোদাবানকে চিন্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। তার শেষ পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাতেই এসেছিল।
এখানে এস ওয়াজেদ আলির 'প্রেমের ধর্ম' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে - 'মসজিদ থেকে আজানের আহ্বান শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আরতির শঙ্খ এবং কাঁসরের ঘণ্টাও বেজে উঠল।' [ উদ্বোধন, বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১০ ] লেখকের প্রশ্নের উত্তরে ওই মসজিদের খাদেম বলেছিলেন - 'মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভগবান। তাঁরই উদ্দেশে আজানের ডাক আর শঙ্খের হাঁক।' ওই অভিজ্ঞতা এস ওয়াজেদ আলির হয়েছিল পাণ্ডুয়ায়।
সাম্প্রতিক কালেও ওই পাণ্ডুয়ায় দেখা যায় মহামিলনের চিত্র। মহম্মদ আকবর আলি খিচুড়ি পরিবেশন করেন, আর কলাপাতা ধুয়ে পেতে দেন প্রণব দাস। বাতাস পীরের মাজারে উড়স উৎসবে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষ প্রীতিভোজে অংশ গ্রহণ করে। [ 'চন্দ্রহাটির সম্প্রীতি বেঁধে রেখেছে বাতাস পিরের মাজার' -সুশান্ত সরকার; পৃষ্ঠা ৮, ০১/০৪/২০১৮, আনন্দবাজার পত্রিকা ]
স্মরণীয় পরিণতি: সত্যপীরকে এর পরে দেখা গিয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে। সে পরাক্রান্ত দিল্লির ফৌজের বিপক্ষে দায়ুদ খাঁ-র পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল। 'বাঙালি'-র নাট্যদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল পাঠশালার ছাত্রদের প্রার্থনা নিয়ে। দিল্লির উচপদস্থ কর্মচারী আলি মনসূরের প্রার্থনার 'যিনি হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের তিনিই আল্লা, ক্রেস্তানের তিনিই গড - সকল ধর্মের মূল এক, সকল উপাসনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য এক ....' অসহ্য হয়েছিল। সে ছাত্রদের পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে ছাত্রদের মারধোর করেছিল। দায়ুদ তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণাও করেছিলেন। আলি মনসূরের অভিযোগ পেয়ে বাদশা দায়ুদের বিরুদ্ধে বিশাল ফৌজ পাঠিয়েছিলেন। পালার শেষে দায়ুদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ধ্বংস হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীর প্রবল আক্রমণে চূর্ণ হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ পক্ষ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে যে মহাবিদ্রোহ হয়েছিল, তার প্রাবল্য শাসকদের শঙ্কিত করেছিল। তার পরেই তারা ভেদনীতি প্রয়োগ করেছিল। যখনই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়েছিল, তখনই তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। ফলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল বারবার। 'বাঙালি' পালাতেও ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত দায়ুদ-মোবারক-গণপতির প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দিয়েছিল নাসির এবং তার সহযোগীর অন্তর্ঘাত। আলি মনসূর ধর্মীয় গোঁড়ামির সূত্র ধরেই তাদের দলে টেনে এনেছিল। সেই নিরীখে সত্যপীর ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল আক্রমণকারীদের।
প্রাসঙ্গিকতাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আজাদ হিন্দ বাহিনির সেনাপতি এবং সৈনিকদের সামরিক আইনের প্যাঁচে ফেলে বিচার শুরু করেছিল ব্রিটিশ রাজশক্তি। প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা ভারতবর্ষ। আজাদ হিন্দ বাহিনির ক্যাপ্টেন রসিদ আলির সাত বছরের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ধর্ম-বর্ণ-মতবাদ নির্বিশেষে 'রসিদ আলি দিবস' পালিত হয়েছিল পুলিশের টিয়ার গ্যাস, লাঠি এবং গুলি উপেক্ষা করে। ওই ঘটনা ছিল ১৯৪৬-য়ের ফেব্রুয়ারি মাসের। কিন্তু ছ মাস পরেই দেখা গিয়েছিল বাঙালি তথা ভারতবাসী দিকে দিকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পরস্পরের রক্তপাত এবং মৃত্যু ঘটাচ্ছে আর মূল শত্রু ব্রিটিশ দূরে দাঁড়িয়ে সেই হানাহানি উপভোগ করছে। প্রথমে কলকাতায়, পরে নোয়াখালিতে হয়েছিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পালাকার সেই সময় কলকাতার সামান্য দূরে এখনকার উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে থাকতেন। কলকাতার দাঙ্গার কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। নোয়াখালির দাঙ্গায় তাঁর মেজদির দয়িত নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিলেন। তারও কিছুদিন আগে যখন তিনি পূর্ববঙ্গের কার্তিকপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তাঁর এক শিশু কন্যা প্রয়াত হয়েছিল। ওই শিশুর অসুস্থতার সময়ে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ছাত্র এবং প্রতিবেশীদের সহমর্মিতা তিনি ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেন নি কার্তিকপুর ছেড়ে চলে আসবার সময়ে, বিশেষ করে, মুসলমান ছাত্রদের 'যেতে নাহি দিব' আচরণ। তারা তাঁদের প্রিয় শিক্ষকের সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারছিল না। ইছাপুরে এসেও ব্রজেন্দ্রকুমার সেই সব ছাত্র, সেই সব প্রতিবেশী, সেই গ্রামকে ভুলতে পারেন নি। কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কার্তিকপুর বা জন্মস্থান গয়ঘর-গঙ্গানগরে তাঁর আর যাওয়া হয় নি।
রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত দ্বিজাতি তত্ত্বের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। পরবর্তীকালে 'বাঙালি'-র পরিপূরক 'ধর্মের বলি' পালায় [ যে পালা রচিত হয়েছিল ১৯৫০-য়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরে ১৯৫১-তে।] পাইক মর্দান খাঁ-র সংলাপে সেই উপলব্ধিই প্রকাশিত হয়েছিল - '....পোলাডারে ত আমি কোলে পিডে কইর্যা মানুষ করলাম।....ছাওয়ালডার মুখের দিকে চাইলে আমি ভুইল্যা যাই যে সে হিন্দু, আমি মুসলমান।' আরও পরে তাঁর পালায় এক দেশত্যাগীর কন্ঠে আরোপিত হয়েছিল এই সংলাপ - 'কোথায় গেল সে মাটির স্বর্গ পীরগঞ্জ গ্রাম ? সেই দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেতের ঢেউ খেলানো মায়া, সেই নদী, সেই বন, সেই কর্দমাক্ত পথ,....'
এই কারণেই তিনি বাঙালি' পালার মাধ্যমে বলেছিলেন -
'যত মোর ভাইবোন বাংলার আঙিনায়,
সুখে থাক, সুখে থাক গৌরব গরিমায়।
বাংলার আকাশে শশী আর রবিটি,
ফুটে থাক পাশাপাশি পটে যেন ছবিটি,
খোদা আর ভগবান, হিন্দু-মুসলমান,-
কেউ যেন মারে না গো ছুরি কারও কলিজায়।'
আর ওই উদ্দেশ্যেই তিনি এনেছিলেন 'সত্যপীরকে। নিজেরই আট বছর আগের একটি যাত্রাপালায় প্রযুক্ত গানই সময়োপযোগী পূর্ণাঙ্গ রূপে এসেছিল ওই চরিত্র হয়ে। সেই গানে ছিল - 'মন্ত্র তন্ত্র ধর্ম দেবতা ভগবান দূরে যাক।।....কী হবে তোর পুতুল পূজায়, কৃষ্ণ কালী দশভূজায়,....সব দেবতার মাথার মণি মাথায় করে রাখ।' [ মাথার মণি = জন্মভূমি ]
ধর্মান্তরিত হবার পরে আত্মীয় পরিজন পরিত্যক্ত এক নি:সঙ্গের মর্মান্তিক আক্ষেপ সেই কারণেই তাঁর রচনায় উৎসারিত হয়েছিল - 'এত যারা আপন ছিল, হিন্দু সমাজের অনুশাসনে এক মুহূর্তে তারা সব পর হয়ে গেল।' সেই সময়ে ধর্ম লোকাচারে পর্যবসিত হয়েছিল, মানবিকতা গৌণ হয়ে গিয়েছিল। [ 'ধর্মের বলি' ] [২]
ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব ধর্মান্তরিতের আট বছরের ছেলে বাবাকে একাকী রেখে চলে যেতে বাধ্য হলে বাবার জন্য প্রার্থনা করেছিল - 'তুমি ঈশা, তুমি খোদা, নারায়ণ, / দীন দুনিয়ার তুমিই শরণ,....' [ 'ধর্মের বলি' ] নিতান্তই বালক কোন্ নামে ঈশ্বরকে ডাকবে বুঝতে পারে নি। কারণ সে দেখেছিল এক সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার অভাব। [৩]
উপসংহার: 'বাঙালি' পালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট এক অধ্যাপক লিখেছিলেন - 'নাট্যকারের যে লক্ষ্য, বিশেষ একটি বক্তব্য প্রচার, তা আত্যন্তিক হয়ে ওঠে।' তিনি এ-ও বলেছিলেন - 'যাত্রাপালায় বক্তব্য থাকে - একটি রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় বা পারিবারিক শিক্ষা।' বেশ বোঝা যায় কৃতী শিক্ষক পালাটির বক্তব্যকে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু স্বল্প পরিসরে তিনি সত্যপীরকে আলোচনা করতে পারেন নি। এই মুহুর্তে, আমার মনে হয়, সাধারণ মানুষের সত্যপীরের ঈশ্বর-নিরপেক্ষতার পথ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ঘনিয়ে আসা অন্ধকার থেকে মুক্তি সম্ভবত ওই পথেই আসতে পারে।
সূত্র:
[১] ব্রজেন্দ্রকুমারের 'রাখীভাই' পালায় অনুরূপ একটি সংলাপ ছিল: 'আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই, সবাই ভারতমাতার সন্তান। একই মায়ের সন্তান যারা, তারা যেদিন কেউ কারও বিপদে সাড়া দেবে না, একজন আর একজনের কলিজার রক্ত শুষে খাবে, সেদিন ভারতে আর মানুষ বাস করবে না, বাস করবে কতকগুলো শেয়াল শকুন - যারা মনুষ্যত্বের গলিত শব নিয়ে কামড়াকামড়ি করবে, আর শয়তান মহানন্দে হাততালি দেবে।'
[২] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য ছিল - 'সেই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে।' - পৃষ্ঠা ৫২৫, 'ধর্মের নবযুগ' , গ্রন্থ - সঞ্চয়, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ [প: ব: সরকার ], দ্বাদশ খণ্ড, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৩] ' এখানে হনুমান মন্দিরের বাইরে যিনি প্রসাদ বিতরণ করেন, তিনি মুসলিম।.... এখানে সহাবস্থান করে মন্দির এবং মসজিদ একটাই ন'ইঞ্চির দেওয়ালকে মাঝে রেখে।....হিন্দুরা ইফতারের সময় মুসলিমদের জন্য সরবত তৈরি করেন।' জায়গাটি পাঞ্জাবের মালেরকোটলা শহরের সমসন্স কলোনি। - পৃষ্ঠা ৯, ১৯/৫/২০১৯, সংবাদ প্রতিদিন।
কলকাতা থেকে আসবার সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ার পোর্টের বাঁ পাশে সমকোণে চলে যাওয়া একটি রাস্তার দুপাশে দুই সম্প্রদায়ের বহু বছরের দুটি উপাসনা গৃহ দেখেছিলাম।

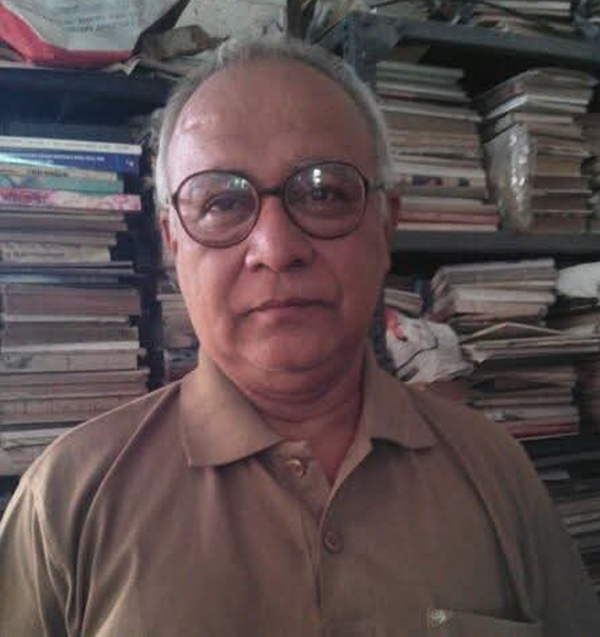 লিখেছেন :
লিখেছেন : 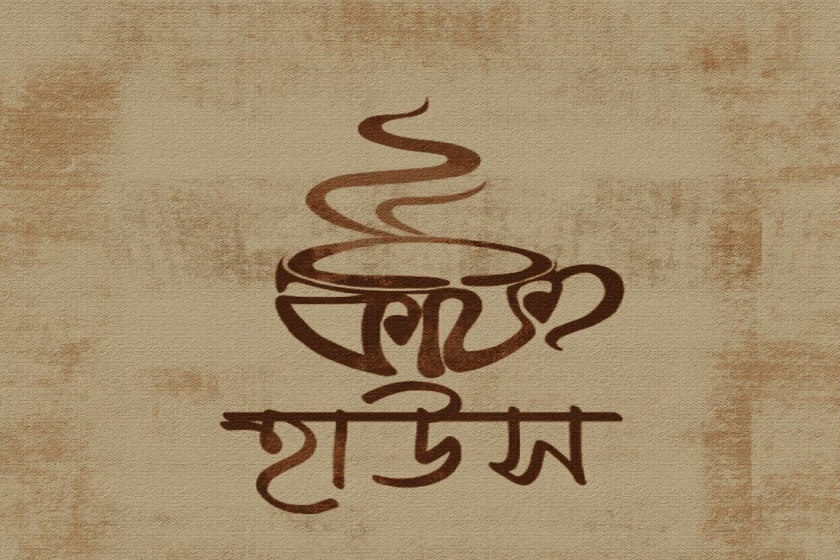



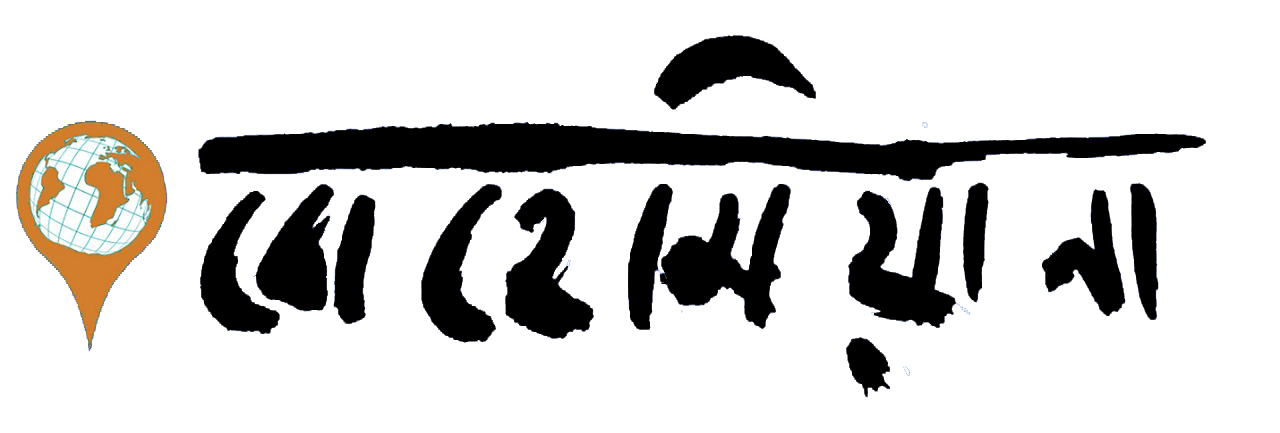
.png)